
সিদ্ধান্তের ভ্রম!

(লেখাটির উদ্দেশ্য পাঠকের চিন্তা প্রক্রিয়া জাগানো)
স্পুরিয়াস কোরিলেশন (Spurious Correlation) এর বাঙলা কি হবে? মেকি অনুসন্ধ, না কি সোজা বাঙলায় ভুয়া আন্তঃসম্পর্ক? অন্য হাজারো ইংরেজি শব্দের মতো স্পুরিয়াস শব্দের সূত্র ল্যাটিন, যার মানে হলো অবৈধ বা ভুয়া! যা সঠিক বা প্রকৃত নয়, কিম্বা যা না থেকেও থাকার ভ্রম জাগায়; তাই স্পুরিয়াস। করিলেশন মানে অনুসন্ধ যা অনেকটা আন্তঃসম্পর্ক (interrelation)-এর মতোন। কোন মতবাদ, প্রকল্প বা তত্ত্ব (তা সে বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব , ধর্ম , সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদি যে বিষয়েই হোক না কেন) বিচারের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত এড়াতে গেলে ভুয়া আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টা বুঝতে পারা জরুরী।
স্পুরিয়াস করিলেশন বুঝতে গেলে আবার ভ্যারিয়েবল (variable) বলতে কি বোঝায় সেটাও জানা দরকার। কিসের জন্য কি হচ্ছে তা বুঝতে চাইলে অর্থাৎ কোনো ঘটনা বা প্রক্রিয়ার কার্যকারণ বুঝতে চাইলে কিছু পরিবর্তনশীল উপাদান-নির্ভর হতে হয়; যার একটির পরিবর্তন অন্যটির অনুধাবনযোগ্য বা পরিমাপযোগ্য পরিবর্তন ঘটায়। বিভিন্ন পরিমাণ বা ধরণে উপস্থিত হতে পারা যে কোনো ফ্যাক্টর, বৈশিষ্ট্য বা শর্তই হলো এই পরিবর্তনশীল উপাদান বা ভ্যারিয়েবল। একটি ভেরিয়েবলকে ডেটা আইটেমও বলা যেতে পারে। বয়স, লিঙ্গ, ব্যবসায়িক আয় এবং ব্যয়, জন্মের দেশ, মূলধন ব্যয়, শ্রেণির গ্রেড, চোখের রঙ এবং গাড়ির ধরণ ইত্যাদি হলো কিছু ভ্যারিয়েবলের উদাহরণ।ভ্যারিয়েবল হতে পারে স্বাধীন, নির্ভরশীল এবং নিয়ন্ত্রিত, এই তিন ধরণের। যখন একটি মিথ্যা বা অপ্রমাণিত অনুমানে দুটি ভেরিয়েবলকে সম্পর্কিত করা হয় তখন সেটি হয় স্পুরিয়াস করিলেশন। কোন তৃতীয় (কিম্বা একাধিক)ভ্যারিয়েবলকে হিসেবে না আনা, আড়াল বা উপেক্ষা করার ফলেই ওই অবৈধ বা ভুয়া অনুমানগুলো সত্যের ভ্রম জাগায়! সমাজ-অর্থনীতির প্রক্রিয়াগুলো জটিল হওয়ায় স্পুরিয়াস করিলেশন-এর প্রয়োগে মানুষকে বিভ্রান্ত করা সহজ হয়!
এবার কিছু নমুনা দেখা যাক (কিছু নমুনা দেশ কাল ভেদে ভিন্ন হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে); বিষয়টির জটিলতার কারণে প্রথমে কিছু রসোদ্দীপক উদাহরণ এবং শেষে কিছু জটিল উদাহরণ তুলে ধরছি। এখানে উদাহরণ হিসেবে যোগ করা হয়েছে একটি সঠিক কোরিলেশন ব্যবহার করে অন্য একটি সঠিক কোরিলেশন ধামাচাপা দেয়ার অপকৌশলও (৫)
১) আইসক্রিম বেশি খেলে ডুবে মরার সম্ভাবনা বাড়ে (Moore, 1993) যে তৃতীয় উপাদানকে এই সম্পর্ক টানায় উপেক্ষা করা হয়েছে তা হোল গরম , গরম বেশি পড়লে লোকের আইসক্রিম খাওয়া এবং জলে নামা দুটোই বাড়ে
২) পুলিশের সংখ্যা বাড়লে অপরাধের পরিমাণ বাড়ে (Glass and Hopkins, 1996): এক্ষেত্রে উপেক্ষিত তৃতীয় উপাদান হোল জনসংখ্যার ঘনত্ব, যেখানে ঘনত্ব বেশি পুলিশও সেখানেই বেশি …
৩) চা ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়ঃ উপেক্ষিত উপাদান ধূমপান, চা পানকারীদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা কম …
৪) উপাসনালয়ের সংখ্যা যেখানে বেশি সেখানে মানুষ-খুনের প্রবণতাও বেশি; বড় শহরগুলোয় উপাসনালয় এবং মানুষ খুনের সংখ্যা দুইই বেশি, তবে কার্যকারণ ভিন্ন।
৫) গ্লোবাল এনার্জি ব্যালেন্স নেটওয়ার্ক জানিয়েছে যে স্থূলতা মহামারীর জন্য জাঙ্ক ফুডের ব্যবহার দায়ী নয়। গ্রুপটি বলেছে, ওজন কমানোর সমাধান, কেবলমাত্র আরও ব্যায়াম করা। আপনি আপনার পছন্দের সমস্ত জাঙ্ক ফুড খেতে পারবেন কিন্তু আপনার ওজন বাড়বে না এমনটি ভাবার আগে, বিবেচনা করুন কে এই গ্রুপটিকে স্পনসর করেছে: বিশ্বের অন্যতম সেরা জাঙ্ক ফুড প্রযোজক, Coca-Cola!
৬) মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যে একটি অনুমানযোগ্য এবং বিপরীত সম্পর্ক আছে (Phillip’s curve): অর্থনীতির রমরমা অবস্থায় বেকারত্ব কম থাকে , বেকারত্ব কম হলে মজুরি বাড়ে (যেহেতু অধিকাংশের কাজ আছে, মজুরের চাহিদা বাড়ে), মজুরি বাড়লে কেনাকাটার ধুম বাড়তে বাড়তে (যেহেতু মজুরেরা পণ্যের ভোক্তাও বটে) এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে পণ্যের যোগান তাল সামলাতে না পেরে আনে মুদ্রাস্ফীতি (যেহেতু পণ্যের যোগানের চাইতে চাহিদা বেশি হয়ে যায়)! বিপরীতে বেকারত্ব বেশি হলে (অর্থনীতির মন্দাবস্থায়) মজুরি কমে, মজুরদের কেনাকাটা কমে আর এতে মুদ্রাস্ফীতিও কমে! এই আন্তঃসম্পর্ক আপাতঃদৃষ্টে যৌক্তিক মনে হলেও একান্তই ক্ষণস্থায়ী, এই তত্ত্বের একদশকের মধ্যেই সত্তর দশকে মার্কিন অর্থনীতিতে আসে যুগপৎ বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতির দীর্ঘস্থায়ী সহাবস্থান বা stagflation! অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান Phillip’s curve – এর অসারতা তুলে ধরেন। মজুর-মালিকের মুদ্রাস্ফীতিকে হিসেবে রেখেই আগে থেকেই মজুরি নিয়ন্ত্রণের মতো তৃতীয় (এবং আরও একাধিক) ভ্যারিয়েবলকে হিসেবে না আনাই মজুরি-বেকারত্বের স্পুরিয়াস কোরিলেশন তৈরি করে।
এটুকু পাঠের পর পাঠককে সঙ্গত কারণেই কিছু হোমওয়ার্ক ধরিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের প্রতিক্রিয়ার ওপরই নির্ভর করবে এই বিষয়ে আরও কিছু লিখবো কি না।
১) আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে
২) আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের অর্থনীতি বহুগুণ বলিয়ান হয়েছে
৩) দেশে ধার্মিকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পর্দা-করা নারীর সংখ্যা বেড়েছে
৪) দেশের মানুষ খুব ভালো আছে তাই শতকরা আশি ভাগ মানুষের সমর্থনের দাবিদার বিএনপি, জনগণকে নিয়ে আন্দোলন গড়ার শক্ত বিষয় খুঁজে পাচ্ছে না (ধর্মানুভূতির সুড়সুড়ি দেয়া বিষয়বস্তু ছাড়া)
৫) প্রোপাগান্ডা করা বা বিশেষ দলমতের চালানো নিউজ (উত্তর আমেরিকার ক্ষেত্রে যেমন ফক্স নিউজ) দেখা আপনাকে বোকা করে তোলে। এটি কি একটি মিথ্যা পারস্পরিক সম্পর্ক?
চোখ-কান খোলা রাখলে এমনই আরও হাজারো আন্তঃসম্পর্ক খুঁজে পাবেন পাঠক। খুঁজুন, ভাবুন!
ডিসেম্বর ১৩, ২০১৪
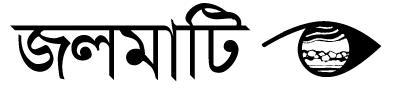












দুই বার পড়লাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এটা হয়ত আমার সীমাবদ্ধতা। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন বুঝতে পারলাম না, তার উত্তর দেয়াটাও কঠিন হয়ে পড়ে। আসলে বুঝতে না-পারা বিষয়ের কোন উত্তর দেয়া যায় না। অপেক্ষায় আছি। দেখা যাক, অন্য কারো কাছ থেকে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিনা?
দুঃখিত, উপস্থাপনার দুর্বোধ্যতার জন্য। কিছুটা জটিল বটে। এই যে আমরা কোন কিছুকে অন্য কিছুর তুলনায় ভালো বলি বা মন্দ বলি কিসের ভিত্তিতে বলি। কীভাবেই বা বলি , এটার জন্য ওটা দায়ী বা এটা করলে ওটা হবে? পরিসংখ্যান গত তুলনা একটা বহুলব্যবহৃত উপায়। কিন্তু এই ব্যবহার পদ্ধতি অতি সরলভাবে করলে আপনি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন অর্থাৎ ভুল বিষয়কে কারণ ভাবতে পারেন, ভালো মন্দ বিষয়ে ভুল ধারণা করতে পারেন। সচেতন মানুষ মাত্রেই বোঝেন যে মানুষকে বোকা বানিয়ে ভুল ভাবনায় প্রভাবিত করবার জন্য বা প্রতারণা করবার জন্য কিছু গোষ্ঠি নানা অপকৌশল প্রয়োগ করে থাকে। পরিসংখ্যানগত অপকৌশলের একটা সহজ উপায় হলো কোন ঘটনার পেছনের সম্ভাব্য কারণগুলোর মধ্য থেকে শুধু সুবিধাজনক দুয়েকটিকে তুলে ধরা আর বাকীগুলো এড়িয়ে যাওয়া। ভুল সিদ্ধান্ত ( কোন কোন ক্ষেত্রে দয়া অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে, কারণ কোন ঘটনার পেছনের একাধিক কারণের মধ্যে কিছু বাহ্য দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে) ধরিয়ে দেবার এই পদ্ধতিই হলো স্পুরিয়াস কোরিলেশন। এবার দেয়া সহজ উদাহরণগুলো আবার একটু দেখুন।
ভাল বিষয় তুলে ধরেছেন লেখক। সহজ করে বলতে গেলে যার যে তথ্যটা মানুষের কাছে তুলে ধরা দরকার তার নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য সেই তথ্যটা সামনে এনে এর সাথে অন্য যে নিয়ামকগুলো জড়িত সেগুলো আড়াল করার চেষ্টা করা হয়।
সঠিক! সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি বিষয়েই একই কথা প্রযোজ্য। উদাহরণগুলো নিয়ে ভাবলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।
চিন্তা করে মন্তব্য করতে হবে। চিন্তা করতেও অনেক পড়তে হবে জানতে হবে। তাই লেখককে অনুরোধ আরো লেখা আসুক। 🙂 অপেক্ষায় রইলাম। ধন্যবাদ।
আমাদের সবারই কমবেশী এমন কিছু বিষয়-ভাবনা রয়েছে যেগুলো অন্যরা অন্যভাবে ভাবে। এরকম দুয়েকটা নিয়ে ভাবা বা প্রশ্ন শুরু করলেই ( কেন অন্যরা সঠিক / যৌক্তিক নয়, কেন আমারটাই যৌক্তিক) উপলব্ধি সহজতর হবে। যেমন, পৃথিবীর সকল প্রাণী একই সময়কালে তৈরী হয়েছে কি? এর উত্তর হ্যাঁ না কি না, এবং কেন?
ভাষার বিকাশের সাথে অর্থনীতির কোন সম্পর্ক নেই, আপনি কি ভাবছেন, কেন? জীবজগত পরিবর্তিত হয়েছে না কি একইরকম রয়ে গেছে? পরিবর্তন প্রক্রিয়া কি চলছে? এসবের পক্ষে বিপক্ষে অনেক উত্তর পাবেন; যে কোন একটি নিয়ে যাত্রা শুরু করে দেখতে পারেন, সিদ্ধান্তের ভ্রমের নমুনা পাওয়া যায় কি না।
আরেকটি লেখা পাঠিয়েছিলাম।