
শ,ষ,স-এর বৈচিত্রময় ব্যবহার

ইংরেজী বর্ণমালায় যেখানে একটি s আছে সেখানে আমাদের আছে শ, ষ, স — এই তিনটি বর্ণ। বর্ত্তমান নিবন্ধে শ,ষ,স-এর বৈচিত্রময় ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু কথা বলছি। এই রচনায় এদের উচ্চারণ নয়, অর্থের তফাতের দিকেই আমি জোর দেব। প্রথমে কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর ‘সরল শব্দার্থকোষ’ থেকে এই তিনটি বর্ণের অর্থ (ক্রিয়া) বলছি:
শ : সার্ব্বিক শক্তিবিচ্ছুরণ (সূর্য্যের আলোর মতো)
ষ : এক দিশায় শক্তিবিচ্ছুরণ (টর্চের আলোর মতো)
স : শক্তিবিচ্ছুরণের শেষাবস্থা (একটি আলোকরশ্মির মতো)
এরপর শ, ষ ও স দিয়ে কতকগুলি শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ বলে আমরা এই তিনটি বর্ণের অর্থের তফাৎ সম্বন্ধে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।
শ বর্ণে ‘সার্ব্বিক শক্তি বিচ্ছুরণ’ বুঝায়, তাই শ্রী বানানে শ হয়। শজারুর কাঁটাও সব দিকে দাঁড়িয়ে যায়, এখানে ষ (ষজারু) বা স (সজারু) বানান চলবে না।
ষ বর্ণে ‘দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ’ (টর্চের আলোর মতো) বুঝায়। বৃষ (রেতবর্ষক), বর্ষা ইত্যাদি বানানে ষ হবে; এইসব ক্ষেত্রে শ বা স চলতে পারে না। বৃষ বানান ‘বৃস’ লিখলে তার তেজ খুব কম মনে হবে, বর্ষা বানান ‘বর্সা’ লিখলে বৃষ্টির পরিমাণ একেবারে কমে গেছে বলে মনে হবে।
স বর্ণে ‘শক্তিবিচ্ছুরণের শেষাবস্থা’ বা ‘নির্য্যাসত্যাগ’ বুঝায় (সূর্য্যের একটি রশ্মির কথা ভাবুন) । সরু বানানটা ‘শরু’ লিখলে সেটাকে সরু বুঝাবে না, গোলগাল বুঝাতে পারে। স হলে তবে সরু হয় (একটি আলোকরশ্মির মতো) ।
আমরা কোনো কিছু কষে বাঁধি, ‘কসে’ নয়। কোনো বস্তার মুখ ‘কসে’ বাঁধতে গেলে দড়িটা খুব সরু বুঝতে হবে, তা হলে সেটা সহজেই কেটে যাবে (কষে বাঁধা হল না)।
কেউ শ্রী বানানটা ‘স্রী’ লিখলে শব্দটা একেবারে শেষ হয়ে যায় (স = সরু, শেষ), ভারী বিশ্রী হয়ে যায়। মৎপ্রণীত ‘বর্ণসঙ্গীত’ বইয়ে বলা হয়েছে,”স-এর শক্তি ত্যক্ত হইলে সত্তা থাকে না আর।” শ্রী-কে ‘স্রী’ লিখলে তার শ্রী একেবারেই থাকে না।
ফুসফুস মানে যা ফুস্ ফুস্ ক’রে হাওয়ার নির্য্যাস ত্যাগ করে। ফুসফুস বানান ‘ফুশফুশ’ বা ‘ফুষফুষ’ করা চলে না। সাপের ‘ফোঁসফোঁস’ বুঝাতেও তেমনি শ বা ষ ব্যবহার না করে ‘ফোঁসফোঁস’ শব্দে স-এরই ব্যবহার হয়। তুলসী বানান তুলষী বা তুলশী লেখা হয় না। তুলসী মানে যেখানে সব তুলনার শেষ (স) হয় (তুলসী মানে অতুলনীয়া), তুলসী শব্দের স বর্ণটি শেষাবস্থার ধারক। আপনারা সর্ব্বদা তুলসী বানানে স ব্যবহার করুন।
রাক্ষস শব্দের শেষেও স হবে, কারণ রাক্ষস শব্দে রক্ষণের শেষাবস্থা বুঝায় (স মানে শেষাবস্থা)। শেষাবস্থায় রক্ষকই ভক্ষক হয়, সেই তখন রাক্ষস (‘যে রক্ষক সেই ভক্ষক’ প্রবাদটি স্মরণ করুন)। রামায়ণের রাবণ রাক্ষস ছিল, তার মানে সে প্রজাদের সম্পদ রক্ষণ করার নামে ভক্ষণ করত। অবশ্য রাবণ কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিবিশেষ নয়। যাইহোক, রাক্ষস শব্দের শেষে যে শ বা ষ চলতে পারে না (রাক্ষশ, রাক্ষষ ইত্যাদি ভুল) তা আশা করি বুঝা গেল।
শ, ষ, স সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘সহজপাঠ’ বইয়ে বলেছেন:
শ, ষ, স বাদল দিনে
ঘরে যায় ছাতা কিনে।
তাঁর এই রচনায় শ, ষ, স-এর অর্থ ফুটে উঠেনি। ‘সহজ পাঠ’ একটি অসাধারণ বই হলেও তাতে বর্ণগুলির অর্থ ঠিক ঠিক ফুটে উঠেনি। অবশ্য বর্ণমালার বর্ণগুলির তাৎপর্য্য নিয়ে কবিগুরু যে কিছুটা হলেও ভেবেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ‘জীবন ও বর্ণমালা’ নিবন্ধে। এই বিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।
আজকাল কেউ কেউ সংস্কৃত চর্চ্চার অভাবে এবং ইংরেজীর দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত হয়ে বাংলা বর্ণমালা থেকে শ, ষ, স তুলে দিয়ে ওদের মধ্যে শুধুমাত্র একটি রাখতে চান। ব্যাপারটা শুনে আমি খুব আশ্চর্য্য হচ্ছি। এটা চলতে পারে না। বাংলা বর্ণগুলি শুধু উচ্চারণ নয়, অর্থেরও ধারক বটে। শুধু উচ্চারণ ছেড়ে শ, ষ, স এর ক্রমিক শক্তিবিচ্ছুরণের তেজের কথা ভাবতে হবে। এখানে শক্তি বলতে আমি বর্ণগুলির অভিধাশক্তির কথা বলছি, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমি মনে করি যে, বাংলা বর্ণমালা থেকে শ, ষ, স-এর কোনোটিকে বাদ দেওয়া চলবে না।
এই ব্যাপারে আপনাদের মতামত কাম্য।
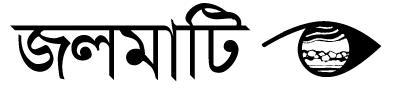












লেখকের সাথে একমত। বাংলা বর্ণমালা থেকে শ, ষ, স-এর কোনোটিকে বাদ দেওয়া চলবে না।
আমার কাছে স, শ ও ষ নিয়ে লেখার যুক্তিগুলো কিন্তু বেশ দুর্বল মনে হয়েছে।