

ঝর্ণাধারা থেকে সৃষ্টিধারা
(ইউরোসেণ্ট্রিক রিভার বনাম প্রাচ্যের নদ-নদী)
কলিম খান
“…প্রজারা … বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনও মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।” – (মুক্তধারা/রবীন্দ্রনাথ)
ইউরোসেণ্ট্রিক রিভার বনাম প্রাচ্যের নদ-নদী
পাশ্চাত্য ‘রিভার’ বলতে বোঝে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত জলধারা। এই ব্যাপারে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ খুবই স্পেসিফিক, সুনির্দ্দিষ্ট। শিল্পবিপ্লব সম্পূর্ণরূপে সমাধা করে ফেলবার কৃতিত্বের কারণে, তাঁরা একরৈখিকতার চূড়ান্তে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পেরেছে। যে কোনও বস্তু বা বিষয়কে সম্পূর্ণ আসঙ্গমুক্ত করে, একবারে ‘টু দ্য পয়েন্ট’ উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছেন তাঁরা। তাই ‘স্পেড্কে স্পেড্ বলবার’ গৌরবে তাঁরা গৌরবান্বিত হয়েছেন। ‘স্পেশালাইজেশান’-এর শিখরে তাই তাঁদের স্বাভাবিক বাস।
এই স্বভাবের কারণে, অন্য সকল বস্তু ও বিষয়ের মতো, রিভার বিষয়েও তাঁরা তাঁদের ‘স্পেশালাইজড্’ মতামত হাজির করবার যোগ্যতা ধরেন। উৎস, প্রবাহক্ষেত্র, প্রবাহক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতা, প্রবাহিত মোট জলের পরিমাণ, সে জলে অম্ল ও ক্ষারের কখন কোথায় কত মাত্রা, পলির পরিমাণ – যে কোনও ‘রিভার’ সম্পর্কে এসবই তাঁরা ছবি এঁকে নক্সা বানিয়ে সারণীর সাহায্যে খুবই বিস্তারিত ও নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করে বলে দিতে সক্ষম। কেবল তাই নয়, সমগ্র পরিবেশে, জড়জগতে, জীবজগতে এবং মানবসমাজের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে ওই ‘রিভার’সমূহ কী কী ভূমিকা নির্ব্বাহ করে ও কীরূপ প্রভাব ফেলে; প্রতিটি রিভারের ক্ষেত্রে সেসবের বিস্তারিত হিসেব তাঁরা দাখিলও করে দিতে পারেন। সেই কারণে অন্যান্য সমস্ত বস্তু বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি রিভারের বেলাতেও তাঁদের চিন্তাকাঠামোটি যথার্থই ‘স্পেসিফিক’।
প্রাচ্যের নদ-নদীকে জানতে বুঝতে গেলে সর্বাগ্রে ঝামেলা বাধায় পাশাত্যের ‘রিভার’ বিষয়ক ওই চিন্তা-কাঠামো। একে তো প্রাচ্যের নদীগুলি কেবল নদী নয়, কেউ নদ কেউবা নদী, অর্থাৎ কেউ পুরুষ রিভার কেঊ স্ত্রী রিভার; তায় আবার তাদের কারও কারও দারা-পুত্র-পরিবার বিদ্যমান। গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের কথা সবাই জানেন। কেবল তাই নয়, ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে কেউ আকাশ দিয়ে প্রবাহিত হয় (=আকাশগঙ্গা) তো কেউ পাতাল দিয়ে প্রবাহিত হয়(ভোগবতী) (১), কেউ পতিতপাবনী তো কেউ পাশমুক্তিপ্রদায়িনী (বিপাশা) (২), অনেকেই আবার ‘দেবী বা ‘গডেস’-পদবাচ্যা। কারও জন্ম হয় দু-ফোঁটা অশ্রুজলে তো কারও জন্ম হয় গান শুনে গলে গিয়ে (৩)। পাশ্চাত্যের স্পেসিফিক রিভার-চিন্তা-কাঠামো’র ভিতরে এই সকল নদ-নদীকে তাই কিছুতেই আঁটানো যায় না।
অথচ আজকের দিনে যাঁরাই প্রাচ্যের এই সকল নদ-নদী বিষয়ে জানতে বুঝতে যান, তাঁরা তাঁদের মাথার ভিতরে পাশ্চাত্যের ওই রিভার-চিন্তা-কাঠামোটি ভরে নিয়ে যান; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের অজ্ঞাত-সারেই। অনন্যোপায় হয়ে ওই কাঠামোটি ঝামেলা পাকায়। সে দাবী করে – হয় নদকে বিসর্জন দাও, নয় নদীকে। দুটোকেই এই কাঠামোর ভিতরে স্থান দেওয়া যাবে না। কেননা, ইউরোসেন্ট্রিক রিভার চিন্তাকাঠা-মোর ভিতরে পুং-রিভার ও স্ত্রী-রিভারের জন্য পৃথক প্রকোষ্ঠ নেই। তাছাড়া, জলধারার আবার বিয়ে-সাদি বালবাচ্চা এসব হয় নাকি? ওসব বাদ দাও, ফেলে দাও। মনে রাখ, প্রবাহক্ষেত্র মানেই ভূপৃষ্ঠ; আকাশবাহিনী পাতালবাহিনী – ওসব বাজে কথা। সর্ব্বোপরি, জলধারার কোন পবিত্রতা অপবিত্রতা হয়না, স্রেফ জলধারা হয়। সুতরাং পাপনাশিনী পাশমুক্তি-প্রদায়িনিদের এখানে কোনও জায়গা নেই, হবে না, ওদের বাদ দাও।
ইউরোসেণ্ট্রিক রিভার চিন্তাকাঠামোর এই দাবির কাছে নদ-নদী অনুসন্ধিৎসুগণ অগত্যা নতি স্বীকার করেন। যেহেতু, প্রাচ্যের নদ-নদীকে পাশ্চাত্যের চিন্তাকাঠামোর নিরিখে দেখতে যান তাঁরা, তাই অগত্যা তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন; রিভারের যা নেই, নদ-নদীর সেসব থাকলেও নেই। পাশ্চাত্যমানসের সঙ্গে সাম্য বজায় রাখতে গিয়ে, তাঁরা নদকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েই ক্ষান্ত হন না; নদ-নদীর আর যত আচরণ স্বভাব-চরিত্র রিভারের স্বভাবের সঙ্গে মেলে না, তা সবই তাঁরা পরিত্যাগ করেন কিংবা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ‘রিভারে’র প্রতিশব্দরূপে ‘নদী’ শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করে দেন। ফলে ‘নদী’ শব্দটির অন্তর্নিহিত নিজস্ব অর্থটিও বিসর্জ্জিত হয়ে যায়; ‘নদী’ শব্দের শরীরের ভিতর ‘রিভার’-এর আত্মা ঢুকে পড়ে। ফল হয় এই যে, লোকে মুখে বলে ‘নদী’, আর মনে বোঝে ‘রিভার’। মাঝ থেকে প্রাচ্যের নদ-নদী শেষমেষ ‘প্রাচ্যের রিভার’-এ পরিণত হয়ে যায়।
তাহলে কি প্রাচ্যের নদ-নদী ও পাশ্চাত্যের রিভার আলাদা বস্তু? প্রাচ্যের নদ-নদীতে কি জল প্রবাহাদি নেই? রিভারের মতো সেগুলির উৎস, প্রবাহক্ষেত্র, উপনদী, শাখানদী, এসব নেই? অর্থাৎ রিভারের যা যা গুণাগুণ স্বভাবচরিত্র, প্রাচ্যের নদ-নদীসমূহের কি সে সকল গুণাগুণ নেই?
গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রদের খবরাখবর নিয়ে দেখা যাচ্ছে, রিভারের গুণাগুণ তাদের তো রয়েছেই, তবে সে গুণাগুণ গৌণ; বেশ কিছ বাড়তি গুণাগুণ তাদের রয়েছে এবং সেগুলিই মুখ্য। আর মুশকিল হয় ওই বাড়তিগুলিকে নিয়েই। ইউরোপকেন্দ্রিক-রিভার-ধারণা ওই বাড়তিগুলিকে জায়গা দিতে অক্ষম। সেই কারণে, প্রাচ্যের নদ-নদী বিষয়ক আলোচনার উপর আগেভাগেই সেন্সর চাপে। নদ-নদীকে ছেঁটে কেটে কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠবাহিনী নদী বানিয়ে রিভারের সমান করে নেওয়া হয়। তারপর শুরু হয় আলোচনা, গবেষণা। ফলে, পাশ্চাত্যের ‘রিভার-রিসার্চ’ থেকে যা সব পাওয়া গেছে, প্রাচ্যের ‘নদী গবেষণা’ থেকেও সে-সবই পাওয়া যেতে থাকে। প্রাপ্তি হয়ে যায় সমান সমান, দেখতে ভালো, শুনতেও ভালো।
কিন্তু এরকম না হয়ে যদি উলটো হত? নদী-অনুসন্ধিৎসুগণ যদি তাঁদের মাথার ভিতরে প্রাচ্যের ‘নদী-বিষয়ক-চিন্তাকাঠামো’ ভরে নিয়ে নদী বিষয়ে জানতে বুঝতে যেতেন? সেক্ষেত্রে, স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, তেমন ‘চিন্তাকাঠামো’ কি প্রাচ্যের আছে?
উত্তর হল, নিশয়ই আছে। যে কোনও দেশেরই তার নিজস্ব চিন্তাকাঠামো থাকেই। তার নিজস্ব অর্জ্জন থেকে তার নিজস্ব একপ্রকার চিন্তাকাঠামো গড়ে ওঠে। তাই দিয়ে সে তার মত জগদ্দর্শন করে, তার নদী পাহাড় গাছপালাকে দেখে, বোঝে। প্রাচ্যেরও ছিল। নইলে এমন নদীর কথা প্রাচ্য জানল কেমন করে, যার বাবা হয়, মা হয়, বিয়ে হয়, সন্তানাদি হয়, সেই সন্তানদের নিজের জলস্রোতে বিসর্জ্জন দেবার প্রতিজ্ঞা হয়, সেই প্রতিজ্ঞা পালিত হয় (৪), প্রতিজ্ঞাভঙ্গও হয় এবং কী হয় না? কোন্ চিন্তাকাঠামোতে এমন নদীর কথাও স্বীকার করা সম্ভব হয়, যার কন্যা হয় এবং সে কন্যার নাম হয় সম্পদ বা লক্ষ্মী? (৫), সর্ব্বপ্রকার জলধারাই যেখানে সিন্ধু পদবাচ্য এবং তারা সর্ব্বদা মধুক্ষরণ করে? পতিতপাবনী নদীর অস্তিত্বও বা কীরূপ চিন্তাকাঠামোতে স্বাভাবিক, ত্রিলোকব্যাপী যার জলধারা প্রবাহিত, যার জলে সারা ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত জনসাধারণ আজও পাপস্খালন করে থাকেন? (৬)। তাহলে, প্রাচ্যের সেই চিন্তাকাঠামোটিকেই সর্ব্বাগ্রে জেনে বুঝে নেওয়া দরকার; যে চিন্তাকাঠামোয় নদনদীর এবম্বিধ স্বভাবচরিত্র স্বাভাবিক প্রতীয়মান হয়। কেবলমাত্র তারপরই আমরা প্রাচ্যের ওই সকল বহুরূপী নদনদীগুলিকে জানার চেষ্টা করতে পারি।
‘ইউরোসেণ্ট্রিক অউটলুক’ বনাম প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গী
উড়ছে হাঁটছে চলছে মারছে ধরছে – এইসব কথা বললে, আমরা প্রশ্ন করি, কে, কে? উত্তরে যাকে পাওয়া যায়, ওই ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করবার গৌরব তার। অর্থাৎ ওড়া হাঁটা চলা মারা ধরা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিকে দেখতে পাওয়া যায় না, যদি ওই ক্রিয়াগুলির সম্পাদক ক্রিয়াগুলির সঙ্গে না থাকে। তার মানে, আলো যেমন কারও উপর পতিত হলে তবেই সেই আলোকে দেখা সম্ভব, হয়, তেমনি ‘ক্রিয়া’কে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয় কেবল ক্রিয়াসম্পাদনকারীর আচরণে। পথিকের আচরণেই আমরা ‘পথচলা’কে দেখতে পাই। পথিককে বাদ দিয়ে ‘পথচলা’ দেখতে পাওয়া অসম্ভব। ক্রিয়াকে বাদ দিয়ে, ক্রিয়াসম্পাদককে বাদ দিয়ে, ক্রিয়াকে দেখা যাবে না; বিধির নিয়ম।
এর কারণ হল, কার্য্যত ক্রিয়া ও ক্রিয়া-সম্পাদক এক যৌথ সত্তা। একজনকে বাদ দিয়ে অন্যের অস্তিত্ব নাই। সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় বস্তুটিও একটি ক্রিয়ার সম্পাদনকারী – ‘থাকা’ ক্রিয়া। সুতরাং বিশ্বজগতের সবকিছুই এক একটি দ্বৈত সত্তা, প্রত্যেকেই ‘ক্রিয়া-কারী’। প্রশ্ন হল ঃ ওই দ্বৈত অস্তিত্বের কোন দিকটি আগে দেখা হবে? ক্রিয়ার দিকটি না কি সম্পাদকের দিকটি? ক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে, আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর নাম হবে ক্রিয়াভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সম্পাদকের দিক থেকে দেখলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটির নাম হবে বিশেষ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী। সেই ক্রিয়ার দিক থেকে জগদ্দর্শন করলে, জগদ্বিষয়ে আপনার ক্রিয়াভিত্তিক চিন্তাকাঠামো গড়ে উঠবে। আর, ক্রিয়াসম্পাদকের দিক থেকে জগদ্দর্শন করলে, জগদ্বিষয়ে আপনার গড়ে উঠবে বিশেষ্য-ভিত্তিক চিন্তাকাঠামো।
পণ্ডিতেরা এই ব্যাপারটিকে আরেকভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাঁদের মতে, জগতের মূলত দুটি রূপ। একটি হল তার বহিরঙ্গের রূপ, ফর্ম বা আধার, প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় প্রকৃতি। অপরটি হল, তার অন্তরঙ্গের রূপ, কনটেন্ট বা আধেয়; প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় একে বলে পুরুষ। ওই প্রকৃতিকে ‘দেহ’ এবং পুরুষকে ‘আত্মা’ও বলে। তন্ত্রশাস্ত্রে এই পুরুষটিকে ‘ক্রিয়া’ এবং তার আধারকে ‘প্রকৃতি’ বলা হয়েছে। জগতের ঐ বহিরঙ্গ দেখবার যে চোখ, তাকে বলে outlook বা দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী, এবং জগতের অন্তরঙ্গ দেখবার যে-চোখ, তাকে বলে আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিশেষ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী বা Outlook আসলে একই কথা, এবং বিপরীতে ‘আত্মাভিত্তিক-দৃষ্টিভঙ্গী’ এবং জগতের অন্তরঙ্গ দেখবার যে-চোখ, তাকে বলে ‘আত্মাভিত্তিক-দৃষ্টিভঙ্গী’। এই বিচারে, কার্য্যত দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিশেষ্যভিত্তিক-দৃষ্টিভংগী বা Out-Look বা ‘দেহভিত্তিক-দৃষ্টিভঙ্গী’ আসলে একই কথা। প্রথম প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গীকেই ‘ইউরোসেণ্ট্রিক আউটলুক’ ব’লে। ওই দৃষ্টিভঙ্গীও জগদ্দর্শনে তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ, অভ্যস্ত ও পটু। দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গীকে সাধারণভাবে ‘প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গী’ বলে। পণ্ডিতদের মতে, দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জগতের দৈহিক রূপসমূহের দেখা মেলে, তাই এর সাহায্যে জগতের ‘মর্ত্ত্যরূপদর্শন’ সম্ভব হয়। আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জগতের আন্তরিক রূপসমূহের দেখা মেলে, তাই এর সাহায্যে জগতের ‘অন্তরীক্ষদর্শন’ সম্ভব হয়। মর্ত্ত্যদর্শনের জন্য আমাদের মর্ত্ত্যচোখ দুটিই যথেষ্ট। কিন্তু অন্তরীক্ষদর্শনের জন্য জগতের অন্তরে ইক্ষন্ (দর্শন) করে দেখতে হয় এবং তার জন্য মর্ত্ত্যচোখ দুটি বন্ধ রেখে আমাদের তৃতীয় নয়নটি ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে তাই কবির কথাই সত্যি ঃ ‘চোখ খুললে যায় না দেখা, মুদলে পরিষ্কার’। মোট কথা, জগতের বহিরঙ্গ দেখতে হয় চোখ খুলে, আর জগতের অন্তরঙ্গ দেখতে হয় চোখ বুজে। ইউরোপের গৌরব তাই খোলা চোখে দেখায়, প্রাচ্যের গৌরব বন্ধ চোখে জগদ্দর্শনে, ‘প্রবুদ্ধমিব সুপ্ত’। মনে রাখা ভালো, অন্তরীক্ষদর্শনকেই ‘স্বর্গদর্শন’ বলে।
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, পাশ্চাত্যের মানুষেরা সাধারণভাবে জগতকে দেহের/বিশেষ্যের/প্রকৃতির/আধারের দিক থেকে দেখতে অভ্যস্ত ও পটু ঃ তাই তাঁরা জগতের মর্ত্ত্যরূপ-বিলাসী। আর প্রাচ্যের মানুষেরা সাধারণভাবে জগতকে আত্মার/ক্রিয়ার/পুরুষের/আধেয়র দিক থেকে দেখতে অভ্যস্ত ও পটু; তাই তাঁরা জগতের অন্তরীক্ষবিহারী। সেই কারণে, জগদ্দর্শনের ফলাফল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক নয়, আলাদা। পাশ্চাত্য জেনেছে জগতের দেহের খবর, সে খবর নানা উপায়ে পরিমাপযোগ্য এবং উপযোগী। আর প্রাচ্য পেয়েছে জগতের আত্মার (মনের) খবর, সে খবর অপরিমেয় এবং সমান উপযোগী। দুটোকে জুড়ে নিলে তবেই জগদ্দর্শন সম্পূর্ণ হয়। অতএব, নদ-নদী দর্শনের ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের উপলব্ধির সঙ্গে প্রাচ্যের উপলব্ধিকে জুড়ে নিতে হবে; নইলে নদ-নদী-দর্শন সম্পূর্ণ হবে না।
সুতরাং আমরা যে আজ নদী দেখতে বেরিয়েছি, আমাদের ঠিক করতে হবে, আমরা মর্ত্ত্যবিলাসী হব, নাকি অন্তরীক্ষবিহারী হব, নাকি আমাদের দুটোই চাই। প্রথম ক্ষেত্রে, যাঁরা পাশ্চাত্যের দেহভিত্তিক অউটলুকে জগদ্দর্শনে পটু এবং অতএব জগতের মর্ত্ত্যরূপজ্ঞ, তাঁরা আমাদের সহায়তা করতে পারেন, ইতিমধ্যে করেছেনও যথেষ্ট (৭)। কিন্তু জগতের অন্তরীক্ষবিহারের পথে বিস্তর বাধা। আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জগদ্দর্শন করতে গিয়ে পাওয়া সমস্ত উপলব্ধিই আমাদের বহুকাল-ক্রমাগত সংস্কারের তলায় ও ইংরেজীর আক্রমণে বিদ্ধস্ত বাঙলাভাষার ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে গেছে। একটি মাত্র উপায়, বুলডোজার দিয়ে ওই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সেই চাপা পড়া উপলব্ধিগুলিকে পুনরুদ্ধার করে, তবে অন্তরীক্ষেবিহার করবার চেষ্টা চালানো। সে ক্ষেত্রে, আশার কথা এই যে, সম্প্রতি ‘ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি’ (৮) নামে ওই বুলডোজারটি আমাদের অধিকারে এসেছে। অতএব, তাই নিয়ে আমরা এগিয়েও যেতে পারি। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে, আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাপ্ত জগদ্দর্শনের উপলব্ধিগুলিকে উদ্ধার করে, সেগুলির সাহায্যে অন্তরীক্ষবিহারের চেষ্টা চালাতে পারি।
ত্রিভুবনের নদ-নদী: আনন্দধারা ও ঘটনাপ্রবাহ:
(Universal flux of events and processes)
ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে কোনও কিছুর অনবচ্ছিন্ন অবিরাম গমনশীলতাকে বা ‘অবিচ্ছেদে প্রপাত’কে ধারা বলে। জগতে ওইরূপ অজস্র ধারা বিদ্যমান বা প্রবহমান। সেই সকল ধারাসমূহের ভিতর কোনও কোনও ধারা চোখ মেলে দেখতে পাওয়া যায়, চোখ মেলে দেখতে হয়; যেমন – জলধারা বৃষ্টিধারা অশ্রুধারা ঘটনাপ্রবাহ বিদ্যুৎপ্রবাহ বায়ুপ্রবাহ সংবাদপ্রবাহ বৃষ্টিধারা রক্তধারা ঘৃতধারা রসধারা…ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনও কোনও ধারা ও প্রবাহ আবার দেখতে হয় চোখ বন্ধ করে, যেমন – চিন্তাধারা করুণাধারা বংশধারা আনন্দধারা গতিধারা প্রজাতিধারা সৃষ্টিধারা রীতিপ্রবাহ ক্ষমতাপ্রবাহ চৌম্বকপ্রবাহ পণ্যপ্রবাহ …ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত ধারা বা প্রবাহ আসলে একই সৃষ্টিধারার অজস্র আনন্দময় রূপ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – ‘আনন্দধারা বহিছে ভূবনে’। বলেছেন… ‘আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না’ (৯)। কখনও বা ওই সকল ধারাস্রোতের মনোমুগ্ধকর রূপে গুণে বিমোহিত হয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন – ‘আনন্দমদিরাধারা’। সেই সমস্ত অগণ্য অপরিমেয় অজস্র দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান স্রোতধারা নিয়েই আমাদের এই জগৎসংসার।
স্বভাবের বিচারে ওই সকল স্রোতধারাকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় – পুরুষধারা ও প্রকৃতিধারা। পুরুষধারাগুলি সব ‘ন’-দানকারী ‘ন’-দাতা (‘ন’-দান কীরূপ ব্যাপার, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি), তাই তাদের বলা হয় ‘নদ’। আর প্রকৃতিধারাগুলি সব ‘ন’-দাতার পালন-পোষণ-কারী ও ‘ন’-দাতার ধারয়িত্রী বলে, তাদের বলা হয় ‘নদী’। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওই সকল নদ-নদীসমূহের এক ঘনজালমাত্র। এযুগের বিজ্ঞানীদের ভাষায় – ‘Universal flux of events and processes’ (১০)। প্রাচীন ভারত ওই প্রসেস (প-র-ষ-ষ)-কে পুরুষরূপে এবং ওই ইভেন্টস্কে (ইভ/ আদম/ইভ-এর ইভকে) প্রকৃতিরূপে শনাক্ত করেছিল। প্রাচ্যের এই চিন্তাকাঠামোর দ্বারা প্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ওই পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জানিয়ে গেছেন যে, গতিপ্রধান ধারাকে পুরুষ এবং স্থিতিপ্রধান ধারাকে প্রকৃতি বলে (১১)। এ যুগের বিজ্ঞানীরাও আমাদের জানাচ্ছেন যে উপরোক্ত স্রোতধারার একটি শ্রেণী হচ্ছে ‘variant’-এর স্রোতধারা অর্থাৎ নদ-শ্রেণীভুক্ত; অপর শ্রেণীটি ‘relatively invariant’-এর স্রোতধারা অর্থাৎ নদী-শ্রেণীভুক্ত।
আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এ জগতের তিন ভাগ – মর্ত্ত্যলোক, স্বর্গলোক ও পাতাললোক। এই তিনটিকে একত্রে ত্রিলোক বা ত্রিভূবন বলে। উপরোক্ত নদ-নদীসমূহ এই তিন লোকেই প্রবহমান। মর্ত্ত্যদৃষ্টিতে দৃশ্য নদ-নদীগুলি মর্ত্ত্যলোকে প্রবাহিত, অন্তরে ইক্ষণ্ করে দেখতে পাওয়া যায় যে নদ-নদীগুলিকে সেগুলি সবই অন্তরীক্ষে বা স্বর্গলোকে প্রবাহিত; আর যে সকল হিসেবের ধারা কাগজের ‘পাতা’য় ‘পাতা’য় প্রবাহিত তারা পাতাললোকে প্রবহমান (১২)। এই সকল ধারাগুলিকে নিয়েই ত্রিভূবনের নদ-নদী। আমাদের প্রয়োজন প্রাচ্যের নদ-নদী। সুতরাং, এখন সেদিকে আমাদের যেতে হবে।
প্রাচ্যের নদ-নদী: জ্ঞানপ্রবাহ ও পণ্যপ্রবাহ: চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারা
প্রাচীন ভারত কিন্তু অতকথা জানত না, জানার যোগ্যও সে হয়নি এবং জানার প্রয়োজনও তার ছিল না। তার সমস্যা ছিল সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসটা। সে চোখের উপর দেখতে পাচ্ছিল, কেমন করে সমাজটা নিজের সৃষ্টি করা সমস্যার জালে নিজেই জড়িয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমশ গতিশীলতা হারাচ্ছে। তবে, প্রাচীন ভারতের হাতে ছিল আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী, যার সাহায্যে সে দেখছিল; আর সেই দর্শন থেকে প্রাপ্ত উপলব্ধিগুলিকে বলার জন্য তার মুখে ছিল ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা; যে ভাষায় সে বলছিল। যত কৃতিত্ব, যত কারিস্মা, তার সবটাই ওই দৃষ্টিভঙ্গীর এবং ওই ভাষার। কেননা, ওই ভাষার সাহায্যে একটি নদ বা নদীর বর্ণনা দিলেই, ওই নদ বা নদীর সমধর্ম্মী সমস্বভাবী সর্ব্বলোকের সকল নদ বা নদীর বর্ণনাই দেওয়া হয়ে যায়; তা সে সকল নদ বা নদী ওই বক্তা দেখুক চাই না-দেখুক।
তার মানে, আপনি আপনার সামনে মর্ত্ত্যলোকের কোনও বস্তুকে দেখছেন আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিতে এবং তার বর্ণনা দিচ্ছেন ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়। আপনার ওই বর্ণনা, আপনার বর্ণিত বস্তুটির সমধর্ম্মী সর্বলোকের সর্ব্ববস্তুর বর্ণনাই সেরে ফেলতে সক্ষম; অথচ অন্যান্য লোকে গিয়ে সমধর্ম্মী বস্তুসমূদয়কে আপনি দেখেননি, জানেননা তাদের সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গও। এবার, আপনার বক্তব্য শোনার পর, কোনও শ্রোতা যদি মিলিয়ে দেখতে যায়, সে তাজ্জব হয়ে দেখবে যে, আপনার কথাটি সর্ব্বলোকেই সত্য। তার ধারণা হবে, আপনি বুঝি সর্ব্বলোকে অধ্যয়ন চালিয়ে, তবে ওইসব বলেছেন – আপনাকে তার খুব জ্ঞানী মানুষ মনে হবে। কিন্তু সত্যিই তো আপনি সর্ব্বলোকে অধ্যয়ন চালাননি। আপনি আসলে একটি ভাত টিপে সেই ভাতের ভিতরের খবরটা বলছিলেন ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়, তাতে যে সব ভাতের খবরই বলা হয়ে গেছে, সেটা আপনি খেয়াল করেননি। …এই সেই কারণ, যে জন্য প্রাচ্যের প্রতি একটা সমীহের ভাব পাশ্চাত্যের আজও আছে। একটি উদাহরণ দিয়ে, তারপর আমরা সোজাসুজি প্রাচ্যের নদ-নদীতে প্রবেশ করব।
‘… আদিম উদ্ভিদ ছিল ফুলহীন…। সাইলুরিয়ান যুগের শেষে (৪৪ কোটি বছর আগে) যে ফুলহীন উদ্ভিদের আত্মপ্রকাশ, পরবর্ত্তী ডিভোনিয়ান যুগের শুরুতে (৪১ কোটি বছর আগে) তার ব্যাপক বিকাশ ঘটে, ফুলহীন উদ্ভিদে ডাঙা ভরে যায়…। অ্যাঙ্গারাল্যান্ড এবং গন্ডোয়ানাল্যান্ড উভয় অতি-মহাদেশের কয়লার স্তরগুলোর উৎস যে সব গাছপালা, তারা ছিল ফুলহীন। দেশে দেশে ব্যাপ্ত ফুলহীন এই সব গভীর বন কয়লার স্তরে চিরস্থায়ী আকার নিয়েছে।’ (-সঙ্কর্ষণ রায়)।
এই বাক্যগুলি এ যুগের পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানীদের। প্রচুর অধ্যয়ন গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বহু বিজ্ঞানীর বহু বছরের চেষ্টায় তাঁরা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হতে পেরেছেন। এদিকে ভারতীয় পুরাণাদিতে, মনুসংহিতার জগৎসৃষ্টি অধ্যায়ে, আদিতে ‘পুষ্পহীন বৃক্ষের আবির্ভাব’-এর কথা বলা হয়েছে। কী করে একথা লেখা তাঁদের পক্ষের সম্ভব হল? মনুসংহিতা নিশ্চয় ১৯০০ খৃস্টাব্দের পরে লেখা হয়নি যে, পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারসমূহ মনুসংহিতাকারগণ আত্মসাৎ করেছেন। মনুসংহিতার রচনাকাল নিয়ে যত মতানৈক্য থাক না কেন, একটি ব্যাপারে সবাই একমত ঃ গ্রন্থটি নিশ্চয়ই ১০০০ খৃস্টাব্দের আগেই লেখা হয়েছিল। তা, ভারতের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা কি কয়লার প্রত্নতাত্ত্বিক পাঠ নিতে শিখে গিয়েছিলেন ১০০০ খৃস্টাব্দে বা তারও পূর্ব্বে? তখন তো কয়লাই আবিষ্কার হয়নি! তাহলে, ভারতীয় পণ্ডিতেরা ‘পুষ্পহীন বৃক্ষের’ উদ্ভব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, তার ভারতীয় উত্তরপুরুষদের কানে কানে সে কথা বলে দিয়ে যান! তাহলে মনুসংহিতাকারেরা পুষ্পহীন বৃক্ষের কথা জানলেন কেমন করে?
আসলে সংস্কৃতকারগন দিতে বসেছিলেন সামাজিক সঙ্গঠনগুলির বর্ণনা। তাঁদের সময়ে সেগুলি কেমন ছিল, তার আগে কেমন ছিল ইত্যাদি। তো, সেই প্রাচীনকালের আদি সামাজিক উৎপাদন সঙ্গঠনগুলি, তাঁরা দেখেছিলেন, ছিল পণ্যহীন। অর্থাৎ ওই সকল সঙ্গঠনগুলি বিক্রয়ের জন্য কোনও রকম উৎপাদন করত না। তাদের উৎপন্ন বিশেষ নিয়মে সারা সমাজে ভাগ হয়ে যেত। আজও অমন কিছু সরকারি সঙ্গঠন রয়েছে, যাদের উৎপন্ন বাজারে বিক্রি হয় না। ভারতে যেমন টেলিফোন লাইনের খুঁটির মাথায় চীনামাটির যে ‘পাখি’ লাগানো হয়, ওই পাখী-উৎপাদক সঙ্গঠন একটি পুষ্পহীন বৃক্ষ। আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি গাছে ফুল ফুটেছে, চারদিকে তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে – এটা যেমন দেখতে, তাঁতী অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে ধনেখালি শাড়ী বিকোচ্ছে, এই খবর (গন্ধ) বাতাসে ছড়িয়ে পড়াও তেমনি দেখতে। এবার সেখানে দ্বি-পক্ষবান পক্ষীরা [দো(দু)-কান-দারেরা] তো আসবেই, যারা তাদের ক্রেতাপক্ষ ও বিক্রেতাপক্ষ এই দুই পক্ষের উপর নির্ভর করে দোকানদারি (কিচিরমিচির) করে থাকে।
ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় এইরকম অ্যাসোসিয়েশন বা উৎপাদন সঙ্গঠন হল ‘পুষ্প’বান বৃক্ষ। আর যে সঙ্গঠনের উৎপন্নের খবর ওইভাবে বাতাসে ছড়ায় না, সে সঙ্গঠন হল পুষ্পহীন-বৃক্ষ – আদিতে এইরকম সামাজিক উৎপাদন সঙ্গঠনই সর্ব্বাগ্রে উদ্ভুত হয়েছিল। পুরাণকারগন সেই সকল সঙ্গঠনকে দেখে লিখে গেলেন ‘পুষ্পহীন বৃক্ষের সর্ব্বাগ্রে আবির্ভাবের’ কথা। আমরা এযুগে সেসব পড়ে ভাবলুম, তাঁরা বুঝি প্রকৃতিতে ফুলহীন উদ্ভিদের আদিম আবির্ভাবের পুরাতাত্ত্বিক কথা লিখে গেছেন। কিন্তু কার্য্যত তাঁরা তো প্রাকৃতিক ফুলহীন উদ্ভিদের কথা আদৌ জানতেন না। কিন্তু আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার দৌলতে পুরাতত্ত্ববিদের কথাও নিজেদের অজান্তেই পুরাণকারগন অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলে বসেন। (কেন পণ্যকে পুষ্প বলা হত, তা জানতে হলে পুষ্কর, পুষ্প, পুষ্পক, পুষ্পিকা, পুষ্পদন্ত পরভৃতি শব্দের ভিতরে ঢুকতে হয়। এই মুহূর্ত্তে সেই সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক)। একই ঘটনা ঘটে তাঁদের ‘প্রথম জলের সৃষ্টি হইয়াছিল’ (১৩) ইত্যাদি বয়ানে। কার্য্যত তাঁদের সামাজিক ঘটনাক্রমের বিকাশের বর্ণনা জড়জগৎ উদ্ভিদজগৎ ও জীবজগতের সমজাতীয় বিকাশের বর্ণনা একই সঙ্গে সেরে ফেলে তাদের বহুরৈখিক ভাষার জোরে। আমরা সেসব পড়ে আমাদের মতো করে তার মানে বুঝতে গিয়ে অবাক হয়ে যাই।
নদ-নদীর ক্ষেত্রেও সেইরকম। আদি পুরাণকারগণ দেখতে পান, মানুষের জ্ঞান ও কর্ম্ম, চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারা ক্রমশ পৃথক হয়ে যাচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে, অজস্র শাখায় ভাগ হয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, যেন দুটি ধারা থেকে দুটি ধারাশ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। তাঁদের তৎকালীন প্রকাশভঙ্গীতে, তাঁরা ওই চিন্তাধারাকে (বা চেতনাপ্রবাহ/জ্ঞানপ্রবাহ/অভিজ্ঞতাপ্রবাহকে) প্রকাশ করেন ‘নদ’ শব্দের সাহায্যে; এবং কর্ম্মধারাকে (বা উৎপন্নধারা/পণ্যপ্রবাহ/সম্পদধারাকে) প্রকাশ করেন ‘নদী’ শব্দের সাহায্যে। উত্তম অধিকারীদের বিচারে এ দুটোই আনন্দধারা। বাস্তবে, তারই প্রতিরূপ তাঁরা দেখেন ভূপৃষ্ঠবাহিনী নদ-নদীতে। নিম্ন-অধিকারীগণ অতঃপর সেই বর্ণনা বহন করতে থাকেন কেবলমাত্র ‘রিভার’ অর্থে। এখন কথা হল, উত্তম-অধিকারীদের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রেরা তাহলে দেখতে কেমন, সেটা আমাদের জানতে হবে।
ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, দামোদর, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা ও শতদ্রু
ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু
এযুগে আমরা দেখতে পাই, বুদ্ধিজীবিদের প্রধানত দুটো জাত; সমাজতন্ত্রবাদী বুদ্ধিজীবী ও ধনতন্ত্রবাদী বুদ্ধিজীবী। এঁরা একই ইউনিভার্সিটির (ভৃগুর) সন্তান হলেও, এদের স্বভাব আলাদা। একদল পণ্যজীবিদের বিরোধিতা করেন, অপরদল পণ্যজীবিদের সমর্থন করেন, বুদ্ধি জোগান। প্রাচীনকাল থেকেই বুদ্ধজীবিতার বা জ্ঞানের এই দুই ধারা। সেই ধারা আজও প্রবাহিত হয়ে আসছে। প্রাচীনকালে সমাজতন্ত্রবাদী বুদ্ধিজীবিদের বলা হত শুক্রাচার্য এবং ধনতন্ত্রবাদী বুদ্ধিজীবিদের বলা হত বৃহস্পতি। এঁরা দুজনই ভৃগুর সন্তান, ভার্গব। শুক্রাচার্য অসুরদের (বা আদি জ্ঞানঞ্জীবী সমাজতন্ত্রবাদিদের) সমর্থক, পরামর্শ-দাতা। আদ্যিকাল থেকে জ্ঞানের এই দুটি ধারা। প্রাচীন ভারতীয়রা বৈদিক যুগেই এই দুটি ধারাকে চিহ্নিত করে ফেলেছিলেন। আসুরিক-ধারাটির তাঁরা নাম দেন ব্রহ্মপুত্র এবং দেব-ধারাটির তাঁরা নাম দেন সিন্ধু। জ্ঞানপ্রবাহ বলে দুটিই পুরূষ, তাই দুটিই নদ।
মানবসমাজে কারা ‘ব্রহ্মপুত্র’, কীভাবে তাঁরা জ্ঞানপ্রবাহ অব্যাহত রাখেন, তার বিস্তারিত বিবরণ পুরাণাদিতে রয়েছে। এঁরা বেদজীবী বা জ্ঞানজীবী-বুদ্ধিজীবী হলেও জ্ঞানবিক্রয় বা বেদবিক্রয় ব্যাপারে এঁদের ঘোরতর আপত্তি ছিল। বিপরীতে, ‘স্যন্দন-স্বভাব-আদ্য-অভিমানী দেবগণ’কেই যে ‘সিন্ধু’ বলা হত, সেকথা তো শব্দকোষে আজও লিখিত দেখা যায়। এঁরা পণ্যজীবী-বুদ্ধিজীবী, জ্ঞান বিক্রয়ে এঁদের আপত্তি নেই। এই দুটি বুদ্ধিপ্রবাহেরই উৎস হল ‘মানস-সরোবর’। ধারাদুটি স্বভাবতই পরস্পরের বিপরীত দিকে ধাবিত। এই দুটি ‘নদ’ই ভারতের সবচেয়ে আদি প্রবাহ, জ্ঞানপ্রবাহের আদি বিভাজন। (কত আদি, সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব) তা সে যাই হোক, বেদবিক্রয়ে যার আপত্তি নেই, সেই সিন্ধুধারা থেকেই ক্রমে একদিন পণ্য-বিক্রয়, পুঁজিসংগ্রহ, ব্যক্তিগত সম্পদ প্রভৃতির জন্ম হয়ে যায়। সেই কারণে সম্পদ বা লক্ষ্মীকে বলা হয় সিন্ধুকন্যা।
দামোদর
পরবর্ত্তী কালে জ্ঞানপ্রবাহের অপর একটি রূপের সাক্ষাৎ পান পুরাণকারগণ। সেই প্রবাহটি হল ‘দাম উদরে যাহার’ – সেই দামোদর। যেমন পেটে পেটে বুদ্ধি, এ’র তেমনি পেটে পেটে দাম। এ’ হল পুরোপুরি পণ্যধারার সূত্রপাত হবার আগের অধ্যায়। কিংবা গোহাটাতে যেমন দেখা যায়, গরুব্যবসায়িরা একটি দড়িতে (দামে) এক সারিতে বিশ ত্রিশটি গরু বেঁধে রাখে। এক দামের একই বস্তু পরপর অনেকগুলি সাজিয়ে রাখাই ব্যবসায়িদের রীতি। ওই একজাতীয় বস্তুগুলি যেন গরুর সারি; তাদের এক দর যেন ঐ দড়ি। সমগ্র পণ্যজগতে এই দামের বাঁধন, পণ্যপ্রবাহের পেটে পেটে এই দাম-ধারণার প্রবাহ বা জ্ঞানপ্রবাহ; তাই এর নাম দামোদর।
যমুনা পদ্মা সরস্বতী
সেকালে যৌথ সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে বলা হত ‘সূর্য্য’। সেই ব্যবস্থা থেকে জাত যে উৎপন্নধারা, যা বিক্রয় হত না কিন্তু সমাজসদস্যদের ভিতর নিয়মিত ভাগ হয়ে যে, সেই উৎপন্ন-প্রবাহকে বলা হত যমুনা। এটি কর্ম্মধারার বাহক বলে স্ত্রীগুণসম্পন্না, তাই এটি নদী। এই প্রবাহ সহজবোধ্য হবে যদি সরকারি বিলি বন্দোবস্ত, কিংবা রেশন দোকানগুলির দিকে আপনি তাকান। এইরূপ সামাজিক বিলিবন্টন ব্যবস্থা আগেও ছিল। পুরাণকারগণ দেখেছিলেন, ওই বিলিবন্টনের জন্ম হয় যৌথব্যবস্থায় কার কোথায় স্থান, সেই অবস্থান নির্ণয় থেকে। এই অবস্থান নির্ণয়কে বলা হত সংজ্ঞা (বা অলিখিত সংবিধানের আদিরূপ)। যৌথব্যবস্থা আচরিত হত ওই নিরূপিত সংজ্ঞা অনুসারে। তদনুসারে সমাজসদস্যদের ওই উৎপাদনে ও উৎপন্ন বন্টনে সুনির্দ্দিষ্ট ভূমিকা ও প্রাপ্তির বিধান ছিল। ফলে একপ্রকার আইনেরও জন্ম হয়ে যায়, কে কী করবে আর কী পাবে, তাই নিয়ে। সেই কারণে সূর্য্যের (যৌথব্যবস্থার) স্ত্রীর নাম সংজ্ঞা, তাদের পুত্র যম (বা আদি আইন/ধর্মাবতার কোর্টের আদিরূপ) এবং কন্যা যমুনা (বা সমাজ কর্তৃক বিলি করা উৎপন্ন প্রবাহ)।
ভারতে এই যমুনা ধারা দু’টো। একটি গঙ্গার উপনদী, অপরটি ব্রহ্মপুত্রের শেষাবস্থা। আদি পণ্যজীবিতায় যৌথ উৎপন্ন চোরাই হয়ে জুড়ে যেত, যেমন রেশন দোকানের মাল লোকে বাজারে এখনও বেচে দেয়। এ হল গঙ্গার উপনদী। আর জ্ঞানজীবীর শেষাবস্থা যে পেনশনের ধারা, সেই ধারাই ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী যমুনা। আর পদ-অনুসারে প্রাপ্তির যে ধারাবাহিকতা সেটিই পদ্মা। এতে পণ্যজীবীদের good-will-এর প্রাপ্তিধারা যেমন প্রবাহিত, তেমনি ব্রহ্মপুত্রদের উঁচুনীচু পদ-অনুসারে প্রাপ্তিধারাও সংযুক্ত।…
অতঃপর বেদ বিভাজিত হতে হতে যখন সম্পূর্ণরূপে বিক্রয়যোগ্য ‘জ্ঞানপণ্যে’ পরিণত হয়ে গেল, জ্ঞান-বৃক্ষের (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের) জ্ঞানফলরূপে বিক্রয় হতে লাগল; তখন ওই ‘জ্ঞানপণ্যধারা’কে নাম দেওয়া হল সরস্বতী। যেহেতু এই প্রবাহটি আসলে জ্ঞানরূপী পণ্য, আবার পণ্যরূপী জ্ঞানও; তাই সরস্বতীকে নিয়ে পুরাণকারগণ ভারী মুশকিলে পড়েছেন। একে কোন পুরুষের প্রকৃতি বলা হবে, তা নির্ণয় করতে গিয়ে হিমসিম খান তাঁরা। কাজটি এখন রীতিমতো কঠিন। বইবাজার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ঘোরাঘুরি করলে ধন্দ লাগে, এগুলি জ্ঞানজীবিদের (ব্রহ্মার) রাজত্ব না পণ্যজীবিদের (বিষ্ণুর) রাজত্ব, বোঝাই যায় না। একবার মনে হয় এগুলিতে ব্রহ্মার রাজত্বই প্রকট, অন্যবার মনে হয় এগুলিতে বিষ্ণুর দাপটই বেশী। স্থির করতে না-পেরে পুরাণকারগণ কেঊ সরস্বতীকে বলেছেন ‘ব্রহ্মার ভার্য্যা’, কেউ বা বলেছেন ‘হরির ভার্য্যা’। এযুগের নিম্ন-অধিকারী পুরাণজ্ঞরা এসব কিছুই না-বুঝে ‘তোটয় তোটয়’ উচ্চারণ করতে থাকেন; যদ্দেখিতং শুনিতং তল্লিখিতং। কিনা, ‘সরস্বতী অংশে ব্রহ্মার ভার্য্যা, অংশে হরির ভার্য্যা, অংশে নদীরূপা ।’ (১৩) ‘কেন?’ – এ’রকম, প্রশ্ন করলে ঝুড়ি-ঝুড়ি বাজে কথা বকে যাবেন তাঁরা।
নর্ম্মদা শতদ্রু
আর এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা আছে, যা ‘বৈদগ্ধক্রীড়িত'(১৪)। ‘থিয়োরী’-‘প্র্যাক্টিস’-এর বা জ্ঞান-কর্ম্মের মিলন ঘটিয়ে কর্ম্মযজ্ঞ চালিয়ে সেই কর্ম্মযজ্ঞের আগুনে তেতে পুড়ে যে অভিজ্ঞতাবলী নিয়ে মানুষ সদ্যতপ্ত উঠে আসে, এ হলো সেই অভিজ্ঞতাবলীর প্রবাহ। এই অভিজ্ঞতাসমূহ সত্যম-শিবম-সুন্দরমের সাধক প্রগতিশীল মানুষদের মননের ফসল। তাই এ প্রবাহ আমাদের নর্ম্ম [নৃ+মন (ণ) ] দান করে নতুন নতুন norms গড়ে তুলতে সহায়তা করে; নর্ম্মসহচর করে, ‘নর্মাল’ রাখে। সেই কারণে, এই প্রবাহের নাম নর্ম্মদা। মানুষের নব নব অগ্রণী চিন্তাসমুহের এই ধারা মানুষের অস্তিত্বের সর্ব্বোত্তম সহায়তাকারী। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে কিছু মানুষকে এই স্বাভাবিক বিশুদ্ধবাদী ধারাটির (১৫) বাহক হতে দেখা যায়।
‘দ্রু’ শব্দের অর্থ ‘ঊর্ধ্বগামী’। একে বৃক্ষও বলা হয়। এ’টি প্রতিষ্ঠানও বটে। তবে এ হল শত শত প্রতিষ্ঠানের ধারা। এ’ ধারার উদ্ভব ঘটেছিল সিন্ধুধারার পরেই। তাই শতদ্রু মানে ‘শত ধারা প্রবাহিতা’। এইটি পণ্যজীবী-সমর্থক-বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা অধ্যুষিত। এ নদ তাই সিন্ধুর সগোত্র, উৎসও তার একই।
গঙ্গা নদী
এককালে কাটিলেন হর দ্বিজ মাথা ।
/ব্রহ্মহত্যা পাপ তার না হয় অন্যথা ।।…
শুনিয়া গৌরীর কথা শিব হাসি ভাষে ।
পৃথিবীতে গেল গঙ্গা সর্ব্বপাপ নাশে ।। – (কৃত্তিবাস)
গঙ্গানদীর আবির্ভাব ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করা দরকার যে এই প্রবাহকে ‘আনয়ন’ করা হয়েছিল। সেটা কেমন ব্যাপার? ব্যাপার এই হয়েছিল যে, পণ্যজীবিদের আদি পণ্যজীবিতা ক্রমশ সাবালক হয়ে ওঠার ফলে সমাজে পণ্যধারা-স্রোতের একটি সর্বজনস্বীকৃত ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল; মেলা ও হাট বসানোর দাবি উঠেছিল। কিন্তু সেকালের সমাজতন্ত্রবাদী বেদজীবিদের চোখে সেটি ছিল ‘পাপ’-আচরণকে রীতিমতো প্রশ্রয় দেওয়া। কেবলমাত্র বিক্রয়ের জন্য উৎপন্নকে (বা পণ্যকে) সেকালে বলা হত পাপ-আচরণ করা। কিন্তু বেদজীবিদের পক্ষে ঐ দাবীকে ঠেকানো শেষ পর্যন্ত অসম্ভব ছিল। কারণ তাদের আদি বৈদিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভিতরে ভিতরে ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল; তাতে অজস্র ছিদ্র দেখা দেয়েছিল। আদি পণ্যের উদ্ভব ঘটেছিল সেই ফাঁকগুলিতে – ‘in the pores of the society’ (১৬) – ভিতরে ভিতরে পণ্য (পাপ) জমে উঠেছিল মানুষের ঘরে ঘরে। সেই ‘পাপ’-স্খালন করবার জন্য সমাজে ‘commodity flow’ বা পণ্যধারা প্রবাহিত করবার প্রয়োজন দেখা দেয়েছিল একান্তভাবেই। কিন্তু হাট মেলা বাজার এসব বসিয়ে ফেললে, পণ্যধারা-গঙ্গাধারা তো হাট থেকে হাটে, তীর্থ থেকে তীর্থে ঘুরে ঘুরে প্রবাহিত হয়ে হয়ে জনসমুদ্রে গিয়ে মিশে যাবে! বেদজীবীরা যাকে যা বানাতে এবং যাকে যা দিতে নির্দ্দেশ দিয়ে রেখেছেন; তার মর্য্যাদা থাকবে কী করে? লোকে তো যাকে খুশী তাকে নিজের উৎপন্ন বেচে দেবে? সেকালের বিচারে এ ছিল উচ্ছন্নে যাবার অবাধ স্বাধীনতা।
তবে শেষ পর্য্যন্ত বহু ত্যাগ তিতিক্ষার ভিতর দিয়ে ঐ পণ্যপ্রবাহ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, গঙ্গা আনয়ন করা সম্ভব হয়, কৃত্রিম প্রবাহের সূচনা করা সম্ভব হয়। … ক্রমে একদিন সর্বজনস্বীকৃত পণ্যধারারূপে তা প্রবাহিত হতে থাকে। তবে ওই সর্বজনস্বীকৃতির জন্য কোথাও আবেদন নিবেদন করে কাজ বয়, কোথাও চাতুরীতে কাজ হয়, কোথাও বা ব্রহ্মহত্যারও প্রয়োজন পড়ে। যাইহোক, এই গঙ্গা আনয়নের ফলে, হাটে হাটে পণ্য-বানেরা (বা পাপীরা) তাদের পণ্যস্খালন করে পুণ্যবান হতে থাকেন। সেকালে সুবর্ণ বা gold money-কে ‘সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্রতা সম্পাদক পাদার্থ’ (১৭) বলা হ’ত এবং ‘পবিত্রতা সম্পাদক পাদার্থ’কে বলা হ’ত ‘পুণ্য’। পাপ বা পণ্যের হাত থেকে ওই প্রবাহই অবশেষে মানুষকে মুক্তি দেয়। লোকে নিজেদের পাপ বা পণ্যকে হাটে হাটে বা গঙ্গার তীর্থে তীর্থে বেচে দিয়ে পুণ্য বা সোনা অর্জ্জন করে। সেকালে যার ঘরে অনেক পণ্য জমে যেত, সমাজের চোখে সে ছিল পতিত। পণ্যধারা ওই অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি দেয় বলে, তার নাম হয় ‘পতিতপাবনী গঙ্গা’। মনে রাখা দরকার, ‘গঙ্গা’ শব্দটি থেকে ‘গাং’ কথাটি এসেছে; এবং এই ‘গাং’ ইউরোপে পৌঁছে ‘gang-way’ শব্দে পরিণত হয়েছে; যার মানে ‘বণিকপথ’ ।…তা সে যাই হোক, গঙ্গার সেই অপার মহিমার কথা রামায়ণাদিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে এই ক্ষুদ্র পরিসরে সে সবকিছুর ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কেননা আমাদেরকে এই মুহূর্তে জানতে হবে স্বর্গগঙ্গা ও মর্ত্ত্যগঙ্গাগুলির মিলের রহস্য কোথায়।
স্বর্গের নদনদী ও মর্ত্ত্যের নদনদী
সম্পদ আমাদের দুরকম, জাগতিক সম্পদ ও মানসিক সম্পদ। একটিকে কর্ম্মবিত্ত এবং অপরটিকে জ্ঞানবিত্ত বলা যেতে পারে। এই উভয় প্রকারের বিত্তকে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে বলে ‘ন’। অই ‘ন’ যে দান করে, তাকে বলে ‘নদ’। আর যেহেতু ‘কর্ম্মধারা’র মধ্যে জ্ঞানের পালন পোষণ চলে, তাই ‘কর্ম্মধারা’-সঞ্জাত প্রবাহগুলিকে বলে নদী।…
পুরাণশাস্ত্রকারগণ দেখেন, মানবসমাজে প্রবাহিত অদৃশ্য ধারাগুলি ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত দৃশ্য জলধারাগুলির অনুরূপ। অর্থাৎ স্বর্গীয় নদনদীগুলি যেন মর্ত্ত্যের নদনদীগুলিরই প্রতিচ্ছবি। আর, সেই সমস্ত প্রবাহগুলিই কোনও না কোনও প্রকারের ‘বিত্তদাতা’ (বা নদ) কিংবা ‘বিত্তদাতার ধাত্রী’ (বা নদী)। সেই বিচারে সমস্ত ধারাগুলিই মধুক্ষরণ করে। সে সকল কারণে, তাঁরা তাঁদের মানসদৃষ্ট অদৃশ্য নদ-নদীগুলির স্বভাবের ও রূপের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে ভূপৃষ্ঠের নদনদীগুলির নামকরণ করেন। প্রশ্ন হল ঃ কেমন সেই মিল? কেন সেই মিল? এবং কেনই বা পুরাণশাস্ত্রকারগণ ওইরূপভাবে নামকরণ করা দরকার বলে মনে করেছিলেন?
ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে পুরাণাদির পাঠ থেকে প্রাচীন ভারতের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তার থেকে জানা যায় যে, মানবসমাজে সর্ব্বাগ্রে প্রবাহিত ধারাটি হল জ্ঞান-জীবী-বুদ্ধিজীবিতার ধারা, যা ‘মানস সরোবর’ (১৮) থেকে তার যাত্রা শুরু করেছিল। এই ধারাটি বহন করত ব্রহ্মপুত্রেরা। তারপরেই, এর বিপরীত ধারার সূত্রপাত হয় ওই একই উৎস থেকে। সেটা পণ্যজীবী-বুদ্ধিজীবিতার ধারা, যা বহন করে ‘স্যন্দনস্বভাবাদ্যাভিমানি দেবগণ’ বা সিন্ধু। কাছাকাছি অঞ্চল থেকেই অতঃপর শত-শত-দ্রু বা শতদ্রু-ধারার উদ্ভব হয়। কিন্তু ঐ ইতিহাস অনুসারে, এই তিনটি ধারার উদ্ভব হয় সমাজের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানরূপে ‘আদি সমাজিক ব্যবস্থা’ বা ‘আদি সরকারি ব্যবস্থা’র উদ্ভবের আগেই। সেকালে সমাজের সকল ছাত্রদের বলা হত ‘উমা (উ মা=যাইয়ো না)’, সরকারি কর্ম্মীদের বলা হত ‘পার্ব্বতী’ এবং ওই সরকারি ব্যবস্থাকে ‘হিমালয়’ বলা হত। তার মানে আদিরাষ্ট্রের উদ্ভবের আগেই সমাজে জ্ঞানজীবী ও পণ্যজীবিদের আদি ধারাদুটির সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিল।
এবার এযুগের ভূবিজ্ঞানীদের বয়ান শুনুন।’… সাধারণত জলবিভাজিকার (Water-shed or Water Parting), দুদিকের ঢাল দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। কিন্তু উত্তর ভারতের সিন্ধু ও শতদ্রু এবং উত্তরপূর্ব্ব ভারতের ব্রহ্মপুত্র, এই তিনটি নদী অই অঞ্চলের জলবিভাজিকা হিমালয়কে আড়াআড়িভাবে কেটে ভারতে এসেছে। এরকম হবার কারণ, ভূবিজ্ঞানীদের অনুমান, হিমালয় উৎপত্তির আগে থেকে নদী তিনটির ওই গতিপথ ছিল। হিমালয়ের ধীরে ধীরে উথ্থানের সঙ্গে সঙ্গে নদী তিনটিও সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষয়কার্য করে আগের গতিপথ বজায় রেখেছে। সুতরাং সিন্ধু, শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্র হল ‘পূর্ববর্ত্তী নদী’ (Antecedent River)।’ – (ড. গৌতম মল্লিক/ভু-পরিচয়)
কিংবা ধরা যাক গঙ্গার কথা। পুরাণকারগণের মতে এটিকে ‘আনয়ন’ করা হয়, অর্থাৎ বাণিজ্যিক পণ্য-স্রোত সমাজে আপনি আপনি প্রচলিত হয়ে যায়নি। তার জন্য বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল, সুদীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল; প্রচুর শ্রম বা তপস্যা (১৯) করতে হয়েছিল। সে সবের বিস্তারিত বিবরণ সবাই জানেন, প্রয়োজন কেবল সেই বিবরণকে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে বুঝে নেওয়া। সেই বিস্তারে না-গিয়ে এই মূল সিদ্ধান্তটি সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া যেতে পারে যে, বাণিজ্যিক পণ্যপ্রবাহ বলতে গেলে গায়ের জোরেই সমাজে চালু করতে হয়েছিল। অর্থাৎ গঙ্গা হল manmade, কৃত্রিম প্রবাহ।
এবার এযুগের নদীবিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্য শোনা যাক। তাঁদের কারো কারও মতে, গঙ্গা নদীর সার্ভে রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, সমুদ্রতল থেকে তার প্রবাহপথের উচ্চতা নাকি ক্রমশ নিম্নমুখী না-হয়ে কোথাও কোথাও উঁচুর দিকেও গিয়েছে। প্রাকৃতিক নদীর ক্ষেত্রে নাকি এমন হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব কেবল মানুষের তৈরী মানুষের কাটানদীনালার ক্ষেত্রে। এসব দেখে শুনে এক ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার নাকি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, নিশয়ই প্রাচীন ভারতবাসী এই নদী খনন করেছিল, কতকগুলি নদীকে জুড়ে একই পথে প্রবাহিত করবার জন্য। সিদ্ধান্তটি পরবর্ত্তীকালে বহু নদীবিশেষজ্ঞ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
সুতরাং, ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত নদনদী ও সমাজে প্রবাহিত নদনদীসমূহের একপ্রকার সমস্বভাব ও সমরূপিতা বিদ্যমান রয়েছে। আর ওই সমরূপিতা কেবল যে ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু শতদ্রু ও গঙ্গার ক্ষেত্রেই রয়েছে, এমন নয়। প্রায় সমস্ত নদনদীর প্রচলিত মিথসমূহ, জনসমাজে তৎসংস্লিষ্ট আচার-আচরণ এবং সর্ব্বোপরি পুরাণাদিতে সেগুলি সম্পর্কে প্রদত্ত বিস্তারিত বিবরণ ও কাহিনীগুলির যথাযথ পাঠ থেকে আমরা সমাজে প্রবাহিত ধারাসমূহের যে ইতিহাস ও চিত্র পাই, আধুনিক নদীবিশেষজ্ঞদের ভূপৃষ্ঠবাহিনী নদী সংক্রান্ত ইতিহাস ও চিত্রের সঙ্গে সেগুলি মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কাজটি বিশাল এবং একজনের পক্ষে করণীয়ও নয়, অনেকে মিলে করতে হবে এবং করা যাবেও। তাতে দৃশ্যধারা-সংক্রান্ত জ্ঞান ও অদৃশ্যধারা-সংক্রান্ত জ্ঞান পরস্পরের ঘাটতি পূরণ করে দেবে। যেমন উপরোক্ত ব্যাখ্যা জানিয়ে দিল যে, ব্রহ্মপুত্র সিন্ধুর চেয়েও প্রাচীন, গঙ্গার জন্ম তারও পরে। ভূবিজ্ঞানীরা এখনও সেকথা জানেন কী? না জানলে এবার তাঁরা সেটি আবিষ্কার করে নিতে পারেন।
উপরোক্ত উপলব্ধি থেকে, অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, সমাজে সৃষ্ট অদৃশ্য প্রবাহগুলির নক্সা ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত ধারাগুলির নক্সার অনুরূপ তো বটেই, জগতে যত লোক বিদ্যমান, তা সে ত্রিলোক-ত্রিভুবন হোক কিংবা চতুর্দ্দশ ভুবনই হোক, প্রত্যেক লোকের প্রবাহিত ধারাসমূহের নক্সা যে-কোনও এক লোকের (স্ফীয়ার-এর) ধারাসমূহের অনুরূপ। সেকারণেই আমরা প্রাকৃতিক ‘ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু-মানসসরোবর ইত্যাদি’র সঙ্গে মানসিক ‘ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু-মানসসরোবর ইত্যাদি’র এমন মিল দেখতে পাচ্ছি। সেকারণেই প্রাকৃতিক বৃক্ষের ইতিহাসের সঙ্গে সামাজিক বৃক্ষের (সঙ্গঠনের) ইতিহাসকে আমরা সমান্তরাল দেখছি। সেকারণেই প্রাকৃতিক ‘পক্ষী-মৎস্য-পশুর বিকাশের ইতিহাসে’র সঙ্গে সামাজিক ‘পক্ষী-মৎস্য-পশুর বিকাশের ইতিহাস’কে আমরা সমান্তরাল দেখি।…কিন্তু কেন যে তারা এই নিয়ম মেনে চলে, তা আমরা জানি না; ঠিক যেমন বিজ্ঞানিরা আজও জানেন না কেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অঙ্ক মেনে চলে।
তার মানে প্রত্যেক লোকের বিকাশ ঘটেছে একই নিয়ম ও নক্সা অনুসরণ করে। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সেকথা কতখানি বুঝেছিলেন, সে ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে এখনও আমি জানতে পারিনি। তবে এব্যাপারে যে তাঁরা কমবেশী অবহিত ছিলেন, তার কিছু প্রমান মেলে তাঁদের ‘আঠাশ প্রকার বিপর্য্যয়’-এর বিবরণ এবং ‘জগৎ-সৃষ্টি’ অধ্যায়ের কিছু কিছু ব্যাখ্যা থেকে। উত্তরাধুনিক বিজ্ঞান ওই ব্যাপারটিকেই কোয়ান্টাম জগতে ধরার চেষ্টা চালাছে ‘স্ট্রিং থিয়োরি’র মাধ্যমে। ওই সব অনুমান যদি সত্যি বেরোয়, তাহলে বলতেই হবে বিচূর্ণিভবনের অঙ্কটি সর্ব্বত্রই একপ্রকার।
অর্থাৎ মানুষ যে বিচূর্ণীভূত হয়ে জ্ঞানজীবী, পণ্যজীবীর সমর্থক জ্ঞানজীবী, নানা শ্রেণীর পণ্যজীবী, শ্রমজীবীতে পরিণত হয়েছে; সেই অঙ্কেই বায়বীয় জলীয় কঠিন বস্তুজগতের বিচূর্ণীভবন ঘটেছে। একই নিয়মে ও নক্সানুসারে মৎস্য অজস্র মৎস্য-প্রজাতিতে, বৃক্ষ অজস্র বৃক্ষ-প্রজাতিতে, পক্ষী অজস্র পক্ষী-প্রজাতিতে বিচূর্ণিভূত হয়েছে – ঘটনাটি একই ভাবে ঘটেছে মানসজগতেও। একটি আংশিক ও হাইপোথিটিক্যাল সারণীর সাহায্যে বিষয়টির ইঙ্গিত রাখা যাক।
মূলধারা ১নং ধারা ২নং ধারা ৩নং ধারা ৪নং ধারা
সৃষ্টিধারা -> মানবধারা পশুধারা পক্ষীধারা বৃক্ষধারা..
১নং মানবধারা -> জ্ঞানীধারা শ্রমিকধারা দোকানদারধারা গৃহস্থধারা … ->
২নং পশুধারা -> সিংহধারা বাঘধারা ভালুকধারা হরিণধারা … ->
৩নং পক্ষীধারা -> শকুনধারা চিলধারা বাজধারা পায়রাধারা… ->
৪নং বৃক্ষধারা -> অশ্বথ্থধারা বটধারা শালধারা সেগুনধারা… ->
৫নং মৎস্যধারা -> কাৎলাধারা রুইধারা মৃগেলধারা ইলিশধারা… ->
৬নং জলধারা -> ব্রহ্মপুত্রধারা সিন্ধুধারা শতদ্রুধারা গঙ্গাধারা … ->
পুরাণকারগণ এরকম কোনও সারণী তৈরী করেননি, কিংবা করে থাকলেও আমার চোখে এখনও পড়েনি। তাসত্ত্বেও তাঁরা নদনদীর সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলিয়ে ভূপৃষ্ঠবাহিনী দৃশ্যনদীগুলির নামকরণ করে যেতে পারলেন , সেটা সম্ভব হয়েছিল যে সকল কারণে, তার অন্তত তিনটি কারণ খুবই সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়; (ক) তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, জলধারাসমূহ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ধারাসমূহ সম-স্বভাবের, অর্থাৎ তারা সমজাতীয় ক্রিয়ার কারক। তাঁদের হাতে ছিল ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা। তার সাহায্যে তাঁরা এক বর্ণনায় দুই প্রকার ধারার কথাই বলে দিয়ে যান। (খ) মানসিক ভূগোলের সঙ্গে মিলিয়ে পার্থিব ভূগোল বর্ণনা করবার একটি রীতি ইতোমধ্যে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, যাতে নিম্ন-অধিকারিগণ নক্সাটি নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বহন করতে পারে। (গ) ধারাসমূহের সন্ধিস্থলগুলি তাঁদের নজরে পড়ে গিয়েছিল; যেমন বট=বেনিয়া >Banian Tree>=পক্ষী…ইত্যাদি, কিংবা অশ্বথ্থ=বেদজীবী=ব্রহ্মপুত্র …ইত্যাদি। তবে পরবর্ত্তীকালের নিম্ন-অধিকারিদের হাতে পড়ে ওই বর্ণনার কী হাল হয়েছে, তা আর বলে শেষ করা যাবে না। লোকে গঙ্গায় ডুব দিয়ে পুণ্য অর্জ্জন করেই ক্ষান্ত হয়নি, পিতৃপুরুষের ছাই নিয়ে গিয়ে ওই গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়েছে; কোন কারণে গঙ্গাতীর্থে যেতে না-পারলে গঙ্গাজলপায়ী ব্যক্তিকে ওই ছাই খাইয়ে তবে মানসিক শান্তি লাভ করেছে। তা সে যাই হোক, প্রশ্ন হল: এই নদনদীদর্শন থেকে আমরা কী পেলাম?
ইউরোসেণ্ট্রিক ও প্রাচ্যের নদনদী-দর্শনের মিলিত পুণ্যফল
ইউরোসেণ্ট্রিক রিভার-দর্শন অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্টভাবে ভূপৃষ্ঠের নদীসমূহ আমাদের দেখিয়েছে। আমরা জেনেছি, পৃথিবীতে উপনদী শাখানদী মিলিয়ে মোট প্রাকৃতিক নদীর সংখ্যা কত, তারা বছরে মোট কত জল বহন করে (২০), …ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রাচ্যের নদনদীদর্শন করতে গিয়ে আমরা জেনেছি, ওইরূপ নদনদীসমূহ কেবল ভূপৃষ্ঠেরই প্রবাহিত নয়, সর্ব্বলোকেই প্রবহমান। চিন্তার অজস্র ধারা; সাহিত্যের, দর্শনের, বিজ্ঞানের, অর্থনীতির, সংস্কৃতির, ঐতিহ্যের, গানের, নাচের, ধর্ম্মের, ভাষার – হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রবাহ। কর্ম্মেরও অজস্র ধারা; চাষাবাদের, কাপড় বোনার, সেলাইয়ের, শিল্প-উৎপাদনের, গৃহনির্ম্মানের, কারুশিল্পের – হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ধারা। এই যে বইটি আপনি পড়ছেন, সারা পৃথিবীতে ওইরকম কত বই নিয়মিত প্রকাশিত হয়? অর্থাৎ বইয়ের প্রজাতিধারার মোট সংখ্যাটি কত? অবশ্যই কয়েক কোটি। তাহলে, জগতের দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত ধারাসমুহের মোট পরিমানটা কত?
দুটি প্রশ্নের উত্তর থেকে ওই পরিমাণটির একটা আন্দাজ দেওয়া যেতে পারে। (ক) পৃথিবীতে মোট কত জাতের গম উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ গম নামক দানাশস্যটির প্রজাতিধারার মোট সংখ্যাটি কত ঃ – উত্তর হল, ৯৫০,০০০। (মনে রাখা ভালো, প্রত্যেক প্রজাতির গম চাষের জ্ঞানটিও মানবমস্তিষ্কে প্রবাহিত হতে থাকে)। (খ) এখন পৃথিবীতে মোট কত প্রজাতির উদ্ভিদ জন্মায়? – উত্তর হল, ২,৪২,০০০। (২১)। এই উদ্ভিদসমুহের প্রত্যেকের আবার ওই গমের মতো যদি কয়েক লাখ উপ-প্রজাতিধারা (বা শাখানদী) হয়, তাহলে জগতে প্রবাহিত ধারাসমূহের সর্ব্বমোট সংখ্যাটি কত হতে পারে? উত্তর হল: কোটি কোটি কোটি…অগণ্য। তার ওপর রয়েছে প্রায় সমপরিমাণ মানসধারা।
এ ধারাগুলি কী করে? মানুষের বিচারে ‘মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ’ অর্থাৎ তারা মধু ক্ষরণ করে, বিত্ত দান করে। তাতে কী হয়? জড়জগতের, জীবজগতের ও মানবসমাজের অহিত বিনাশ হয়।
তাই যদি হবে, তাহলে আমাদের চারদিকে এত অহিত কেন? অশুভের রমরমা কেন? জীবন অতিষ্ঠ কেন? তাহলে এখনও পৃথিবীতে ১০০ কোটি মানুষের পানীয় জলের অভাব কেন? ১৩০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে কেন? (২১)। …তাহলে কি ওই ধারাগুলি আর জলবহন করছে না, মধুক্ষরণ করছে না, বিত্তদান করছে না? নাকি মধুক্ষরণের পথে কোথাও কোনও বাধার সৃষ্টি হয়েছে (যে ধারাগুলিই আমাদের প্রাণ)? সুতরাং প্রাণ বাঁচানোর জন্যই আমাদের জানা দরকার, ওই ধারাগুলির, ওই নদনদী-সমূহের বর্ত্তমান প্রবাহ ঠিকঠাক আছে কি না। না-থাকলে কেন নেই? কেন নেই, সেকথাই এখন আমরা জানব। এই নদনদীদর্শনের সেই পুণ্যফল।
যে কোনও নদীর দু’টি পাড় থাকে। ওই পাড়, বলতে গেলে, নদীর নিজের সৃষ্টি, ন্যাচারাল, স্বাভাবিক। প্রাগাধুনিক মানুষ প্রকৃতির ওই পাড়-সৃষ্টির বিপরীতে না গিয়ে, বরং ওই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়ে, ন্যাচারাল পাড় বরাবর উঁচু করে রাস্তা বানাত। সেই কারণে, প্রায় সব নদীর দুই তীর বরাবর দুইখানি সমান্তরাল রাস্তা বা বাঁধ দেখা যায়। এগুলি নদীকে তার প্রাবাহপথে যথারীতি প্রবহমান থাকতে সহায়তা করে থাকে। ওই রাস্তায় শত শত ‘লকগেট’ বা ‘পোল’ বানিয়ে তার মাধ্যমে ওই নদীর জল নেওয়া হত, যেখানে যেমন প্রয়োজন। সমস্ত অদৃশ্য নদনদীর ক্ষেত্রেও ওইরকম দুইটি পাড়ের ব্যবস্থা দেখা যায়। একটি পাড়কে বলে উর্দ্ধসীমা এবং অপরটিকে বলে নিম্নসীমা। ওই দুই সীমার মাঝ বরাবর ‘দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়।’ একথা চিন্তাধারাসমূহের ক্ষেত্রেও খাটে, খাটে সমস্ত সৃষ্টিধারার ক্ষেত্রেই।
কিন্তু সকল মধুক্ষরণকারী ধারা সম্পর্কেই মানুষের একটি অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়। সে তাদের যেমন খুশী যখন খুশী পান করতে পারে না, ব্যবহার করতে পারে না। ঠিকসময়ে ঠিক মাত্রায় পান করলে ওই ধারা যেমন তার পক্ষে ‘প্রাণ’দানকারী হয়, তেমনি অসময়ে বেঠিক মাত্রায় পান করলে সেটাই দেখা দেয় যমদূতরূপে অর্থাৎ মানুষের পক্ষে ধারাগুলির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে। ইতোমধ্যে আধুনিকতা মানুষকে এই বিশ্বাস যুগিয়ে দেয় যে, সে প্রকৃতির উপর রাজত্ব চালাতে পারবে; অতএব ওই সকল ধারাগুলিও নিয়ন্ত্রণযোগ্য। Part cannot conquer the whole – এই স্বতঃসিদ্ধটিকে, তার মনে হল, অবান্তর। স্বভাবতই, আধুনিক মানুষ গেল ওই ধারাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সেই নিয়ন্ত্রণের উপায়রূপে সে ওই ধারাসমূহের সামনে ‘বাঁধ’ বাঁধার সিদ্ধান্ত নিল। তার বিশ্বাস জন্মাল, ওই সকল ধারাসমূহের সামনে বাঁধ বেঁধে, সে ওইগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং যহাসময়ে যথাবিহিত মধুগ্রহণ ও পান করতে পারবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে, আধুনিক মানুষ দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত নদনদীসমূহের সামনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাঁধ বেঁধে বসে আছে। আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত অহিতের মূলে ওই বাঁধসমূহ।
পৃথিবীতে বাঁধ বাঁধার বুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে আবিষ্কার করে মন্দিরকেন্দ্রিক পুরোহিত পরিচালিত বৈদিক সভ্যতা। প্রথম বাঁধটি সে বাঁধে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানপ্রবাহের উপরে, শূদ্রের বেদপাঠ নিষিদ্ধ করে। এরপর সে বাঁধ দেয় উৎপন্নধারার মুখের এবং সেই বাঁধের সাহায্যে ওই উৎপন্নধারা কোন কোন দিকে কী পরিমাণে প্রবাহিত হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। ওই নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র ছিল তাদের মন্দিরগুলি। ফলে, মানবসমাজে মন্দিরসমূহই ‘আদি-বাঁধ’ রূপে দেখা দিয়েছিল। মানুষের জীবনপ্রবাহ, আচারধারা, বংশধারা, ঐতিহ্যধারা, মোট কথা সর্ব্ববপ্রকারের মানবিক কর্ম্মধারা ও চিন্তাধারার উপর ওই মন্দিরগুলির কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এর ফলে, ধারাসমূহের ক্ষরিত মধুর সিংহভাগ চলে যায় মন্দিরের ‘সেবাইত’ পুরোহিতদের হাতে। বাকী মানুষেরা ওই প্রবাহের মধুক্ষরণ স্পর্শ করবার অধিকার হারিয়ে বঞ্চিত হয়ে যায়। বহু মানুষ বিতাড়িত হয় বনে জঙ্গলে মরুপ্রান্তরে দুর্গম অরণ্যে পর্ব্বতে সমুদ্রোপকূলে। মন্দিররূপী বাঁধগুলিকে মানুষ অতিক্রম করতে পারে না।
এক সময় বিদ্রোহ দেখা দেয় স্বাভাবিক নিয়মেই। বিদ্রোহিরা, যেখানে যেখানে সম্ভব, ওই মন্দিরগুলি ভেঙে ফেলে বটে, কিন্তু তার বদলে নতুন বাঁধরূপে মঠ,গির্জ্জা,মসজিদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে বসে। বলতে গেলে, মন্দিররূপী বাঁধগুলি অক্ষতই থাকে, কেবল সেবাইত বদলে যায়। এরপর নতুন বাঁধরূপে দেখা দেয় রাষ্ট্র। মন্দির মসজিদের পুরোহিত মোল্লাদের কর্ত্তব্য এবার বর্ত্তায় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাঁধে। বাঁধ বাঁধার, পুরোনো বাঁধগুলিকে অক্ষত রাখার দায়িত্ব ও অধিকার ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়। আগের বারের ভুল-ত্রুটিগুলিকে পরের বার সংশোধন করে নতুন নতুন সামাজিক ‘নর্ম্স্’ গড়ে তোলার যে স্বাভাবিক বিশুদ্ধির প্রবাহ, তার উপর মহাবাঁধ নির্ম্মাণ করল মন্দির-মসজিদের সেবাইতরা এবং তাদের নিযুক্ত রাষ্ট্রসমূহ। বেদ-বাইবেল-ত্রিপিটক-কোরান সবই অপৌরুষেয় অলঙ্ঘনীয় হয়ে গেল। আর সেবাইতরা সর্ব্বধারার মধুক্ষরণের সিংহভাগ ভোগদখল করতে লাগলেন।
অতঃপর, স্বর্গগঙ্গা যেমন একদিন মর্ত্ত্যে নেমে আসে, তেমনি স্বর্গের ওই বাঁধগুলিও একদিন মর্ত্ত্যে নেমে এল। অদৃশ্য নদনদীর উপর বাঁধ বাঁধবার বুদ্ধিও নেমে এল, নেমে এলেন স্বর্গলোকের পুরোহিত-মোল্লারা, রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা। এবার মর্ত্ত্যের দৃশ্য ধারা-সমূহের সামনে, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠবাহিনী নদীসমূহের সামনেও দৃশ্য বাঁধ বাঁধার পরিকল্পনা নেওয়া হল। এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল যাতে ওই বাঁধগুলি একদিকে আধুনিক পুরোহিত-মোল্লাদের অর্থাৎ রাজপুরুষদের, শাসকদের, নিয়ন্ত্রকদের বিপুল পরিমান মধুপানের সুযোগ করে দেয়; অপরদিকে নিয়মিতভাবে খরা ও বন্যা সৃষ্টি করে সমস্ত শাসিত দেশবাসীকে সর্ব্বদা ‘সাহায্য-প্রার্থনাকারী’তে পরিণত করে রাখে। নিজেদের জান মাল বাঁচাতে তারা যেন এমন জেরবার থাকে যে, ওই খরা-বন্যার কারণ খুঁজবার অবকাশ পর্য্যন্ত না-পায়। উদ্ভুত পরিস্থিতিকে তারা যেন ‘ভাগ্য’, ‘ভবিতব্য’, ‘ঈশ্বরের অনিবার্য্য অভিশাপ’ ইত্যাদি ছাড়া অন্য কিছুই না-ভাবে। সর্ব্বোপরি, প্রাচীনকালের মন্দিররূপী বাঁধগুলি যেমন হাজার হাজার মানুষকে বিতাড়িত করে; যাতে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও পাথুরে এলাকাসমূহকেও আধুনিক পুরোহিত-মোল্লাদের ভোগদখলে আনতে পারা যায়। মোটকথা, মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য রাজভোগের ব্যবস্থা, বেশীর ভাগ মানুষকে বোকা বানানো ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে রাখা এবং কিছু মানুষকে উদ্বাস্তু করা, বিতাড়িত করা – প্রাচীন ভারতের মন্দিরসমুহের এই তিনটি কাজই আরও সুষ্ঠ ও নিখুঁতভাবে এই পার্থিব বাঁধগুলি সেরে ফেলতে পারবে; এমনি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। আর, সেই কথাটা একদিন স্বাধীন ভারতের রূপকার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তিনি বলে বসলেন: ‘বাঁধগুলি হল স্বাধীন ভারতের মন্দির’।
দেখতে দেখতে সারা ভারতের দৃশ্য নদীগুলির উপর ৩৬০০টি বাঁধ বেঁধে ফেলা হল এবং আরও ১০০০-টি বাঁধের নির্ম্মান কাজ চলতে লাগল। প্রতিটি বাঁধ মুষ্টিমেয় সেবাইত-পুরোহিতদের ‘গৌরী সেন’ হয়ে গেল – লাগে টাকা, দেবে বাঁধ। পঞ্চাশ বছরে ওই বাঁধের নামে আশী হাজার কোটি টাকা ওই পুরোহিত-মোল্লারা ভাগ বাঁটোয়ারা করে খেয়ে ফেলল। বরাদ্দ রইল আরও আশী হাজার কোটি। প্রাচীন ভা্রতে সামাজিক কর্ম্মযজ্ঞের নামে পুরোহিতেরা বছরের পর বছর ধরে ভূরি ভূরি দক্ষিণা চুষে নিতে পারত বলে ওইগুলিকে বলা হত ‘দীর্ঘকালিন যজ্ঞ’ বা ‘ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ’। বর্তমানে এই বাঁধগুলিই তাদের ভূরিদক্ষিণযজ্ঞ ও পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনা (বছরের পর বছর চলতেই থাকে, শেষ আর হয় না) হয়ে গেল।
আর খরা-বন্যা? বিগত পঞ্চাশ বছরে সারা ভারতে খরা-বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির মোট পরিমাণ কেউ জানে না। সব ব্যাপারে ভারত সরকারের পরিসংখ্যান আছে; এ ব্যাপারে নেই। থাকলেও সেকথা কেউ জানে না। গোপনীয় সরিকারী তথ্য – কাউকে জানতে দেওয়া যা্বে না। কেউ কেউ অনুমান করেন, অঙ্কটি হবে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। আর বিতাড়ণ? বাঁধের সেবাইতদের হিসেবেই সংখ্যাটি ৫ কোটি। প্রকৃতসংখ্যা নিঃসন্দেহে বহু বহু গুণ বেশী। মনে রাখা ভালো, যে-কোসোভোতে আমেরিকান বোমাবাজি নিয়ে এত চেঁচামেচি; সেখানে উৎখাত হয়েছিল মাত্র ১০ লক্ষ মানুষ। তাতেই সারা পৃথিবীতে ছিছিক্কার পড়ে গিয়েছিল । ভারতরাষ্ট্রের পুরোহিতেরা যে গত ৫০ বছরে তাদের হিসেবেই ৫ কোটি মানুষকে চুপিসাড়ে তাদের মাটি থেকে, তাদের সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধন থেকে, বাঁচবার নিজস্ব পদ্ধতি থেকে সমুলে উপড়ে উচ্ছেদ করে উদ্বাস্তু করে দিয়েছে; সেকথা কেউ জানে না। আরও আছে। কখনও চার কোটি লোকের পানীয় জল কেড়ে নেবার জন্য বাঁধ বানাও, তো কখনও আর চার কোটি লোককে পানীয় জল জোগাবার ভান করে বাঁধ বানাও’ (২২)। মোট কথা বাঁধ আমাদের চাই। বাঁধ আমাদের মন্দির। আমরা সে মন্দিরের সেবাইত, তোমরা তার সেবাদাস। তাই তোমাদের মন্দিরে উঠতে মানা, ওই মন্দিরের ভিতর কী চলছে তা জানতে মানা। ইয়ে রাজ-কি বাত্ হ্যায়। সত্যগোপন না-থাকলে আধুনিক পুরোহিত-তন্ত্রেরও রাজত্ব থাকে না।
সারা দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য নদনদীসমূহের সামনে বাঁধ বেঁধে মুষ্টিমেয় মানুষের সুবিধার জন্য জেনে শুনে এত বিশাল ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা চালানো হয়েছে, হচ্ছে, একথা অনেকেই বিশ্বাস করতে চান না। এর থেকে প্রমাণিত হয়, ভারতীয় উপমহাদেশে ভালোমানুষের সংখ্যা এখনও বিস্তর। আর সেই সুযোগ নিয়ে ওই বাঁধ-সেবাইতরা এতবড় কাণ্ড ঘটিয়েও তা গোপন করে রাখতে পেরেছে। গোপন রাখার উপায় স্বরূপ তারা হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে যে লোক-দেখানো প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করছে, সেগুলির উপর ‘রূপায়ন-উত্তর গবেষণা’ নিষেধ করে রেখেছে। ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে কোনও ছাত্রকে তাই কোনও রূপায়িত-প্রকল্পের উপর গবেষণা করে ডক্টরেট করতে দেওয়া হয় না; কোনও ছাত্র বা অধ্যাপক চাইলেও দেওয়া হয় না। এ ব্যাপারে খোদ প্রধানমন্ত্রীর নিষেধমূলক লিখিত ‘ডাইরেক্টিভ’ রয়েছে’ (২৩)। কেননা, তাহলে ভারতীয় জনগণের জীবন ও অর্থ নিয়ে ওই সেবাইতরা কতখানি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তার সব ‘রাজ কি বাত্’ বেরিয়ে পড়বে; তাদের রাজত্বই ধসে পড়বে। কেননা, তথ্যগোপন রাখাই রাজত্ব বজায় রাখার শেষ উপায়। রাজত্ব মানেই তথ্যগোপন, সত্যগোপন। তাই ‘রাজ-কি-বাত’ই গোপন কথা, রাজত্বের কথা।
বিশ্বের অগ্রণী দেশগুলি ইতোমধ্যে হিসেব করে দেখে ফেলেছে, ওই বাঁধগুলি যতখানি লাভ দেয়, লোকসান করে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। তাঁরা বুঝে গেছেন, বাঁধ বাঁধা মানে দেশের মানুষগুলোকে হাত-পা বেঁধে একপাল শকুনের সামনে অসহায় ফেলে দেওয়া। নিজেদের দেশের মানুষদের প্রতি এমন ব্যবহার করতে তাঁদের হৃদয়ে বেধেছে। তাই তাঁরা তাঁদের কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে নির্ম্মিত বাঁধগুলি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন, দিচ্ছেন। দৃশ্য নদীগুলির উপরের দৃশ্য বাঁধগুলি ভাঙতে ভাঙতে তাঁদের অদৃশ্য নদীর উপর প্রতিষ্ঠিত বাঁধগুলিও তাঁরা ভাঙতে শুরু করেছেন এক এক করে। তাঁরা এই কাজটির নাম দিয়েছেন – ‘Crossing the borders and blurring the boundaries’। অঙ্কটি এভাবেই কার্য্যকরী হবে, প্রকৃতির বিধান। ‘অনুলোমে যার উদ্ভব, প্রতিলোমে তার সংহার’ (২৪) – অর্থাৎ ফার্স্ট কাম লাস্ট গো। শুরুর বেলায়, আগে অদৃশ্য বাঁধগুলি এবং শেষে দৃশ্য বাঁধসমূহ আর বিলোপের বেলায় আগে দৃশ্য বাঁধের পালা, শেষে অদৃশ্য বাঁধের পালা।
কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশ হল ‘হৃদয়বান’দের দেশ। এখানকার আধুনিক পুরোহিত-মোল্লাদের বিচারে, দেশের মানুষগুলোকে ওরকম হাত-পা বেঁধে শকুনের সামনে অসহায় ফেলে দিলে এমন কিছু হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে না; বরং তাতে পুণ্য হয়। কারণ শকুন তো বাঁধের সেবাইত ওই আধুনিক পুরোহিত-মোল্লারাই। সেই কারণে, বাঁধগুলিকে তাঁরা কেবল অক্ষতই রাখেন না, নতুন নতুন বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনাগুলিকেও অব্যাহত রাখেন। ফলে, ভারতীয় উপমহাদেশে দৃশ্য-অদৃশ্য নদ-নদীগুলি কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য মধুক্ষরণ করছে, তাদের প্রাণ দান করছে, বাকী সমগ্র দেশবাসীর কাছে দেখা দিচ্ছে যমদূতরূপে। মানুষের জীবন এখানে তাই চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত।
তবে এবার বুঝি দিনবদলের পালা শুরু হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ ভাঙা ‘সবচেয়ে দুঃসাধ্য যখন হয়, তখনই তাঁর (ভাঙবার জন্য ভৈরবের জেগে উঠবার) সময় আসে’ (মুক্তধারা)। নর্ম্মদা প্রকল্প সেই দুঃসাধ্য সময়টিকে চিহ্নিত করছে। এই মহাবাঁধ থেকেই শুরু হবে বাঁধ ভাঙার সূত্রপাত।
নদনদী বিষয়ে অধুনান্তিক বিবেচনা ঃ ভেঙে দাও বাঁধ, জুড়ে দাও ধারা
‘কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন / চারিদিকে তার বাঁধন কেন!
ভাঙ্রে হৃদয় ভাঙ্রে বাঁধন, / সাধ্রে আজিকে প্রাণের সাধন,…
ওরে চারিদিকে মোর এ কি কারাগার ঘোর
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর।’ – (রবীন্দ্রনাথ)
নিষ্প্রাণের বুকের ভিতর থেকে প্রাণের ধারাস্রোতসমূহ নিত্য উৎসারিত হচ্ছে। তাই, বিশ্বজগতে যত প্রকার নদ-নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তা সবই প্রাণ-বান্ধব, ‘লাইফ-ফ্রেণ্ডলি’। নানাভাবে ওই স্রোতধারাসমূহ আজ বাধার সম্মুখীন, কারারুদ্ধ। একদিন রবীন্দ্রনাথ ওই স্রোতধারাসমূহের গতিরোধকারী বাঁধসমূহ দেখতে পেয়ে যান, নিজের অন্তরের মধ্যে বিশ্বের ওই প্রাণধারাসমূহের রুদ্ধবেদনা অনুভব করে ফেলেন, তাদের প্রবাহিত হবার আকুল আকাঙ্ক্ষাকে উপলব্ধি করে বসেন। সেই উপলদ্ধিই তাঁকে বিশ্বের সমস্ত বাধাবন্ধনগুলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে প্ররোচিত করে। সেই প্ররোচনাতেই তিনি ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’-র গান গেয়ে ওঠেন। তারপর ওইসকল দৃশ্য-অদৃশ্য বাঁধগুলির প্রকৃত রহস্য অনুধাবন করে লেখেন ‘মুক্তধারা’ নাটক। সেই নাটকের পরিণতিতে তিনি সবাইকে ওই সকল বাঁধ ভেঙ্গে দেবার জন্য আহ্বান জানান ‘বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও’ – গান গেয়ে গেয়ে।
বাঁধগুলি তো ভেঙে পড়বেই, লোকে সেগুলি ভেঙে দিতে বাধ্য করবেই; আজ না হয় কাল। সারা পৃথিবী ইতিমধ্যে যে-সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আজ হোক কাল হোক, ভারতকেও সেই সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। ভারতে মেধা পাটকরেরা যে-লড়াই চালাচ্ছেন, সে-লড়াইকে গুঁড়িয়ে দিলেও, কিছু করার উপায় নেই ঃ বাঁধগুলি ভেঙে ফেলতে হবেই, দু’দিন আগে কিংবা দু’দিন পরে। তবে মানুষের পৃথিবী তো বহু কুকীর্তির সাক্ষী। যিশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে ঝুলিয়ে দেবার পর, দেখা যায়, সিংহাসন স্বয়ং যিশুর ধর্ম্মকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে এবং খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। মেধা পাটকরদের নিঃশেষ করে দিয়ে, দেখা যাবে, বাঁধের সেবাইতরাই বাঁধ ভাঙতে উঠে পড়ে লেগেছে; যাতে বাঁধ গড়ার সেবাইতগিরি করে যে সুবিধাজনক অবস্থানে তারা ছিল, বাঁধ ভাঙার সেবাইতগিরি করে সেই একই সুবিধাজনক অবস্থানে তারা থাকতে পারে। সেবাইতগিরিটি যেন তাদের অক্ষুন্ন থাকে।
তা সে যাই হোক, এভাবে প্রথমে দৃশ্য বাঁধগুলি এবং পরে অদৃশ্য বাঁধগুলি না হয় এক এক করে ভেঙে ফেলা হল। কিন্তু তারপর? যে সমস্যা থেকে মানুষ বাঁধ বাঁধতে গিয়েছিল, সেই সমস্যা তো থেকেই যাবে। ধারাসমূহের ‘প্রাণদা-যমদূতিকা’ স্বভাবটিকে সামলানো যাবে কেমন করে?
আমরা দেখেছি, আগে অদৃশ্য বাঁধ বাঁধা শুরু হয় স্বর্গগঙ্গাগুলিতে অর্থাৎ অদৃশ্য ধারাগুলিতে; তারপর দৃশ্য বাঁধ বাঁধা হয় দৃশ্যজগতের ধারাগুলিতে। ধ্বংসের বেলায় প্রথমে ভাঙে দৃশ্য বাঁধসমূহ, তারপরে অদৃশ্য বাঁধসমূহের পালা। তার পরিবর্ত্তে নতুন কোনও ব্যবস্থার উদয় হলে, সর্ব্বাগ্রে সেগুলির সূত্রপাত হবে অদৃশ্য ধারাগুলির ক্ষেত্রে, তারপরে সেই ব্যবস্থা নেমে আসবে মর্ত্ত্যে, দৃশ্য জগতে। তো অদৃশ্য ধারাসমূহের ক্ষেত্রে বাঁধের পরিবর্ত্তে নতুন কোনও ব্যবস্থার কি কোনও ইঙ্গিত পাওয়া গেছে?
হ্যাঁ। অদৃশ্য ধারাসমুহের জগতে, দেখা যাচ্ছে, বর্ডার ও বাউণ্ডারিগুলিকে অকেজো করে দিয়ে, ধারাগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও এর নাম দেওয়া হচ্ছে ‘Inter-subjectivity’, কোথাও বা এর নাম ‘ইন্টারবিয়িং হওয়ার চেষ্টা’, কোথাও বা ‘কর্পোরেট কালচার’। চিন্তাধারার বহুধাবিভক্ত শাখাগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে – ‘Synthesizing knowledge from the gamut of disciplines’ অর্থাৎ কিনা বাঁধগুলি ভেঙে দিয়ে বা অকেজো করে দিয়ে, স্রোতধারাসমূহকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে নেওয়ার ভিতর দিয়েই মানবসমাজ ‘প্রাণদা-যমদূতিকা’র স্বভাবের হাত থেকে পরিত্রান পেতে চাইছে। তার মানে অদূর ভবিষ্যতে দৃশ্য-নদীগুলির বাঁধগুলিকেও অকেজো করে দিয়ে, প্রবাহিত নদীসমূহকেও পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে নেবার পরিকল্পনা করা হবে, করতেও হবে। একমাত্র তাহলেই নদনদীসমূহ যে মধুক্ষরণ করে, মানবসমাজ সে মধুর সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করতে পারবে।
অতএব অদৃশ্য ধারাসমূহের বাঁধ ভেঙে দিয়ে সেগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। দৃশ্য ধারাসমূহের বাঁধ ভেঙে দিয়ে, সেগুলিকেও পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে নিতে হবে। মানুষের অহিত-বিনাশের লক্ষ্যে শতাব্দী-শেষের এই ভাবনা। নদনদী-দর্শনের এই পুণ্যফল।
ব্যাখ্যা ও সূত্র নির্দেশ –
১। ভারতের লোকবিশ্বাস ও পুরাণাদি অনুসারে গঙ্গা নদী তিন লোকেই প্রবাহিত। স্বর্গলোকে তার নামে আকাশগঙ্গা, সুরধনি-গঙ্গা, মন্দাকিনী বা অলকানন্দা, মর্ত্ত্যলোকে তার নাম ভাগীরথী, জাহ্নবী ইত্যাদি এবং পাতাললোকে তারই নাম ভোগবতী। পতিতকে উদ্ধার করার অসীম ক্ষমতার জন্য একে পতিতপাবনী বলে। সে ক্ষমতা কত, রামায়ণে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।
২। পুরাণাদি অনুসারে, বশিষ্ঠ মুনি পাশবদ্ধ হয়েছিলেন অভিশাপে। এই নদী তাকে পাশমুক্ত করেছিল বলে এর নাম বিপাশা।
৩। পুরাণাদি অনুসারে ব্রহ্মার দু’চোখ থেকে দু’ফোঁটা জল পড়ে নর্ম্মদা ও শোন নদীর উদ্ভব হয়েছে। আর শিবের সুর শুনে ব্রহ্মার পা গলে যায়, বিষ্ণু তা ধরে রাখেন কমণ্ডলুতে, ভগীরথ তাকেই আনয়ন করেন …ইত্যাদি।
৪। শান্তনুকে বিয়ের শর্ত্ত ছিল যে, গঙ্গা তার সন্তানকে নিয়ে কী করছেন, সে প্রশ্ন করা যাবে না। তো, এক একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, আর গঙ্গা তাকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দেন। থাকতে না-পেরে অবশেষে অষ্টমবারে প্রশ্ন তোলেন শান্তনু, বেঁচে যায় দেবব্রত (ভীষ্ম), আর গঙ্গা শান্তনুকে ত্যাগ করে চলে যান। কারণ শান্তনু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন।
৫। পুরাণ অনুসারে লক্ষ্মী সিন্ধুর কন্যা।
৬। গঙ্গায় পাপস্খালন বলতে বোঝায়, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজে যে বানিজ্যিক পণ্যধারাস্রোত প্রবাহিত থাকে, তাতে নিজের উৎপাদিত পণ্য (বা পাপ) সকল ভাসিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ নিজের পণ্য বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচে দেওয়া। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা লেখকের ‘দিশা থেকে বিদিশায় ঃ নতুন সহস্রাব্দের প্রবেশবার্ত্তা’ গ্রন্থে পাওয়া যাবে। ওই গ্রন্থের ‘নরকদর্শন…’ নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।
৭। লেখকের ‘পরমাভাষার সঙ্কেত ঃ ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি ও ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। গ্রন্থটি ঢাকার প্যাপিরাস থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ‘আমার জগৎ’।
৯। কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যায় এখন এই বাক্যবন্ধটি হামেশাই ব্যবহৃত হয়।
১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ‘নারী’।
১১। লেখকের উপরোক্ত ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।
১২। প্রায় সকল পুরাণেই এই বাক্যটি দেখতে পাওয়া যায়। জলের যেমন সমোচ্চশীলতা, আদিম সমাজের মানুষেরাও তাই ছিল; কেউ বেশী উঁচু কেউ কম – এমন ছিল না। ওই বাক্যটি ওইরূপ জনসাধারণ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছিল। পৃথিবীর সূত্রপাতে যে-জলের সৃষ্টি হয়েছিল, সেকথা পুরাণকাররা জানতেন না।
১৩। ‘দেবদেবী ও তাঁদের বাহন’ / স্বামী নির্ম্মলানন্দ।
১৪। দ্রষ্টব্য ঃ ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ / হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিবন্ধের বেশীর ভাগ শব্দার্থের উৎস ওই গ্রন্থ, পরে আর তা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে না।
১৫। আগের বারে কাজটা করতে গিয়ে যে যে খামতি থেকে গিয়েছিল, পরের বার সেগুলিকে কাটিয়ে ওঠার যে স্বাভাবিক মানবিক প্রবণতা, তাকে ‘স্বাভাবিক বিশুদ্ধিবাদ’ নাম দেওয়া হয়েছে। লোকে স্বভাববশতই এই জ্ঞানের অধিকারী। বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকের ‘মৌলবিবাদের থেকে নিখিলের দর্শনে’ গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।
১৬। এটি মার্কস সাহেবের বক্তব্য। দ্রষ্টব্য ক্যাপিট্যাল। ১ম খণ্ড।
১৭। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত দ্রষ্টব্য।
১৮। সেকালে যৌথ সমাজের ‘থিঙ্ক ট্যাঙ্ক’গুলিকে ‘মানস সরোবর’ বলা হয়। সে ছিল একাকারের (বা একার্ণবের) যুগ। বর্তমানে পুনরায় মানবসমাজ একাকারের (গ্লোকালাইজেশনের) যুগে পা রাখতে চলেছে বলেই শব্দটি ফিরে এসেছে ‘থিঙ্ক ট্যাঙ্ক’ রূপে। কিছুদিন আগেও এই শব্দটি ইংরেজী ভাষায় ছিল না।
১৯। ‘শ্রম’ মানেই ‘তপস্যা’, একথা ‘বঙ্গীয় শব্দকোষে’ স্পষ্ট লেখা রয়েছে। অথচ আমাদের বোঝানো হয় যে, ‘তপস্যা’ মানে ‘এবাদত’-জাতীয় কোনও ব্যাপার। অথচ সেকালে যেখানে শ্রম করা হত, তাকে বলা হত ‘আশ্রম’, যেখানে তপস্যা করা হত তাকে বলা হত ‘তপোবন”।
২০। এই নিবন্ধটি ‘মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা’র ‘নদী’ সংখ্যার জন্য লিখিত। তাতে ভূপৃষ্ঠবাহিনী নদী বিষয়ে অন্যান্য লেখকেরা এত বেশী লিখেছেন, যে, পুনরায় সেসব উল্লেখ করা বাহুল্য হবে বিবেচনা করে পার্থিব নদ-নদী এই বিষয়ে কোনও আলোচনা করা হয়নি।
২১। ‘State of The World 1999’ by World Watch, Millenium edition থেকে।
২২। বাক্যটি শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়ের ‘জনগণের বৃহত্তর মঙ্গল’ নিবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রকাশক ‘নর্ম্মদা বাঁচাও’ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ‘ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব পিপলস মুভমেন্টস’ নামক সর্বভারতীয় সঙ্গঠনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার মুখপত্র ‘বিকল্প’ পত্রিকা। নিবন্ধটি লোমহর্ষক তথ্যে ভরপুর। উল্লিখিত বাক্যের প্রথম ‘চার কোটি মানুষ’ বাঙলাদেশের এবং বাঁধটির নাম ফরাক্কা, দ্বিতীয় ‘চার কোটি মানুষ’ গুজরাটের এবং বাঁধটির নাম নর্ম্মদা।
২৩। শ্রী বিমানবিহারী মাইতি, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অত্যন্ত গুণী ছাত্র, পাশ করার পর গিয়েছিলেন সেচ বিভাগের কাজ করতে। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিধিবহির্ভূত কাজ করে চলেছে ভারতের সেচ বিভাগ। ব্যাপারগুলির গভীরে অনুপ্রবেশ করে, সারাদেশকে প্রতিবছর খরা-বন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে রাখার বিশাল ষড়যন্ত্র তিনি দেখতে পান। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল, সে সবই জেনেশুনে ভেবেচিন্তে করা। তাঁকে চাকুরি থেকে তাড়িয়ে, নানান আইনের ফাঁসে ফেলেও দমানো যায় না। শেষমেষ ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে রূপায়িত প্রকল্পের উপর ডক্টরেট করতে চাইলে উপরোক্ত তথ্যটি জানতে পারেন এবং ‘থ’ বনে যান। খোঁজ নিয়ে তিনি দেখেন, সকল ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতেই ঐ ডাইরেক্টিভ বলবৎ আছে। ইতোপূর্বে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতিকে জানান যে, আপনার সেচ বিভাগের নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারেরা ‘ইডিয়ট’, কারণ তারা ইঞ্জিনিয়ারিং বিধি জানে না। সে চিঠির কপি সর্বত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি উত্তর দেন না। সেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারেরা মানহানির মামলা করেন। আদালত রায় দেয় যে, শ্রী বিমানবিহারী মাইতি যেভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে বিষয়টি অ্যাকাডেমিক। অতএব আদালত বলতে পারছেন না, ভারতের সেচ বিভাগের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারগণ ‘ইডিয়ট’ কি না। পশ্চিমবঙ্গের অ্যাসেমব্লিতে সেচ বিভাগের এই ‘কীর্তির’ বিষয়ে অতঃপর এম.এল.এ, ড. ওমর আলি প্রশ্ন তোলেন। সে প্রশ্ন আজও অনুত্তরিত আছে। …একা একা ওই অচলায়তনের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে শ্রী মাইতির জীবনটাই বলতে গেলে খরচ হয়ে গেল। তবে, এখনও তিনি প্রাণবন্ত। তাঁর বর্তমান ঠিকানা – ‘সাহেবের আবাদ’, ১ নয়াবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ।
২৪। এই বাক্যটি শিবপুরাণের বায়বীয় সংহিতার।
[প্রথম প্রকাশ: মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা, নদী সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৯]
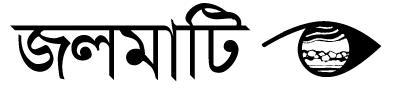












সাম্প্রতিক মন্তব্য