
ভাষার ধর্ম্ম-রাজনীতি-সাম্রাজ্যবাদ

যদি প্রশ্ন করা হয়– গায়ত্রী মন্ত্র কোন ভাষায় রচিত? বারো আনা মানুষই উত্তর দেবেন– সংস্কৃত। কিন্তু, এই উত্তরটি সঠিক নয়। আদতে, গায়ত্রী মন্ত্র ঋগ্বেদের একটি সূত্র (৩.৬২.১০) এবং বেদ সংস্কৃত নয়, ‘ছান্দস’ ভাষায় রচিত। ছান্দসের ব্যাকরণও সংস্কৃতের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology), শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics), এমনকি বাক্যগঠনেও (Syntax) দুটি ভাষায় বিস্তর পার্থক্য আছে। ছান্দস ভাষার ‘র’ ধ্বনি সংস্কৃতে ‘ল’-য়ে পরিণত হয় (শ্রীর > শ্লীল, রোম > লোম, ইত্যাদি)। অবশ্য পরবর্তী সময়ে দুই প্রকার ধ্বনিই সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে। ছান্দস ভাষায় পাশাপাশি দুটি স্বরবর্ণ আলাদা ভাবে উচ্চরিত হতেই পারে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সন্ধি অনিবার্য্য (ছান্দসে ‘সপ্ত ঋষয়ঃ’ পদদ্বয় সংস্কৃতে এলেই ‘সপ্তর্ষয়ঃ’ হয়ে যায়)। সংস্কৃতে উপসর্গ সবসময়ই ধাতুর আগে বসে, ছান্দসে তেমন বিধিনিষেধ নেই,– উপসর্গ ধাতুর পরে তো বসেই, অনেকসময় ধাতু আর উপসর্গের মাঝে একাধিক অন্য শব্দও থাকতে পারে। (‘জয়েম সংযুধি স্পৃধঃ’ বাক্যটি সংস্কৃতে ‘জয়েম-সং’ নয়, ‘সংজয়েম’ হত।) ছান্দস ভাষার ধাতুরূপে বৈচিত্র তুলনামূলক ভাবে বেশি। ইত্যাদি…
আবার যদি প্রশ্ন ওঠে, অন্তত ব্যাস-বাল্মিকীর মহাভারত-রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত কিনা,– তার উত্তরও এককথায় দেওয়া কঠিন। এখানে কালক্রম কিছুটা বিভ্রান্তিকর। লোকবিশ্বাসে মহাকাব্যদুটির রচনাকাল ৩০০০-২০০০ খ্রিষ্টপূর্ব্ব। ঐতিহাসিকদের মতে ১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব্ব। খ্রিষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত ‘অষ্টাধ্যায়ী’তে মহাকাব্যদুটির নাম পাওয়া যায়। সুতরাং, তার আগে তো বটেই। এদিকে রাময়ণে তথাগত ও বৌদ্ধদের গালমন্দ করার ও মহাভারতে বৌদ্ধদের বৈদিক ধর্ম্মে ফিরিয়ে আনার ঘটনার/ কাহিনীর উল্লেখ আছে। অতয়েব, সেগুলি নিশ্চিতভাবেই বুদ্ধের জন্মের পর রচিত।
এদিকে, প্রচলিত বিভিন্ন লোকভাষা থেকে উপাদান নিয়ে সে’গুলিকে ঘষে-মেজে ‘অষ্টাধ্যায়ী’তে পাণিনি যে ‘নতুন’ ভাষার কাঠামো গড়েছিলেন, খ্রিষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি বা বিক্রমাদিত্যের আমলে বররুচির মতো বৈয়াকরণেরা সেই ভাষার নামকরণ করেন ‘সংস্কৃত’। পাণিনির বহু আগে বেদ বা রামায়ণ-মহাভারত রচনা হয়ে গেলেও পতঞ্জলিদের ‘অষ্টাধ্যায়ী-ভাষ্য’ রচনার আগে ‘সংস্কৃত’ নামটি অবধি ছিল না। অথচ, রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সংস্কৃত নামক ভাষার উল্লেখ আছে!
এ হেন ধাঁধার সমাধান করে মোটামুটি যে সিদ্ভান্তে পৌছানো যেতে পারে, তা হল– ‘স্মৃতি’ পর্যায়ের অন্তর্গত মহাকাব্য দুটি অন্তত খ্রিস্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগে ‘অ-সংস্কৃত‘ ভাষায় ‘রচিত’ হলেও অন্তত খ্রিষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পর ‘সংস্কৃত’ ভাষায় লিখিত হয়। দেখা যাচ্ছে, বেদের ভাষাও সংস্কৃত নয়, রামায়ণ ও গীতা সহ মহাভারতের আদি সংস্করণগুলির ভাষাও সংস্কৃত কিনা বলা কঠিন। কিন্তু, সংস্কৃতের পরিচয় ‘হিন্দুর ভাষা’ হিসেবে!– এ এক অদ্ভুত কূটাভাস।
পাণিনি প্রাক-বৈদিক ভাষাগুলির নাম দিয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ভাষা। সেই ‘জাতিভাষা’গুলি ছিল মৌখিক। শৈলীগত দিক থেকে বেদের ভাষায় কাব্যভাব বেশি। আন্দাজ করা যায়, ‘ছন্দ’ থেকেই ‘ছান্দস’ ভাষার নামকরণ। আসলে অষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনি ‘সাধারণের কথ্য’ ও ‘বিশিষ্টজনের কথ্য’ হিসেবে ভাষাকে বিভাজিত করেছিলেন। প্রচলিত বিভিন্ন লৌকিক (প্রাকৃত) ভাষার ‘সংস্কার’ করে ‘সংস্কৃত’ ভাষাটির সৃষ্টি করা হয়েছিল (‘সংস্কারকৃত’ থেকে ‘সংস্কৃত’)। এই সংস্কারের কাজ আরো ব্যাপকভাবে শুরু হয় বৌদ্ধযুগের (মৌর্য্যযুগের) পতনের পর থেকে।– গুপ্তযুগে তো বটেই– যখন সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন পুরাণ ছাড়াও ‘অমরকোষ টীকা’ রচিত হয়। এমনকি পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ‘আমি পুষ্যমিত্রের যজ্ঞে পৌরহিত্য করেছি’– জাতীয় বাক্যের উপস্থিতি থেকে অনুমান করা যায় তিনিও রাজ-অনুগ্রহ পেয়েছিলেন এবং শুঙ্গ আমল থেকেই সেই দ্বিতীয় দফার সংস্কার শুরু হয়েছিল।
এই সংস্কারের কারণ অনেকটাই রাজনৈতিক। স্বাভাবিক কারণেই বৌদ্ধযুগে পালি ভাষার রমরমা বেশি ছিল। (আজকের আরবি ও ইসলামের মতো) এই পালি ভাষা বৌদ্ধধর্ম্মের (আদতে রাষ্ট্রধর্ম্মের) অন্যতম প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। মৌর্য্যযুগের পতনের পর হিন্দু রাজাদেরও প্রয়োজন ছিল তেমন একটি ভাষার। জনসাধারণের কথ্য ভাষার তুলনায় কৃত্রিম হলেও সংস্কারকৃত ভাষাটি ছিল অনেক বেশি আভিজাত্যপূর্ণ। তখন সমাজের উচ্চতর ত্রিবর্ণ মোট জনসংখ্যার চারআনা আর বাকি বারোআনা শূদ্র। এই উচ্চ বর্ণের ছটা ও নিম্নবর্ণের কালিমা আরোপিত হয়েছিল তাদের যার-যার মুখের ও চর্চার ভাষাগুলির গায়েও। তবে উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক, এই সময়ে সংস্কৃত ভাষাটি দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতা উচ্চতা– সবদিক থেকেই যে চূড়ান্ত উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু, ভাগ্যের এমন পরিহাস, প্রাচীনতর লৌকিক ভাষার যে শব্দগুলি সংস্কৃতে প্রবেশ করেছিল, আজ সেই শব্দগুলিকে ‘সংস্কৃত থেকে এসেছে’ বা ‘সংস্কৃত-তৎসম’ বলা হয়! আর যে শব্দগুলি অন্যান্য ভাষা থেকে কিছুটা পরিবর্ত্তিত হয়ে সংস্কৃতে প্রবেশ করেছিল, সেগুলিকে সংস্কৃত থেকে বাংলা, মারাঠি, গুজরাতি, ইত্যাদি ভাষার তদ্ভব শব্দ হিসেবে পরিচিত হয়েছে!
যদিও ভাষার দুনিয়ায় শব্দের আদান-প্রদান বিষয়টা একরৈখিক নয়। এমন হতেই পারে– কিছু পাঞ্জাবি শব্দ সংস্কৃত ঘুরে গুজরাতি ভাষায় প্রবেশ করেছে বা কিছু বুন্দেলি/ ভোজপুরি শব্দ সংস্কৃত ঘুরে অবহঠট প্রাকৃতে (যার থেকে আধুনিক বাংলা ভাষার সৃষ্টি) প্রবেশ করেছে। সংস্কৃত ভাষার এই ‘আভিজাত্য’ বা সামগ্রিক ভাবে ভাষার ভদ্রলোক-ছোটলোক ভেদাভেদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রায় দেড় হাজার বছর পরও বাংলা গদ্যসাহিত্যের শুরুতে বঙ্কিমচন্দ্র হাটে-বাজারের-অন্দরমহলের মুখের ভাষার বদলে অত্যন্তরকম সংস্কৃতঘেঁষা একটি অপ্রচলিত ভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের বা রবীন্দ্রনাথের গদ্যে চরিত্রগুলির মুখের ভাষা ‘চলিত’ হলেও লেখকের ভাষা সেই সংস্কৃতঘেঁষা।
না, এখানে শরৎ-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করা হচ্ছে না। কিন্তু, এমন উদাহরণ আরো আছে।– শরীরি বর্ণনায় কালিদাসের মাত্রা না ছাড়িয়েও ভরতচন্দ্র অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। হয়তো সংস্কৃতের এই আভিজাত্যের কারণেই রামমোহনের ‘গৌড়িয় ব্যাকরণ’-এর বদলে বিদ্যাসাগরের ‘ব্যাকরণকৌমুদী’ বেশি মান্যতা পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মধ্যযুগে যে ‘কাতন্ত্র’, ‘মুগ্ধবোধ’, প্রভৃতি গুটিকয়েক (সংস্কৃত) ব্যাকরণ বঙ্গদেশে রচিত হয়েছিল, তাদের নামের মধ্যেও ছিল হীনমন্যতার গন্ধ।– ‘কাতন্ত্র’ শব্দের অর্থ ‘ক্ষুদ্র তন্ত্র’, ‘মুগ্ধবোধ’ শব্দের অর্থ ‘মুগ্ধ বা মূঢ় বা অল্পজ্ঞদের বোধের নিমিত্তে রচিত ব্যাকরণ’।
বাংলা ব্যাকরণের ওপর সংস্কৃত ব্যাকরণের এই খবরদারি ও নজরদারির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা খুব প্রাসঙ্গিক।– তিঁনি সমস্যায় পড়েছিলেন ‘Originality’-র বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে। ‘স্বকীয়তা’ বা ‘মৌলিক’ জাতীয় শব্দগুলি সুবিধাজনক হচ্ছিল না। ‘মৌলিকে’ বড্ড radical-গন্ধ, ‘স্বকীয়তা’ সব জায়গায় খাটে না। ভেবেচিন্তে একটি নতুন শব্দ তৈরী করলেন– ‘মৌলীন্য’। কিন্তু… ‘কুলীন শব্দে যেমন কুলগৌরব প্রকাশ করে তেমনি মূলীন শব্দে মূলগৌরব প্রকাশ করিবে এই মনে করিয়াই ঐ কথাটাকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। কিন্তু শাস্ত্রী-মহাশয় বলিয়াছেন কুলীন শব্দ ব্যাকরণের যে বিশেষ নিয়মে উৎপন্ন মূলীন শব্দে সে নিয়ম খাটে না। শুনিয়া ভয় পাইয়াছি। ভুল পুরাতন হইয়া গেলে বৈধ হইয়া উঠে, নূতন ভুলের কৌলীন্য নাই বলিয়াই ভাষায় তাহা পঙ্ক্তি পায় না। বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের ব্যভিচার অনেক চলিয়াছে; কিন্তু আজকালকার দিনে পূর্ব্বের চেয়ে পাহারা কড়াক্কড় হওয়ায় সে সম্ভাবনা আর নাই। অতএব জাতমাত্রই মৌলীন্য শব্দের অন্ত্যেষ্টি সৎকার করা গেল।’
স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও ‘প্যারিচাঁদ’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ‘আমি বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ ‘খয়ের’ বলিতেন না, ‘খদির’ বলিতেন, কদাচ ‘চিনি’ বলিতেন না, ‘শর্করা’ বলিতেন। ‘ঘি’ বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, ‘আর্জাই’ বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন।… পণ্ডিতদের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাংলাভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য।’ এই পণ্ডিতদের সেই ভাষা যে মোটেই সাধারণ মানুষের মাথায় ঢুকত না তার নিদর্শন হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটিতেই একটি মজার ঘটনার উল্লেখ আছে।– জনৈক অধ্যাপক তার একটি ভাষণে ‘শুশুক’-এর বদলে ‘শিশুমার’ শব্দটি ব্যবহার করেন। এদিকে ‘শিশুমার’ শব্দটি অপরিচিত হওয়ায় উপস্থিত জনগণ নাকি তাকে ‘শিশুকে মেরে জলে ফেলে দেওয়ার’ প্ররোচনা বুঝে প্রচণ্ড গোলমাল বাঁধিয়ে তুলেছিল!
বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত (তৎসম) শব্দের প্রাধান্য যেমন রাতারাতি দূর হয়নি, তেমন রাতারাতি শুরুও হয়নি। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত চর্যাপদগুলির শব্দতালিকায় মোট হাজারদুয়েক শব্দের মধ্যে সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ মোটামুটি পাঁচ শতাংশ। চতুর্দশ শতাব্দীর ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন’ কাব্যে তৎসম শব্দের পরিমাণও মোটামুটি বারো-তেরো শতাংশ। অথচ, আঠারো-ঊনিশ শতকে এসে দেখা গেল বাংলাসাহিত্যের ভাষার প্রায় আশি শতাংশ শব্দই তৎসম!
আসলে, আঠারো শতকে হেলহেড, হেনরি ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরি বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের ‘সন্তান’ ধরে নিয়ে সাধারণের কথ্য বাংলায় উপস্থিত আরবি বা ফারসি উৎসের শব্দগুলিকে ‘অশুদ্ধ’ ঘোষণা করেছিলেন। মূলত, এই দুই ইংরেজ ও এক আইরিসের হাতে বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়নের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে সম্পন্ন হয়। এরপর ১৮৩৮ সালে আইনের সাহায্যে কোম্পানির আদালতগুলিতে ইংরেজির পাশাপাশি ফারসির বদলে বাংলা ভাষার এই নতুন রূপটির প্রবর্ত্তন করা হয়। সজনীকান্ত দাসের ভাষায়, ‘সাহেবরা সুযোগ পাইলেই আরবী-ফারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন; ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যে বাংলা-গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল।’ (সূত্র: ‘বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস’ – সজনীকান্ত দাস)
যেখানে উত্তর ভারতের ভাষাগুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ইংরেজি ও ফারসিকে সরকারি ভাষা ঘোষণা করা হয়েছিল, সেখানে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে নাকউঁচু ইংরেজরা হঠাৎ বাংলা ভাষার ঐতিহ্য বিষয়ে খুব আগ্রহী বা যত্নশীল হয়ে পড়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় টানাপোড়েন সৃষ্টি করে সেই ডিভাইড অ্যান্ড রুল।– হিন্দুদের দলে টানলে তারা মুসলমান শাসকের হাত থেকে মুক্তিদাতা হিসেবে তোমার পুজো করবে। (ঠিক যেমন, পাকিস্তানি পাঞ্জাবের বহু লোক আজও বিশ্বাস করে ইংরেজরা তাদের শিখ শাসকদের হাত থেকে ‘স্বাধীনতা’ দিয়েছিল! তবে যদি বলা হয়, ইংরেজদের কাণেই এদেশে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয়েছে,– সেটি অতিসরলীকরণ হবে। এদেশের হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে একটি বিভাজন রেখা পলাশীর যুদ্ধের আগেও ছিল। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে তাকে ক্রমাগত চওড়া করে গিয়েছে।)
ঘটনাচক্রে, বহু সম্ভ্রান্ত বংশের বাঙালি হিন্দুও রাতারাতি ফারসির বদলে বাংলার প্রবর্ত্তনের পক্ষে ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের (১৮২০-৮৫) আত্মজীবনীতে দেখা যায়, ‘…গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ হইল যে এদেশের রাজকার্য্য দেশীয় ভাষায় চলিবেক। বাঙ্গালীর পক্ষে পারস্য একরূপ অকর্ম্মণ্য হইল, এবং ইহার আদর এককালে উঠিয়ে গেল। বহু যত্নের ও শ্রমের ধন অপহৃত হইলে অথবা উপার্জ্জনাক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয় সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমার মনে উপস্থিত হইল।’…
তবে শুধু ফারসি ভাষাকে ব্রাত্য করাই নয়, সরকারি বাংলা ভাষা থেকে ফারসি শব্দগুলিকেও বাতিল করার পিছনে বাঙালি হিন্দুদের একাংশের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ঘটনাচক্রে, আইন ঘোষণার বছরেই (১৮৩৮) শ্রীরামপুর থেকে শ্রী জয়গোপাল তর্ক্কালঙ্কারের ‘পারসীক অভিধান’ প্রকাশিত হয়। তার ভূমিকায় লেখা ছিল, ‘ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন যে স্বকীয় ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা লুক্কায়িত হইয়া চিরকাল বিহার করিতেছে এবং তাঁহারা আর বিদেশীয় ভাষার অপেক্ষা না করিয়াই কেবল স্বদেশীয় ভাষা দ্বারা লিখন পঠন ও কথোপকথনাদি ব্যবহার করিয়া আপ্যায়িত হইবেন এবং স্বকীয় বস্তু সত্ত্বে পরকীয় বস্তু ব্যবহার করাতে যে লজ্জা ও গ্লানি তাহাহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এবং প্রধান ও অপ্রধান বিচারস্থলে বিদেশীয় ভাষা ও অক্ষর ব্যবহার না করিয়অ স্বস্ব দেশ ভাষা ও অক্ষরেতেই বিচারীয় লিপ্যাদি করিতে সম্প্রতি যে রাজাজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতেও সম্পূর্ণ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।’ (বানান ও ছেদ-যতিচিহ্ন অপরিবর্ত্তিত)
এর পাশাপাশি সেই সময় ‘সমাচার দর্পন’, ইত্যাদি বাংলা সংবাদপত্রগুলি বাংলা ভাষা প্রচলনের সরকারী সিদ্ধান্তের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগে সফল হয়েছিল।আসলে ইংরেজরা জানত, বাংলা ভাষা বাঙালির মননে যেটুকুই হোক, যে ভাবেই হোক থাকবেই। বরং, বাঙালির সাপেক্ষে যে ভাষাটি বিদেশি, সেই ফারসির বদলে আরেকটি বিদেশি ভাষা ইংরেজিকে একবার ঢুকিয়ে দিতে পারলে ভাষার পথ ধরে ইংরেজি সংস্কৃতি ও ইংরেজি শাসক– দুইয়ের প্রতিই আনুগত্য আদায় করা সম্ভব হবে।
সংস্কৃত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ চর্চা অসম্ভব। অষ্টাধ্যায়ীকে অস্বীকার করে বাংলা ব্যাকরণ রচনাও প্রায় অবিশ্বাস্য। কিন্তু, এই যে সংস্কৃতের ‘আভিজাত্যের কারণে আধিপত্য’,– এককথায়, তা হল ভাষার সাম্রাজ্যবাদ। আর সেই আধিপত্য মেনে নেওয়ার পেছনে কাজ করছে এক ধরণের হীনমন্যতা। আজ একুশ শতকে এসে সংস্কৃতের সেই বাজারদর আর নেই, ফলে যে শ্রেণী একসময় তাদের কথ্য বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ গুঁজতো, আজ ইংরেজি, হিন্দি অথবা আরবি-ফারসি শব্দ ঠুঁসে চলেছে। হ্যাঁ, ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের বশেই আজ বহু গড়পড়তা বাঙালি বাংলার বদলে ইংরেজি, হিন্দি বা আরবি শিখে যেন বেশি আহ্লাদিত হয়।
‘আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ইচ্ছা হয় বাঙ্গালা ভাষায় কোন কোন বিষয় লিখিয়া সমাচার পত্রে প্রচার করিবেন। কিন্তু তাহা লিখিতে বসিলেই দুই চক্ষু ললাট পানে উঠিয়া যায়। অতি ক্লেশে যাহা লিখিয়া পাঠান তাহা পাঠ করিতে পাঠকদিগের শিরোঘর্ম পাদস্পর্শ করেন। এই ক্ষণে আমরা আধুনিক ছাত্রদিগের যে সকল পত্র পাইতেছি তাহা পাঠ করিতে অত্যন্ত ক্লেশ জ্ঞান হয়, অক্ষরগুলি যাহা লেখেন তাহা যেন কাক বকের নখ চিহ্ন সাজাইয়া যান, সে সকল অক্ষর পাঠ করা যায় না এবং অনেক চিন্তায় মর্ম গ্রহণ করিতেও সম্পাদকেরা গলদঘর্ম হন।’… বলাই বাহুল্য, এই প্রতিবেদনটি আজকের নয়, ১৮৫৬ সালের ১৫ই জানুয়ারির ‘সম্বাদ ভাস্কর’-এর (বানান অপরিবর্ত্তিত) সম্পাদকীয় নিবন্ধের অংশবিশেষ।
সুতরাং, আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না, ‘রোগ’টি বেশ পুরোনো। ‘অমুক ভাষা জানলে তাড়াতাড়ি চাকরি হয়’– গোছের ধারণাগুলি কিছুটা দূরে রাখলেই নজরে পড়ে,– যে দুটি ভাষা আজ গড় বাঙালির কৌলীন্যের পরিচায়ক হয়েছে, তার মধ্যে ইংরেজির নিজস্ব লিপি অবধি নেই (বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির মতো ইংরেজরাও তাদের প্রাক্তন শাসক রোমানদের লিপিই ব্যবহার করে,– ঠিক যেমন মেঘালয়ের খাসিয়া ভাষা ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজি ভাষার লিপিকে আপন করেছিল) আর হিন্দি একটি ‘কৃত্রিম ভাষা’। আফশোস এই যে, আজ আশেপাশে একজন অমিত রায়ও নেই যে বলবে,– ‘কল্পনা করুন-না, যেন এখনই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি, নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হল, আকাশের ঐ রঙিন মেঘের কাছ পর্যন্ত পৌঁছল, সামনের ঐ পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। মনে ভাবতেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস ডাট?…’
ভাষা বিষয়টি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তবে ‘সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানে’র ধারণাটি আদতে দার্শনিকের স্বপ্নদোষ। বাস্তবে (১) প্রাণের ভয়, (২) পেটের দায়, (৩) বিবাহ বা যৌন সম্পর্ক ও (৪) গভীর হীনমন্যতা ছাড়া কেউই অন্যের সংস্কৃতির গুণমুগ্ধ হলেও নিজেরটি ছেড়ে তাকে আপন করে নেয় না। তবে সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিক জাতি হামেশাই কৌশলগত দিক থেকে নিজের সংস্কৃতি ও ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আক্রান্ত জাতি/ গোষ্ঠির নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা তখন হয়ে ওঠে তাদের জাতীয়তাবাদের প্রতীক। তবে এই লড়াইয়ের দৈর্ঘ্য ও ফলাফল অনেকটাই নির্ভর করে দুদিকের ভাষা/ সংস্কৃতির তুলনামূলক সমৃদ্ধির ওপর। একসময়ে সংস্কৃত তার সুবিশাল সাহিত্যভাণ্ডারের উপস্থিতির কারণে এইখানে টেক্কা দিয়েছিল। তবে ভাষাকে কখনও-সখনও ধর্ম্ম, ইত্যদির সঙ্গে সংযুক্ত করে এই সমৃদ্ধিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলার চেষ্টাও চলে।
ওপরের বক্তব্যগুলি অনেকাংশেই অনুমান।‒ নৈয়ায়িক পরিভাষায় যাকে বলে ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ (Retrospection, অভিজ্ঞতাজাত সংস্কারের প্রভাবে গৃহিত সিদ্ধান্ত)। আদৌ কি এমন ঘটে?– যথেষ্ট পরিমাণ ‘পাথুরে প্রমাণ’ আছে এমন একটি ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরা যাক;–
ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের পর গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়েই আরবি ভাষার আধিপত্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই হিসেব অনেকটাই উলটে যায় পারস্যে এসে। আরবের হাতে সেলিক সাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও, অধিকাংশ পারসিকেরা ইসলাম গ্রহণ করলেও নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি ত্যাগ করেনি। বলাই বাহুল্য, বেদুইন জাতির ভাষা বা সংস্কৃতির তাদের পারসিক প্রতিরূপের মতো সুবিশাল ঐতিহ্য ছিল না। যুদ্ধজয়ী আরব পারসিক (ফারসি) ভাষার রূপ ও চরিত্র পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করলে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখিন হয়। ‘শাহনামা’র রচয়িতা মহান ফিরদৌসি, প্রমুখ কবিদের নেতৃত্বে পরসিকেরা রুখে দাঁড়িয়েছিল। এর ফল হয়েছিল চমকপ্রদ। ইসলাম ধর্ম্ম মধ্যপ্রাচ্য থেকে আরো পূর্ব্বদিকে (ভারতীয় উপমহাদেশে) যাত্রা শুরু করলে আরবির পাশাপাশি ফারসি ভাষাও তার অন্যতম মূখ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। ভুললে চলবে না, দিল্লি সালতানাতের প্রায় শুরুর দিন থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অবধি ফারসিই ছিল রাজভাষা।
কিছু আগে হিন্দি ভাষাকে যে ‘কৃত্রিম ভাষা’ বলা হয়েছে, তা অনেকেরই অদ্ভুত লাগতে পারে। একসময়ে ফারসির রাজভাষা হয়ে ওঠা হিন্দির এই পরিণতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। প্রথমত, ‘হিন্দি’ শব্দটি কোনো ভাষার নাম বা বিশেষ্য পদ ছিল না। এটি ছিল বিশেষণ। অওয়াধি, ভোজপুরি, খড়িবোলি, বুন্দেলি, বাঘেলি, ছত্তিশগড়ি, কণৌজি, মৈথিলি, ইত্যাদি প্রায় কুড়িটি ভাষা উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল এবং আজও আছে। সেই ভাষাগুলিকে একত্রে হিন্দুস্তানি বা হিন্দি ভাষা বলা হত। (ঠিক যেমন আজও উত্তর ভারতীয়দের ‘হিন্দুস্তানি’ নামে চিহ্নিত করার চল আছে।) হ্যাঁ, এগুলি পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাষা, হিন্দির ডায়ালেক্ট নয়। বরং হিন্দির লিঙ্গিউস্টিক ইম্পেরিলিজমের চাপে ভাষাগুলির আজকে মর-মর দশা! এককালে যেগুলি রামচরিতমানস, মীরার ভজন, কবিরের দোঁহা থেকে শুরু করে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভাষা ছিল, সেগুলি ‘পরিণত হয়েছে’ তথাকথিত ছোটলোকের ভাষায়। (বর্ত্তমান ভোজপুরি ভাষার দিকে তাকালেই একটা আন্দাজ পাওয়া যায়)। আজ হিন্দির যে প্রচলিত রূপ সেটা আসলে উর্দুর আদলে তৈরী। উর্দু থেকে খুঁটে খুঁটে আরবি ফারসি তুর্কি শব্দগুলিকে বাদ দিয়ে, তাদের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত তৎসম শব্দ ঢুকিয়ে ‘বানানো’ এবং আর মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত। ‘শুদ্ধ হিন্দি’ আদতে একটি কৃত্রিম ভাষা।
এই ঘটনাপ্রবাহের কারণ বুঝতে আরো একটু পিছনে হাঁটতে হবে। দুই বা তার বেশি ভাষায় মিলিয়ে-মিশিয়ে কথোপকথনকে ভাষাবিজ্ঞানে ‘কোড মিক্সিং’ বলা হয়। কলকাতাইয়া ‘বাংরেজি’ বা ‘হিংলা’ নয়, এদেশের (সম্ভবত) প্রথম কোড মিক্সিংয়ের নমুনা হল উর্দু ভাষা। মুঘল যুগের তখন রাজভাষা আরবি মিশ্রিত ফারসি, আর উত্তর-ভারতীয় সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে বাদশাহি সৈন্যরাও হিন্দুস্তানি ভাষাগুলিতে কথা বলে। প্রয়োজন পড়েছিল এমন ভাষার, যা দুপক্ষেরই বোধগম্য হয়।– এই হল উর্দু ভাষার উৎপত্তির কাহিনী। ঘটনাচক্রে, ‘উর্দু’ শব্দটির অর্থ ‘সেনানিবেশ’ (প্রসঙ্গত, ‘উর্দি’ শব্দের কথাও ভাবা যেতে পারে)।
প্রথমদিকে উর্দু ভাষাটি ভারতীয় হিন্দু-মুসলিমের সঙ্গে বহিরাগত ও অভিজাত মুসলিমদের কথোপকথনের মাধ্যম ছিল। তবে অসাধারণ শব্দ মাধুর্যের কারণে ও রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় উর্দু ভাষাটি কাব্য, সাহিত্য, লঘু সঙ্গীতের জগতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে ভাষাটি অভিজাত ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গে পরিণত হয়।– ঠিক যেমন শুঙ্গ-কাহ্ন-গুপ্তযুগে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষায় যাবতীয় পুরাণ, মহাকাব্য, সংহিতা, ব্যাকরণ মহাভাষ্য, ইত্যাদি ‘লেখা’ শুরু হয়েছিল।
ইসলাম যুগের ভারতবর্ষে অভিজাত মুসলিমের পাশাপাশি হিন্দু রাজবংশ বা অভিজাত শ্রেণীও বর্ত্তমান ছিল। এই দুই ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠির মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত-বন্ধুত্বের বাইরে আভিজাত্যের লড়াইও (সহিংস নয়) ছিল ষোলআনা। আজকের দিনে ভারতীয় উপমহাদেশের সিংহভাগ হিন্দু ধর্মীয় কারণে যতটুকু সংস্কৃত জানে, মুসলিমদের আরবি জ্ঞানও তার সমতুল্য।– সাত-আটশো বছর আগের ছবিও খুব একটা আলাদা ছিল না। কোরান ও হাদিস বাদ দিলে আরবি সাহিত্যের তখন শৈশব চলছে। এদিকে আলেকজ়ান্ডারের (আক্ষরিক অর্থেই) মাতলামির কারণে ব্যবিলনের বিশাল গ্রন্থাগার পুড়ে যাওয়া ও অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের সময় আশুরবানিপালের গ্রন্থাগার ধ্বংস হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্যকীর্ত্তির বেশিরভাগটাই ততদিনে বিনষ্ট। যেটুকু ছিল, তাও মূলত ফারসি ভাষায়,– রাজভাষা হলেও যা কিনা গড়পরতা মানুষ তেমন ভাল বোঝে না (অনেকটা আধুনিক ভারতের ইংরেজির মতো)। সেই তুলনায় হিন্দুদের ‘পক্ষে’ সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের পাশাপাশি লৌকিক ও আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যকীর্ত্তিও ছিল সুবিশাল। ফলে ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্রের ‘লড়াই’য়ে ভারতের অভিজাত মুসলিমবর্গ উর্দু বেছে নিয়েছিল।
আরো এগোনোর আগে আশুরবানিপালের গ্রন্থাগারটির সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলার লোভ সামলানো কঠিন।– এই গ্রন্থাগারের বইগুলি আদতে মাটির ট্যাবলেটে ‘কিউনিফর্ম’ নামক সুমেরীয় তথা আক্কাদীয় লিপিতে লিখিত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ‘গিলগামেসের কাব্য’ তারই একটি। ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রগুলি আগে ‘রচিত’ হলেও ‘গিলগামেসের কাব্য’ মানবসভ্যতার প্রথম লিখিত বই। তার সবচেয়ে পুরোনো সংস্করণের পাতাগুলি অবশ্য পাথরের ওপর খোদিত, আর পুরো ‘বই’টির ওজন প্রায় টনখানেক!
আশুরবানিপালের রাজপ্রাসাদের দুটি তল জুড়ে বিস্তৃত ছিল এই গ্রন্থাগার। সেখানে বিষয়ভিত্তিক বইয়ের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ ছিল। ছিল প্রতিটি কক্ষের আলাদা আলাদা পুস্তকতালিকা। যে পদ্ধতিতে আধুনিক লাইব্রেরির ক্যাটালগ প্রস্তুত করা হয়, তার অনেকটাই এই সুপণ্ডিত ও লেখক সম্রাট আশুরবানিপালের চিন্তাপ্রসূত। তবে বই চুরি বিষয়টি যে সেই সময়েও একটা সমস্যা ছিল তার আন্দাজ পাওয়া যায় গ্রন্থাগারের প্রতিটি বইয়ে চোরেদের প্রতি দেবতার অভিশাপের ভাষ্যের উপস্থিতি দেখে।
ভারতবর্ষে ফেরা যাক। সংস্কৃতের তুলনায় উর্দু ভাষার বেশি জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল তার ভাষাগত ও বিষয়গত সহজবোধ্যতা। তার লিপিও ছিল ফারসি, ফলে রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের মতো সেও রাজভাষার ‘অনুজ’ হিসেবে পূজিত হতে শুরু করে। তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও হিন্দু জনগোষ্ঠী ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল (মানসিংহ, বীরবল, টোডরমলেরাও ছিলেন। কিন্তু, সেটা সার্বিক চিত্র নয়)। বরং, হিন্দুদের মধ্যেও উর্দুর জনপ্রিয়তা, বলা ভাল গ্রহণযোগ্যতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।
ইংরেজ রাজত্বে স্বাভাবিক ভাবেই ফারসির বদলে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তার পাশাপাশি ১৮৩৭ সাল নাগাদ ফারসি লিপিতে লিখিত উর্দুকে ‘অতিরিক্ত সরকারি ভাষা’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইংরেজরা শুরু থেকেই যে ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ পদ্ধতিতে সিদ্ধহস্ত ছিল তার প্রমাণ তাদের ভাষা ও শিক্ষানীতি।‒ হান্টার কমিশনের সুপারিশে তারা হিন্দুস্তানি ও উর্দু, দুটি মাধ্যমেই শিক্ষাব্যবস্থা চালু করলেও সরকারি কাজে হিন্দুস্তানি ভাষা বা দেবনাগরী লিপির প্রবেশাধিকার ছিল না। ফলে চাকরির সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে হিন্দি ও উর্দু শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়। অসন্তোষ দানা বাঁধতেও সময় লাগেনি। শুরু হয় হিন্দি-উর্দু বিতর্ক এবং ভাষা বিতর্ক অচিরেই ধর্মীয় বিতর্কের রূপ নিয়ে ফেলে। মুসলিমদের বক্তব্য ছিল, হিন্দুরা উর্দু ত্যাগ করছে, হিন্দুদের বক্তব্য ছিল, উর্দু কৃত্রিম ভাষা। সংযুক্ত প্রদেশ ও অওধ রাজ্য থেকে এই ‘আন্দোলন’ শুরু হয়েছিল। কিন্তু, একটা সমস্যা ছিল উর্দুর প্রতিপক্ষ ভাষাটির সর্ব্বজনগ্রাহ্য রূপ নিয়ে।‒ কারণ, গাড়োয়াল থেকে ঝাড়খন্ড অবধি হিন্দুস্তানি ভাষাগুলির প্রায় কুড়িটি রূপ, লিপিও একাধিক। তখন হিন্দুস্তানি ভাষাগুলির মধ্যে খড়িবোলি ভাষাটির ‘সংস্কারকৃত’ রূপ (কিছুটা যেন উর্দুর ফারসি লিপি গ্রহণ করার ধাঁচেই) সংস্কৃতের দেবনাগরী লিপিকে গ্রহণ করে ‘হিন্দি’ ভাষাটিকে উপস্থাপন করা হয়। (তবে খড়িবোলির সংস্কার শুরু হয় আরো আগে।)
উত্তর ভারতের এই দেবনাগরী লিপির সরকারি স্বীকৃতির অন্দোলনের নেতা ছিলেন মদন মোহন মালব্য, বাবু শিবপ্রসাদ, প্রমুখ। সংযুক্ত প্রদেশের বেশ কিছু হিন্দু ১৮৬৭ সাল নাগাদ অতিরিক্ত সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দুর বদলে হিন্দিকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী জানায়। ঠিক তার পরের বছরেই বাবু শিবপ্রসাদ ‘মেমোরেন্ডাম অন কোর্ট ক্যারেক্টারস্’-এ প্রাক্তন মুসলিম শাসকদের দ্বারা হিন্দু প্রজাদের উর্দু শিখতে বাধ্য করার কথা লেখেন। ১৮৮১ সালে বিহারে উর্দুর বদলে হিন্দি ভাষাকে অতিরিক্ত সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়ার কথা ঘোষিত হলে হিন্দি আন্দোলন আরো জোরদার হয়। ১৮৯৩ সালে বেনারস শহরে গঠিত হয় ‘নাগরী প্রচারণা সভা’।
এই সব কর্ম্মকাণ্ডের পালটা হিসেবে সৈয়দ আহমেদ খানের নেতৃত্বে উর্দু ভাষার সরকারি মর্যাদা রক্ষার জন্য অন্দোলন শুরু হয়ে যায়। গঠিত হয় ‘আঞ্জুমান তরিকা–এ-উর্দু’র মত সংগঠন। তবে ১৯০০ সালে ইংরেজ সরকার উর্দু ও হিন্দির জন্য সমান মর্যাদা কথা ঘোষণা করে। এতে হিন্দি পক্ষ আরো উৎসাহী হয়ে উঠলেও উর্দু পক্ষের নেতৃবৃন্দ কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়। যে সৈয়দ আহমেদ খান এক সময় বলেছিলেন, ‘হিন্দু ও মুসলিম উভয়কেই একই দৃষ্টিতে দেখি ও তাদের দুটি চোখ মনে করি… আমাদের স্বার্থ ও সমস্যা একই এবং তাই আমি দুই সম্প্রদায়কে এক জাতি হিসেবে বিবেচনা করি’, তিনিই বলে বসেন ‘এখন আমি নিশ্চিত যে হিন্দু ও মুসলিমের ধর্ম্ম ও জীবনের পথ একে অন্যের চেয়ে এতটাই অলাদা যে, তারা কখনওই এক জাতি হতে পারবে না।’
এদিকে ১৯১০ সালে এলাহাবাদে আয়োজিত হয় হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন। তার দশ-পনেরো বছরের মধ্যেই ‘দক্ষিণ ভারত হিন্দি প্রচার সভা’, ‘রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি’, ইত্যাদি সংগঠন তৈরী হয়ে যায়। ১৯১৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে ‘দক্ষিণ ভারত হিন্দি প্রভাষক’ নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তারই মাঝে উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্তানি ভাষাগুলি খাতায়-কলমে হিন্দির উপভাষা ও ডায়ালেক্টে পরিণত হতে শুরু করে। মৈথিলি সাহিত্য, বুন্দেলি সাহিত্য, ভোজপুরি কাব্য থেকে শুরু করে আওধি রামচরিতমানসেরও নতুন পরিচিতি পায় ‘হিন্দি সাহিত্য’ হিসেবে।‒ ভাষা অন্দোলন, নাকি ব্র্যান্ডনেম অ্যাকুইজিশান বোঝা দায়! আজ একুশ শতকে এসে দক্ষিণ বা পূর্ব্ব ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলির ওপর হিন্দির আগ্রাসনের প্রসঙ্গে বলা যায়,‒ হিন্দি ভাষা উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্তানি ভাষাগুলির এককালে যে দশা করেছে, তার তুলনায় এটি নগণ্য।
যাই হোক, হিন্দি ও উর্দু যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে পড়া সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের উত্থানের অন্তরায় ছিল। সুযোগসন্ধানী ইংরেজও সেই ছিদ্রপথে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢালতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে তা ছিল একটি বড় সমস্যা। মধ্যস্থতার চেষ্টায় মহাত্মা গান্ধী হিন্দি ও উর্দুকে মিশিয়ে ‘হিন্দুস্তানি’ ভাষার প্রস্তাব দেন, যখানে নাগরী ও ফারসি দুটি লিপির ব্যবহারের স্বাধীনতা থাকবে। প্রস্তাবটি তেমন একটি কার্য্যকর তো হয়ই না, বরং সেটি গান্ধীজীর জীবনে কাল হয়ে নেমে আসে।– নাথুরাম গডসে তার জবানবন্দীতে গান্ধীহত্যার অন্যতম কারণ হিসেবে হিন্দুস্তানি ভাষার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছিল। গডসের মতে, ‘বাদশা রাম বেগম সীতা’র মতো ভাষায় কথা বলার বদলে একজন হিন্দু মৃত্যুকে বেছে নেবে। (সূত্র: ‘শুনুন ধর্মাবতার’ – নাথুরাম গডসে ও গোপাল গডসে)
এদিকে বাল গঙ্গাধর তিলকের মতো বেশ কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতা দেবনাগরী লিপিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবশ্যক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন (১৯৩৭-৩৯) চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ম্যাট্রিকুলেশান পর্যায়ের শিক্ষায় হিন্দুস্তানি ভাষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় গণবিক্ষোভ। দুবছরে প্রায় দু’হাজার নারী-পুরুষকে কারাগারে পাঠিয়েও শেষরক্ষা হয়নি। সরকার সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।
১৯৫০ সালে উর্দুকে ব্রাত্য রেখে হিন্দি ‘রাজভাষা’ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছিল, পনেরো বছর হিন্দি ভাষাটি ইংরেজির সহকারী ভাষা হিসেবে থাকলেও তারপর হিন্দিই হবে ভারতের একমাত্র সরকারি ভাষা। সংবিধানের এই বিতর্কিত প্রস্তাবটির প্রভাবে দক্ষিণ ভারতে হিন্দিবিরোধী মানসিকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির শেষ ও তামিলনাড়ুর প্রথম মূখ্যমন্ত্রী কোঞ্জিভারাম নেতারাজ আন্নাদুরাই ১৯৬৩ সালে রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে বলেন, ‘যদি একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণেই হিন্দিকে সরকারি ভাষার মান্যতা দিতে হয়, তাহলে ময়ূরের বদলে কাক-কে জাতীয় পাখি ঘোষণা করা হোক।’
পরিস্থিতি বুঝে জওহারলাল নেহেরু সরকারি ভাষা আইনে রদবদল করেন। পরিবর্ত্তিত আইনে অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলিকে ১৯৬৫-এর পরও ইংরেজি চালু রাখার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু, ততদিনে দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। পুরো পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আগেই (১৯৬৪) নেহেরুর মৃত্যু হয়। কিন্তু, ১৯৬৫ সালের ১৬ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ ঘোষণা করে বসেন, ২৬ জানুয়ারি থেকে হিন্দিই হবে কেন্দ্রের সরকারি ভাষা। এর ফলাফলে তামুলনাড়ুতে সেই প্রজাতন্ত্র দিবসে আক্ষরিক অর্থেই আগুন জ্বলে ওঠে। ‘হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া’র প্রতিবাদে রঙ্গনাথন ও শিবলিঙ্গম নামের দুই যুবক নিজেদের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে আত্মাহুতি দেয়। প্রায় দুই মাস ধরে চলা রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে পুলিসে গুলিতে সরকারি হিসেবেই পঞ্চাশ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। পরিস্থিতির চাপে প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ‘ধীরে চলো’ নীতি গ্রহণ করেন। ভাষা বিতর্কের জেরে (আদতে দক্ষিণ-ভারতীয়) রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ ১৭ ফেব্রুয়ারি সংসদে ইংরেজিতে উদ্বোধনী ভাষণ দিলে তার প্রতিবাদে জনসঙ্ঘ ও সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট দলের সাংসদেরা অধিবেশন বয়কট করে।
মোদ্দা কথাটি হল, এই হিন্দি ভাষাকে কেন্দ্র করে সর্ব্বভারতীয় (বলা ভাল উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয়) রাজনৈতিক দলগুলি দক্ষিণ ভারতে দুর্ব্বল হতে শুরু করে। ১৯৬৭ সালের লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনে এদেশের ইতিহাসে প্রথমবার একটি আঞ্চলিক দল (দ্রাবিড় মুন্নেত্র কড়গম) বিপুল সংখ্যায় জয়লাভ করে।
এই সময়ে বাংলাভাষাও তার মর্যাদার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।‒ শুধু উর্দুর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বা পূর্ব্ব পাকিস্তানেই নয়, এদেশেও। তার মধ্যে ১৯১২ থেকে ১৯৫৬ অবধি চলা মানভূমের বাংলা ভাষা আন্দোলনটি পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম। তবে তারও একটি প্রেক্ষাপট আছে।‒ ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বাঙালি অধ্যুষিত মানভূম ও ধলভূম জেলা দুটি যথাক্রমে বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত হয়। এমনকি, কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবী স্বীকৃত হলেও ১৯৩৫ সালে বিহারের জাতীয় কংগ্রেস মন্ত্রী ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে ‘মানভূম বিহারী সমিতি’ নামক এক সংগঠন গড়ে ওঠে। এর বিপরীতে মানভূম জেলার বাঙালিরা ব্যারিস্টার পি.আর. দাসের সভাপতিত্বে ‘মানভূম সমিতি’ নামক সংগঠন তৈরী করে। বিহার সরকার এই জেলার আদিবাসী ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দি বিদ্যালয় খুলতে শুরু করলে বাঙালিরাও বাংলা স্কুল খুলতে উদ্যোগী হয়।
স্বাধীনতা অবধি এই টানাপোড়েন চলতে থাকে। মানুভূমের বাংলায় সংযুক্তি বা ছোটনাগপুর নামক নতুন প্রদেশ গঠনের দাবীও মাঝেমাঝে উঠতে থাকে। ১৯৪৮ সালের অতুলচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের পুরুলিয়া শহরের অধিবেশনে মানভূমের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব খারিজ হয়ে গেলে অতুলচন্দ্র ঘোষ সহ প্রায় চল্লিশজন নেতা-কর্মী জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ করে ‘লোকসেবক সংঘ’ তৈরী করেন। বিহার সরকার বাংলাভাষীদের প্রতিবাদসভা বা মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। লোকসেবক সংঘ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে। ঠিক এই সময়েই বিহারের স্কুল, কলেজ, সরকারি অফিসে হিন্দি বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে হলে অস্থিরতা আরো বেড়ে যায়। শুরু হয় ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও সেই আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগ দেয়। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে শুরু হয় টুসু সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ‘শুন বিহারী ভাই… তোরা রাখতে লারবি ডাঙ দেখাই… তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি… বাংলা ভাষায় দিলি ছাই’–এর মতো বেশ কিছু টুসু গান খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন মানভুম ভেঙে পুরুলিয়া জেলা গঠন করে পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্তির প্রস্তাব দিলে বিহারপন্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ও মানভূম জেলায় ধর্ম্মঘটের ডাক দেয়। দ্বিমুখী আন্দোলনের জেরে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীকৃষ্ণ সিং দুই রাজ্যের সংযুক্তির মাধ্যমে ‘পূর্ব্ব প্রদেশ’ নামক নতুন রাজ্য গঠনের প্রস্তাবনা করেন। পরিকল্পনা ছিল, বাংলা ও হিন্দি দুটি ভাষাই এই নতুন রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হবে। বিহারের বিধানসভায় এই প্রস্তাব পাস হলেও তার বিরুদ্ধে দুই রাজ্যেই সত্যাগ্রহ চলতে থাকে। লোকসেবক সংঘ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও বহু প্রবীন কংগ্রেসীও সেই আন্দোলনে সামিল হয়। পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া হয়ে কলকাতায় মহাকরণ অবরোধের উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয় এক বিশাল পদযাত্রা। ১৯৫৬ সালের ৭ই মে বি.বা.দী. বাগে প্রায় এক হাজার পদযাত্রাকারীদের গ্রেফতার করা হয়। অবশেষে, সেই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্ত হয়।
মানভূমের আন্দোলন শেষ হতে না হতেই আরেকদল বাঙালির লড়াই শুরু হয় আসামের বরাক উপত্যকায়। স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর একদা সহযোগী বিমলা প্রসাদ চালিহা আসামে মূখ্যমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অভিবাসী বাঙালিদেরকে পশ্চিমবঙ্গে সরিয়ে/ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবী করে বসেন। শুধু তাই নয়, দেশভাগের ফলে আসামে আশ্রয় নেওয়া তিন লক্ষ উদ্বাস্তুকেও অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে তাদের বিতাড়নের উদ্যোগ নিয়ে ফেলেন। তার যুক্তি ছিল, বাঙালির উপস্থিতিতে আসামের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হচ্ছে!
চালিহারই উদ্যোগে ১৯৬০ সালে অসমীয়াকে আসামের একমাত্র সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াতে প্রথমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমীয়া ও বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একতরফা আক্রমণে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাঙালি পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে বাধ্য হয়। লক্ষাধিক মানুষ আশ্রয় নেয় বরাক উপত্যকার কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি জেলায় ও উত্তর-পূর্ব্বের আরো কয়েকটি রাজ্যে। সেখানে গড়ে ওঠে ‘কাছাড় গণ সংগ্রাম পরিষদ’ নামক একটি সংগঠন। বাংলা ভাষার সমমর্যাদার দাবীতে শুরু হয় প্রতিবাদ। সংকল্প দিবস পালন, সত্যাগ্রহ, পিকেটিং, প্রতিবাদ সভা, পদযাত্রা চলতে থাকে পুরোদমে। এর মধ্যে প্রথম পদযাত্রাটি প্রায় দুশো মাইলের মাইলের বেশি পথ অতিক্রম করেছিল। দ্বিতীয় পদযাত্রার শেষে ঘোষণা করা হয় ১৩ মে, ১৯৬১-র মধ্যে বাংলা ভাষাকে অন্যতম সরকারি ভাষার স্বীকৃতি না দেওয়া হলে ১৯ মে ধর্ম্মঘটের ডাক দেওয়া হবে। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে আসাম সরকার কঠোর দমন নীতি গ্রহণ করে। বরাক উপত্যকা জুড়ে শুরু হয় কারফিউ। তারই ঘটনা পরম্পরায় ধর্ম্মঘটের দিন আধা-সামরিক বাহিনীর ছোঁড়া গুলিতে এগারো জন আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়। পরিস্থিতি আরো অশান্ত হয়ে উঠলে আসাম সরকার বরাক উপত্যকার জন্য বাংলা ভাষাকেও সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।
তবে বাংলা ভাষা যে শুধু আক্রান্তই হয়েছে, তা কিন্তু নয়। উত্তর-পূর্ব্বের আরেকটি অংশে সে ছিল বন্দুকের উলটো দিকে। সালটা ১৯৭৫, ভারতে তখনও এমার্জেন্সি ঘোষণা হয়নি। তার বছর তিনেক আগে আসাম রাজ্যের পুনর্গঠনে জন্ম নিয়েছে একটি নতুন রাজ্য– ত্রিপুরা। বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় বাংলা ভাষাই সেখানে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি পায়। কিন্তু, সে রাজ্যের আদিবাসিন্দাদের ভাষা ছিল ককবরক। শুরু হয় সেই ভাষার স্বীকৃতির দাবীতে আন্দোলন। সেদিন দক্ষিণ ত্রিপুরার জলাইবাড়িতে শুরু হয় একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল৷ সেখানেই আবার সেই পুলিশের গুলি, আবার মৃত্যু।– ওই কয়েকটি দশকে ইতিহাস যেন খুব দ্রুতগতিতে নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চলেছিল।
বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই যে আগ্রাসন-আন্দোলন-গোলাগুলি-মৃত্যুসংক্রান্ত তথ্যের শরশয্যা রচনা করা হল, বলাই বাহুল্য সেগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়। আর নথিবদ্ধ ইতিহাস মানেই সেখানে ভুলচুক, ভ্রান্তি, বিভ্রান্তি বা বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে। তবে মূল ঘটনাপ্রবাহগুলি যে বাস্তব, তা সন্দেহাতীত। কিন্তু, যে কথার শুরু হয়েছিল ভাষা নিয়ে, তার শেষটুকু এমন ঘোরতর ‘রাজনৈতিক’ হয়ে পড়া যন্ত্রণাদায়ক না হলেও অস্বস্তিকর তো বটেই। তার দায় কি ভাষার?– ঘালিবের শায়েরি শুনে একজন হিন্দিভাষীর মনে কি প্রেয়সীর মুখখানি উঁকি দেয় না?…
ইংল্যান্ড ও আমেরিকার পার্থক্য প্রসঙ্গে জর্জ বার্নার্ড শ্য বলেছিলেন,– ‘Two countries separated by one language’। সীমান্তের দুই পাড়ে বাংলা ভাষা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে আসার পর তেমনই কোনো বিভাজনের সম্মুখিন?– হিন্দুর বাংলা বনাম মুসলমানের বাংলা?– এই বিতর্কটি শতাব্দীপ্রাচীন। বলা যেতে পারে, হেলহেড ফরস্টার আর উইলিয়াম কেরির হাতে বাংলা ভাষার ‘সংস্কার’-এর সময়েই তার বীজটি বপন করা হয়েছিল। তারা ব্রাহ্মণ ও অভিজাত শ্রেণীর বাংলা ভাষার তৎসমঘেঁষা রূপটিকে আরো বেশি সংস্কৃতমুখি করে তুলেছিলেন। আরবি ফার্সি মুণ্ডারি মৈথিলী মিশ্রিত আমজনতার বাংলা ভাষাটি ছিল তাদের ধর্ত্তব্যের বাইরে। অবশ্য একথা ভুললেও চলবে না যে, তার আগেই সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষাগুলির গভীর সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছে। ফলে সাহেবদের এই সংস্কৃত প্রেম তাদের রাজনৈতিক অভিসন্ধির পাশাপাশি স্বজাতগর্ব্বের কারণেও জন্মে থাকতে পারে।
বাঙালি শিক্ষাব্যবস্থায় কেরি সাহেবের ‘সংস্কৃতায়িত’ বাংলা ভাষাকে আপন করলেও সেই সময় মুসলমানের সংস্কৃতচর্চার পথ খুব একটা সহজ হত না। বিশ্ববিদ্যালয় রাজী থাকলেও সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকদের অনেকেই ছিলেন গোঁড়া বামুন, তাদের অনেকেরই মারাত্মক ছুৎমার্গ ছিল। মুসলমান হওয়ার কারণে মুহম্মদ শাহীদুল্লাহার বা খ্রিস্টান হওয়ার কারণে সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতো মানুষেরও সংস্কৃত নিয়ে পড়াশোনা বা শিক্ষাকতা বিষয়ে বহু বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় হিন্দু বুদ্ধিজীবিরা এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চারও হয়েছিলেন। তবে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বঙ্গদেশের একদল মুসলমান বুদ্ধিজীবিদের উপলব্ধি হচ্ছিল বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতিগত কারণের জন্য হলেও বাংলা ভাষায় কিছু কিছু আরবি ফারসি তুর্কি শব্দকে ‘ফিরিয়ে আনা’ প্রয়োজন।
১৯২৫-২৬ সাল নাগাদ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি তুর্কি শব্দের স্বীকৃতির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন জানায়। বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যে তারা গলা চড়িয়ে ঘোষণা করে– হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালির ভাষা আলাদা, এবং সংস্কৃতপ্রেমী আরবি-ফারসি বিরোধী হিন্দুদের জন্যই মুসলিম সাহিত্য সৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।
ততদিনে এমন একটা ধারণা জন্মে গিয়েছে যে, মুসলিম সাহিত্য রচনার জন্য আরবি-ফারসি শব্দ আবশ্যিক উপাদান। ওয়াজেদ আলি সহ মুসলমান বুদ্ধিজীবিদের কয়েকজন আবার সেই শব্দগুলির শুদ্ধ উচ্চারণ নিশ্চিত করার জন্য বাংলা বর্ণমালার সংস্কারের প্রসঙ্গও তোলেন। তারা চেয়েছিলেন কিছু কিছু উর্দু (আদতে ফারসি) বর্ণের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য প্রায়-সমোচ্চারিত বাংলা বর্ণগুলির ওপর আরোপ করা হোক। তবে মুসলমান বুদ্ধিজীবিদের সিংহভাগই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, বর্ণমালাকে ‘বিকৃত’ করার বদলে ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য রচনাই যথেষ্ট।
কিন্তু, এর পরেই ঢাকার মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের পাঠ্যবইতে চিরাগ, খোয়াব, পানাহ্, গুনাহ্, খোয়াব, এলেম, বেফিকর– জাতীয় শব্দের আধিক্য দেখা দিতে শুরু করে। তা নিয়ে প্রবাসী পত্রিকায় ‘মুসলমানের হিন্দু বিদ্বেষে’র কথা ওঠে। রবীন্দ্রনাথও মুখ খোলেন,– ‘বহুকাল মুসলমানের সংস্রবে থাকাতে বাংলা ভাষাও অনেক পারসী শব্দ এবং কিছু কিছু আরবীও স্বভাবতই গ্রহণ করেছে। বস্তুত বাংলা ভাষা যে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আপন তার স্বাভাবিক প্রমাণ ভাষার মধ্যে প্রচুর রয়েছে। যত বড়ো নিষ্ঠাবান হিন্দুই হোক-না কেন ঘোরতর রাগারাগির দিনেও প্রতিদিনের ব্যবহারে রাশি রাশি তৎসম ও তদ্ভব মুসলমানী শব্দ উচ্চারণ করতে তাদের কোনো সংকোচ বোধ হয় না। এমন-কি, সে-সকল শব্দের জায়গায় যদি সংস্কৃত প্রতিশব্দ চালানো যায় তা হলে পণ্ডিতী করা হচ্ছে বলে লোকে হাসবে। বাজারে এসে সহস্র টাকার নোট ভাঙানোর চেয়ে হাজার টাকার নোট ভাঙানো সহজ।… ‘মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে’, এ কথা সহজেই মুখ দিয়ে বেরোয় কিন্তু যাবনিক সংসর্গ বাঁচিয়ে যদি বলতে চাই মনের গতিকটা বিকল কিংবা বিমর্ষ বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছে তবে আত্মীয়দের মনে নিশ্চিত খটকা লাগবে।… নেশাখোরকে যদি মাদকসেবী বলে বসি তা হলে খামকা তার নেশা ছুটে যেতে পারে, এমন-কি, সে মনে করতে পারে তাকে একটা উচ্চ উপাধি দেওয়া হল। বদমায়েসকে দুর্বৃত্ত বললে তার চোট তেমন বেশি লাগবে না। এই শব্দগুলি যে এত জোর পেয়েছে তার কারণ বাংলা ভাষার প্রাণের সঙ্গে এদের সহজে যোগ হয়েছে।’ (সূত্র: ‘ভাষাতত্ত্ব’ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
কিন্তু, তিনি একথাও বলেন–‘শিশুপাঠ্য বাংলা কেতাবে গায়ের জোরে আরবীআনা পারসীআনা করাটাকেই আচারনিষ্ঠ মুসলমান যদি সাধুতা বলে জ্ঞান করেন তবে ইংরেজি স্কুলপাঠ্যের ভাষাকেও মাঝে মাঝে পারসী বা আরবী ছিটিয়ে শোধন না করেন কেন?… মৌলবী ছাহাব প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ইংরেজি সাহিত্যিক ভাষার এ রকম মুসলমানীকরণের চেষ্টা করবেন না। করলেও ইংরেজি যাঁদের মাতৃভাষা এ দেশের বিদ্যালয়ে তাঁদের ভাষার এ রকম ব্যঙ্গীকরণে উচ্চাসন থেকে তাঁদের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হবে।…
বাংলা দেশের গোঁড়া মক্তবেও ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে এ রকম অপঘাত ঘটবে না; ইংরেজের অসন্তুষ্টিই তার একমাত্র কারণ নয়। শিক্ষক জানেন পাঠ্যপুস্তকে ইংরেজিকে বিকৃতি করার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিলে ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষায় গলদ ঘটবে, তারা ঐ ভাষা সম্যকরূপে ব্যবহার করতে পারবে না।… মৌলবী ছাহাব বলতে পারেন আমরা ঘরে যে বাংলা বলি সেটা ফারসী আরবী জড়ানো, সেইটাকেই মুসলমান ছেলেদের বাংলা বলে আমরা চালাব। আধুনিক ইংরেজি ভাষায় যাঁদের অ্যাংলোইণ্ডিয়ান বলে, তাঁরা ঘরে যে ইংরেজি বলেন, সকলেই জানেন সেটা আন্ডিফাইল্ড আদর্শ ইংরেজি নয়—স্বসম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতবশত তাঁরা যদি বলেন যে, তাঁদের ছেলেদের জন্যে সেই অ্যাংলোইণ্ডিয়ানী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা না করলে তাঁদের অসম্মান হবে, তবে সে কথাটা বিনা হাস্যে গম্ভীরভাবে নেওয়া চলবে না।…
হিন্দু বাঙালির সূর্যই সূর্য আর মুসলমান বাঙালির সূর্য তাম্বু, এমনতর বিদ্রূপেও যদি মনে সংকোচ না জন্মে, এতকাল একত্রবাসের পরেও প্রতিবেশীর আড়াআড়ি ধরাতলে মাথা-ভাঙাভাঙি ছাড়িয়ে যদি অবশেষে চন্দ্রসূর্যের ভাষাগত অধিকার নিয়ে অভ্রভেদী হয়ে ওঠে, তবে আমাদের ন্যাশনাল ভাগ্যকে কি কৌতুকপ্রিয় বলব, না বলব পাড়া-কুঁদুলে।… পৃথিবীতে কম্যুনাল বিরোধ অনেক দেশে অনেক রকম চেহারা ধরেছে, কিন্তু বাংলা দেশে সেটা এই যে কিম্ভুতকিমাকার রূপ ধরল তাতে আর মান থাকে না।’
(সূত্র: ‘ভাষাতত্ত্ব’ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
এর প্রত্যুত্তরে ‘গুলিস্তাঁ’ পত্রিকার একটি প্রবন্ধে সাহিত্যিক ওয়াজেদ আলি রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে বলেন, মুসলমানের সংস্কৃতির সঙ্গে আরবি ফারসি তুর্কি উর্দু ভাষার সম্পর্ক অভেদ্য। আর সেই সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় উক্ত ভাষাগুলি থেকে শব্দ বা ভাবের অনুপ্রবেশ কেউ রুখতে পারবে না।
অচিরেই এই বিতর্কে প্রবাসী ছাড়াও ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, রূপরেখা, বসুমতী, ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা পুরোদস্তুর মশগুল হয়ে ওঠে। তখন কিছুটা বিরক্ত ও আহত হয়েই রবীন্দ্রনাথ আলতাফ চৌধুরীকে লেখেন, ‘আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চলছে তার মতো বর্বরতা আর হতে পারে না। এ যেন ভাইয়ের উপর রাগ করে পারিবারিক বাস্তুঘরে আগুন লাগানো। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের দেশ-ভাষাকে পীড়িত করবার উদ্যোগ কোনো সভ্য দেশে দেখা যায় নি। এমনতর নির্মম অন্ধতা বাংলা প্রদেশেই এত বড়ো স্পর্ধার সঙ্গে আজ দেখা দিয়েছে বলে আমি লজ্জা বোধ করি। বাংলা দেশের মুসলমানকে যদি বাঙালি বলে গণ্য না করতুম তবে সাহিত্যিক এই অদ্ভুত কদাচার সম্বন্ধে তাঁদের কঠিন নিন্দা ঘোষণা করে সান্ত্বনা পেতে পারতুম। কিন্তু জগতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ-প্রসূত এই মূঢ়তার গ্লানি নিজে স্বীকার না ক’রে উপায় কি?…
উত্তর-পশ্চিমে, সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব নেই। সে-সকল প্রদেশে অনেক হিন্দু উর্দু ব্যবহার করে থাকেন, তাঁরা আড়াআড়ি করে উর্দুভাষায় সংস্কৃত শব্দ অসংগতভাবে মিশল করতে থাকবেন, তাঁদের কাছ থেকে এমনতর প্রমত্ততা প্রত্যাশা করতে পারি নে। এ রকম অদ্ভুত আচরণ কেবলই কি ঘটতে পারবে বিশ্বজগতের মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশে? আমাদের রক্তে এই মোহ মিশ্রিত হতে পারল কোথা থেকে?’ (সূত্র: ‘ভাষাতত্ত্ব’ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
এই দ্বন্দ্বের নিরসন কি আজও হয়েছে?– বোধ হয় না। আজ অনেকে ‘নাশতা’ করলেও জলখাবার ছোঁন না। আবার অনেক আধুনিকমনষ্কেরও জলখাবারের বদলে ‘স্ন্যাক্স্’, ‘টিফিন’ বা ‘ব্রেকফাস্টে’ অধিক রুচি। সংস্কৃতের প্রাসঙ্গিকতা কমেছে, হয়তো বা ফারসিরও। তাদের বদলে এক পক্ষ হিন্দি ও ইংরেজি শব্দের আমদানি বৃদ্ধি করলে অন্য পক্ষ ঝুঁকেছে আরবি শব্দের প্রতি। এদিকে হিন্দি নিজেই আরবি ফারসির কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী। অর্থাৎ, খিচুড়িটি রেঁধে বেড়ে খেয়ে হজম হয়ে গেলেও ডাল-চালের বিবাদ মেটেনি! অতয়েব, মোক্ষম প্রশ্নটি হল– শব্দের এমন জাত নির্ণয় কি আদৌ যুক্তিপূর্ণ? উত্তরের খোঁজে যদি (চূড়ান্ত অনৈতিক ভাবে) উর্দু সহ মধ্যপ্রাচ্যের ভাষাগুলিকে মুসলমানের ভাষা ও সংস্কৃত সহ ভারতীয় ভাষাগুলিকে হিন্দুর ভাষা ধরে নেওয়াও হয়, তাও এর উত্তর ‘না’-ই হয়।
কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক।– প্রচলিত ধারণা অনুসারে বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা, দাদু-দিদা, দিদি, পিসি, কাকা, জেঠি, জল– এগুলি হিন্দু শব্দ ও অন্যদিকে আব্বা-আম্মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, আপা, বুয়া, চাচা, ফুফু, পানি– এগুলি মুসলমান শব্দ। কিন্তু, শব্দগুলির উৎস কী?–
‘মা’ শব্দটির সংস্কৃতযোগ বিষয়ে দ্বিধা নেই। তবে ‘বাপ’ বা ‘বাপু’ ও তাদের আধুনিক সংস্করণ ‘বাপি’– শব্দগুলি সংস্কৃত ‘বপ্তা’ থেকে সৃষ্ট হলেও ‘বাবা’ শব্দটি আদতে ফারসি। ‘আব্বা’ শব্দের উৎস আরবি ‘আবু’। ‘আম্মা’ শব্দটির উৎস একদিক থেকে মধ্যপ্রাচ্য হলেও জন্মদাত্রীর নামে ‘ম’ ধ্বনির উপস্থিতি বিশ্বের প্রায় সবকটি ভাষারই বৈশিষ্ট্য। ইংরেজির ‘মাদার তো বটেই, জার্মানে তা ‘মাট্টার’, ডাচ ভাষায় ‘ময়েদার’, ইতালিয়ানে ‘মাদর’, চীনা (ম্যান্দারিন) ভাষায় ‘মামা’, মিশরীয় ভাষায় ‘মাত’, বাংলা ও আফ্রিকার বেশ কিছু ভাষায় ‘মা’ ছাড়াও তামিলে তা ‘আম্মা’ই।
‘চাচা’ শব্দটি সংস্কৃতের তদ্ভব। সংস্কৃত ‘তাতঃ’ থেকে হিন্দুস্তানি ‘চাচ/ চচ্চা’ হয়ে হিন্দির ‘চাচা’ অবিকৃত অবস্থায় বাংলায় প্রবেশ করেছে। অন্যদিকে, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ অনুসারে, তথাকথিত হিন্দু-শব্দ ‘কাকা’ আসলে ফারসি শব্দ। সেই তুলনায় বর্ত্তমানে অপ্রচলিত ‘খুড়ো’ বা ‘খুড়া’ শব্দগুলি সংস্কৃত ‘খুল্লতাতঃ’-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
‘ঠাকুর’ শব্দটির উৎস তুর্কি। এই তথ্যে অনেকেরই চমক লাগতে পারে, কারণ সংস্কৃত অভিধানে সমার্থক ‘ঠক্কুর’ শব্দটির উল্লেখ আছে। ‘শব্দকল্পদ্রুম’ অনুসারে, ‘ঠক্কুর’ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ‘অনন্তসংহিতা’ নামক একটি গ্রন্থে। এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ। সুতরাং, পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ রচিত হওয়ার দরুন সমসাময়িক সংস্কৃতে তুর্কি শব্দের আগমন অসম্ভব কিছু নয়। ঘটনাচক্রে, সংস্কৃত ভাষায় ‘ঠ’ ধ্বনির উপস্থিতি খুবই সীমিত, ‘ঠ’ দিয়ে শুরু শব্দের সংখ্যাও মাত্র তিন;– ঠঃ (শিব, মহাধ্বনি), ঠক্কুর ও ঠের (বৃদ্ধা)। রামেশ্বর শ-এর মতে, তুর্কি ‘তাগরি’ থেকে ‘ঠাগরি’ হয়ে সৃষ্ট ‘ঠাকুর’ শব্দটি সংস্কৃতে ‘ঠক্কুর’ হয়েছে। স্যার মনেয়ার উইলিয়ামসের প্রবাদপ্রতীম সংস্কৃত অভিধান অনুসারে ‘ঠক্কুর’ শব্দটি আবার ‘ধূর্ত্ত’-এর সঙ্গে সম্পর্কিত! যাই হোক, মূল তুর্কি শব্দটির অর্থ ‘প্রধান’ বা ‘কর্ত্তা’।– দেবতা, গাঁয়ের মোড়ল, বা বামুনের ‘ঠাকুর’-পদবাচ্য হওয়া সেই কারণেই।
অন্যদিকে ‘দাদা’ শব্দটি আবার সংস্কৃত ‘তাত’ শব্দ থেকে সৃষ্ট। অর্থও প্রায় অপরিবর্ত্তিত। উত্তর ভারতীয় হিন্দুরাও শব্দটি ব্যবহার করে। বাংলাতেও জেষ্ঠ্য সহোদর বা মস্তানকে ‘দাদা’ ডাকা হয়, মাতামহকেও ‘দাদু’ ডাকলে সমস্যা হয় না। শুধু পিতামহের বেলায় তা হঠাৎ মুসলমান শব্দে পরিণত হয়! আসলে এই শব্দটিও কতৃত্ববাচক। তাই সহোদরদের মধ্য বা পুরো পরিবারের মধ্যে বা সমাজের মধ্যে যারা বয়স, সম্পর্ক বা ক্ষমতার কারণে কর্ত্তা,– তারা সবাই ‘দাদা’ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ অনুসারে ‘নানা’ শব্দটি আবার মুণ্ডারী বা অষ্ট্রিক। ‘দাদা’ শব্দের মতো এটিকেও উত্তর ভারতীয় হিন্দুরা ব্যবহার করে।
‘দাদা’ সংস্কৃতজাত হলেও ‘দিদি’ শব্দটি আদতে ফারসি। বরং, ‘বুবু’ শব্দটি সংস্কৃত ‘ভগিনী’র সঙ্গে সম্পর্কিত। শব্দটির যাত্রাপথ কিছুটা এমন,– ভগিনী→ ভইন→ বহিন→ বইন→ বোন→ বুন→ বু ও শেষে ‘বু’ ধ্বনির দ্বিত্ব। অনেকের মতে ‘আপা’ শব্দটি তুর্কি। কিন্তু, ‘হড় প্রাকৃত ভাষায়’ (সাঁওতালি) ‘আপা’ শব্দের অর্থ ‘কুমারী’/ ‘মাতা’, অসমীয়া ভাষায় ‘আপা আপী’-এর অর্থ ‘ছেলে মেয়ে’।
সংস্কৃত ‘পয়ঃ’ ধাতু থেকে ‘পানীয়’, আর তার থেকে ‘পানি’। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে ‘পনি’ শব্দের অর্থ দুধ, মদ, পানীয় জল সবকিছুই হতে পারে, তবে শেষ অবধি শব্দটির অর্থ ‘জল’-এ পরিণত হয়েছে। (এই ধরণের শব্দকে ‘যোগরূঢ় শব্দ’ বলা হয়।)
ছান্দস (বৈদিক) ও প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় ‘অপ’, ‘নীর’, ‘বারি’– শব্দগুলির ব্যবহার থাকলেও ‘জল’ শব্দের ব্যবহার তেমন নেই। তবে ‘জল’ শব্দটিও সংস্কৃতজাত, ‘জল্’ ধাতু থেকে তার সৃষ্টি। √জল্ = জীবন। জনন বা সৃষ্টি (জ)-কে যা লালন (ল) করে, তা হল ‘জল’। ক্রিয়াভিত্তিকতার নীরিখে, বস্তু-জলকে কেন্দ্রে রাখলে পানি ও জল শব্দদুটি আসলে বক্তার দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ। ওই তরলপদার্থটিকে যে পেয় হিসেবে দেখছে, তার কাছে তা ‘পানি’ আর যে ‘সৃষ্টিকে লালনকারী’ হিসেবে দেখছে তার কাছে তা ‘জল’। তবে বর্ত্তমানের ব্যাবহারিক দিক থেকে (শব্দার্থের লোগোসেন্ট্রিক নিয়মে) পানি ও জল, শব্দ দুটি বস্তু-জলের দুটি নাম মাত্র।– সে পানযোগ্য না হলেও, লালনকারীর বদলে প্রাণঘাতি হলেও কিছু আসে যায় না।…
সে যাই হোক, দুটি ‘নাম’ই সংস্কৃতজাত, অথচ তাদেরও হিন্দু-মুসলমান বিভেদ! অথচ, চৈতন্যভাগবত (‘আহার পাণি নিদ্রা রহিত’), শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (‘যৌবন রাধে পাণির ফোঁটা’), চণ্ডীদাসের রচনায় (‘জোয়ারের পাণি, নারীর যৌবন’) থেকে শুরু করে কাশীদাসী মহাভারত (‘চক্ষে বহে পাণি’) বা কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবধি সর্ব্বত্র ‘পানি’র প্রাচীনতর রূপ ‘পাণি’ শব্দটিকে দেখা যায়।
এমন আরো কত উদাহরণ যে দেওয়া যায়, তার ইয়ত্তা নেই। তাই বলা চলে, বাংলা ভাষা থেকে মুসলমানি অনুষঙ্গ কাটছাঁট করলে আক্ষরিক অর্থেই ‘বাবা’র নাম যাবে বদলে, তখন মান থাকলেও ‘ইজ্জত’ থাকবে না, ‘চাকরি-বাকরি’ সব উবে যাবে, ‘রোজগার’ও হবে অদৃশ্য। ‘দোয়াত’-‘কলম’ থাকবে না, ‘কাগজ’ও নয়। ‘আইন’ ‘কানুন’ দুটোই যাবে রসাতলে, তখন ‘আদালতে’র বদলে বিচারালয় খুঁজে পেলেও না মিলবে ‘দলিল’, না হবে ‘মামলা’, ‘ফয়সালা’র তো প্রশ্নই নেই। উলটো দিক থেকে, বাংলাকে সংস্কৃতমুক্ত করলে যা থাকবে, তা ভাষা নয়, ভাষার কংকাল।
ভাষার বা শব্দের কোনো ধর্ম্ম হয় না। তা জাতির চেতনার অভিব্যক্তি। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জাতির অভ্যন্তরীণ বোধের প্রকাশ। ভাষার শিকড় হচ্ছে জাতির কৃষ্টি, ডালপালাগুলি হল ছোট-বড় বিভিন্ন বিষয়ে জাতির সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিগুলি। সে একটি চলমান প্রক্রিয়া। নিজের বিকাশের প্রয়োজনে সে প্রাকৃতিকভাবেই অন্য একটি ভাষার বা কৃষ্টির কাছ থেকে শেখে, তারপর নিজের মতো করে আত্তীকরণ ঘটায়। গাজোয়ারি বা কৃত্রিম অনুপ্রবেশগুলিই বরং বেমানান, বেখাপ্পা। কিন্তু, দুটি আলাদা ভাষা বা কৃষ্টির মধ্যে ‘বৈচিত্র’ থাকতে পারে ‘বৈরিতা’ থাকে কি? হিন্দি বনাম উর্দু, হিন্দি বনাম তামিল, হিন্দি বনাম বাংলা বা হিন্দু বাংলা বনাম মুসলমানি বাংলা– এগুলি কি আদৌ প্রতিপক্ষ?
এখানেই প্রশ্নগুলি ভাষা বা কৃষ্টির খাসমহল ছাড়িয়ে জাতিয়তাবাদের অন্ধকার দিকটিতে প্রবেশ করে। দেশের/ জাতির/ সংস্কৃতির/ ভাষার প্রতি ‘ভালবাসা’ আর তাকে অন্যের তুলনায় ‘শ্রেষ্ঠতর ভাবা’ এক নয়। শুধুমাত্র আমি জন্মেছি বলেই গায়ের জোরে বা আবেগের তোড়ে আমার দেশটি ‘সকল দেশের সেরা’ হয়ে যায় না। এই তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতার মধ্যেই হিংস্রতার বীজ লুকিয়ে থাকে। বোধহয় এই জায়গা থেকেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ ও অহিংসার সহাবস্থানের বাস্তবতা নিয়ে গান্ধীজীর কাছে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।
ভাষার ক্ষমতা অসীম, কিন্তু ক্ষমতার ভাষা মারাত্মক। আক্রমণকারী বা আক্রান্ত– কারো সংস্কৃতির প্রতিই তার সম্মান বা ভালবাসা থাকে না, তার থাকে স্বার্থ। ভাষা বা সংস্কৃতি তার হাতিয়ার মাত্র। হেজিমনি প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্থুল বা সূক্ষ্ম ভাবে স্রেফ নিজেরটিকে অন্যেরটির ওপরে চাপিয়ে দিতে চায়। ভাষার জগতে এই ‘আধিপত্যশীলতা’ই হল ভাষার সাম্রাজ্যবাদ। ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জাতির ইতিহাস দর্শন জ্ঞান ঐতিহ্য। একবার সেখানে হীনমন্যতা সৃষ্টি করানো সম্ভব হলে অনায়াসেই প্রোপাগ্যান্ডা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।
বিষয়টি ছোট মাপকাঠিতে বোঝার জন্য বর্ত্তমান বাঙালির বাংলাবিমুখতার সাধারণ অজুহাতগুলির দিকে নজর দেওয়া যাক;- ১. নাম্বার কম ওঠে। (অর্থাৎ, ভবিষ্যতে রোজগারের সুযোগ কম।) ২. বাংলার বাজার নেই। (একই, রোজগারের সুযোগ কম।) ৩. ইংরেজি না শিখলে লোকে আনস্মার্ট বলে। (আসল কারণ হীনমন্যতা। যদিও একটি ভাষা জানার সঙ্গে অন্য ভাষাটি না-জানার সম্পর্ক রহস্যময়!) ৪. ইংরেজি না জানলে বিপরীত লিঙ্গের মনোযোগ মেলে না। (হীনমন্যতা ও যৌনতা)…
এই তালিকাটি যত দীর্ঘই করা যাক না কেন, প্রবন্ধটির শুরুর দিকে যেমন বলা হয়েছিল, তথাকথিক ‘সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে’র পেছনে ঘুরে-ফিরে সেই আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, হীনমন্যতা আর যৌনতাকেই খুঁজে পওয়া যাবে।
কিন্তু, এত-শত কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি কী?– ‘আধুনিক পুঁজিবাদের পক্ষে অবাধ ও ব্যাপক বাণিজ্যের জন্য বাজারের পাশাপাশি প্রতিটি মালিক, ক্রেতা ও বিক্রেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত্ত হল ভাষার ঐক্য।’… উক্তিটি লেনিনের (সূত্র: ‘জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের আধিকার’, প্রগতি প্রকাশন)। ভদ্রলোকের আদর্শগত অবস্থানের কথা বাদ দিয়ে শুধু এই কথাটির মেরিট বিচার করে দেখলেও ছবিটি স্পষ্ট হয়। উক্ত প্রবন্ধেই লেনিন আরো বলেছিলেন, ‘কায়েমী স্বার্থসম্পন্নদের কাছে ভাষার ঐক্য মানে এমন এক ভূখণ্ড, যার অধিবাসীরা একই ভাষায় কথা বলে। তাই ভাষার ঐক্যের জন্য তারা ভাষার বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করতে চায়।’… তবে ভাগ্যের এমন পরিহাস যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের অন্যতম কারণ ছিল ইউনিয়নের বাদবাকি প্রদেশগুলিতে রুশ ভাষা ও সংস্কৃতির আগ্রাসন!
সে যাই হোক, লেনিনের কথাগুলি বিশ্বাস করতে কষ্ট হলে ভেবে দেখুন, বর্ত্তমানের দিল্লি, বোম্বে, দুবাই, দোহা, লন্ডন, ব্রাশেলস্, ফ্র্যাংকফার্ট, প্যারিস, মাদ্রিদ, নিউইয়র্ক– পৃথিবীর প্রায় সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলি একই ধাঁচের। বিশ্বের অধিকাংশ চার-পাঁচতারা হোটেল, রেঁস্তোরা, কর্পোরেট অফিস থেকে শুরু করে বড় বড় শহরের মুদির দোকান (ডিপার্টমেন্টাল স্টোর), কাপড়ের দোকান অবধি একই ধাঁচে গড়া। কফিশপ্ কি মধুশালার বিভিন্ন ‘থিম্’ থাকলেও সেগুলিও নির্দিষ্ট।
শুধু তাই-ই নয়, বর্ত্তমানে তথাকথিত ‘সাফল্যে’র যে ঘোর-পশ্চিমা ধাঁচাটি (template) চালু আছে, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই তা অনুরূপ তো বটেই, প্রায় সমস্ত ‘সফল’ মানুষদের জীবনযাত্রার ছিরিছাঁদও এক।– এর পিছনের যুক্তি হিসেবে কেউ স্ট্যান্ডর্ডাইজেশানের কথা বলতেই পারেন। কিন্তু, প্রমিতকরণের অর্থ বোধ হয় বৈচিত্রকে উপেক্ষা করা নয়। পক্ষ-বিপক্ষ বা নিন্দা-প্রশংসার প্রসঙ্গে নয়, ভেবে দেখুন না– মুক্ত বাণিজ্য বা বিশ্বায়ন যদি সত্যিই ‘উদারিকরণ’ হত, তাহলে এই একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে অধিকাংশ দেশের মাথায় রক্ষণশীল দল বা শক্তিগুলি অবস্থান করছে কেন?
আসলে, পণ্য-সভ্যতা বা বাজার-সংস্কৃতির প্রবেশপথটিই হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। তবে সে এই কম্মটি অত্যন্ত সচতুরভাবে সম্পন্ন করে। প্রথমেই সে ‘সংস্কৃতি’র ধারণাটিকেই কেঁটে-ছেঁটে কাব্য-সাহিত্য-ললিতকলায় সীমাবদ্ধ করে ফেলে তার চারআনার অলঙ্করণ আর বারোআনার বাণিজ্যিকরণ সেরে বুঝিয়ে দেয়– এই তো তোমার সংস্কৃতি সপ্রতিভায় উদ্ভাসিত!
কিন্তু, এই বুদ্বুদ চিরস্থায়ী হয় না, হয়ওনি। গতকাল মুক্ত বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশই আজকে হয় অর্থনৈতিক নতুবা সাংস্কৃতিক অথবা একযোগে দ্বিবিধ সঙ্কটেরই মুখোমুখি। সহজ করে বললে, এই সঙ্কটের প্রতিক্রিয়াতেই বিশ্বজুড়ে রক্ষণশীলদের উত্থান। আপনি ব্যক্তিগত ভাবে উদারপন্থি হতেই পারেন, তাই বলে বাকিদের গোঁড়া বা মূর্খ ভাবার কোনো কারণ নেই। এই মুহূর্ত্তে ভারত বা তার প্রতিবেশি দেশগুলির সঙ্কটের অভিমুখ মূলত সাংস্কৃতিক। তাই অন্ধ আবেগে খোলা বাজারের দিকে ছুটলেও তাদের সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।
প্রশ্ন উঠতে পারে, যেখানে মুক্ত বাণিজ্য বা বিশ্বায়ন মূলত একটি অর্থনীতিক প্রক্রিয়া, সেখানে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিষয়টিকে স্বীকার করলেও তা বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতিক বা সামাজিক সঙ্কটের কারণ হয়ে উঠতে পারে কি?– বিশেষত পশ্চিমা দেশগুলিতেও?– যারা নিজেরাই কিনা এই ধাঁচাটির স্রষ্টা!
খুব সহজ ভাষায়, মুক্ত বাণিজ্য বা বিশ্বায়নের অন্যতম শর্ত্ত হল স্পেশালাইজেশান।– যে দেশ যে পণ্য(গুলি) উৎপাদনে কুশলী বা উপযোগী, সেই দেশ সেই পণ্য(গুলি)ই উৎপাদন করে বাকিদের রপ্তানি করবে ও নিজের প্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্যগুলি আমদানি করবে। কোনো একক দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা আত্মনির্ভরতা নয়, এই আমদানি-রপ্তানির মসৃণ গতিপথের ওপরেই নির্ভর করে বিশ্বায়নের সাফল্য। এখন এই শর্ত্তের বশে যদি (উদাহরণ হিসেবে) স্কটল্যান্ড শুধুই হুইস্কি উৎপাদনে, ইতালি শুধুই জুতো উৎপাদনে, বেলজিয়াম শুধুই সুগন্ধী উৎপাদনে, ভারত শুধুই তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিষেবায়, জার্মানি শুধুই মোটরগাড়ি উৎপাদনে, বাংলাদেশ শুধুই বস্ত্র উৎপাদনে লিপ্ত হয়, তাহলে একটা সময়ের পর সেই একঝোঁকামির ফলে দেশগুলির বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিকই শুধু নয় সামাজিক ভারসাম্যও বিগরোতে শুরু করে।
ভেবে দেখুন না, সমাজের প্রত্যেকে যদি শুধুমাত্র দু-চারটি পেশাকেই পরম ও চরম লক্ষ্য ভেবে ছুটতে শুরু করে, শিক্ষা-সংস্কৃতি-আদর্শ– কোনো দিক থেকেই তাকে স্বাভাবিক বলা যায় কি?– এরই ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞানকে প্রযুক্তির তুলনায়, জীববিদ্যাকে পদার্থবিদ্যার তুলনায় বা কলা (art)-কে বিজ্ঞানের তুলনায় গুরুত্বহীন মনে হয়। ‘ক্ষেত্র-ক্ষত্র-ক্ষত্রিয়ে’র দেশে, ‘জয় জওয়ান জয় কিশানে’র দেশে ‘চাষা’ শব্দটিই অবজ্ঞাসূচক হয়ে ওঠে। বিশ্বাস ও আচারের পথ ভিন্ন হতে শুরু করে।– এই প্রেক্ষাপট ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পুরো সংস্কৃতিরই লঘু-গুরু এক করে দেয়।
ব্যক্তিগত জীবনেও স্পেশালাইজেশানের একপিঠে কোনো একটি-দুটি বিষয়ে পারদর্শিতা থাকলে, তার উলটো পিঠে আরো দশটি বিষয়ের আকাট মূর্খতা অবস্থান করে। সে থাকতেই পারে। কোনো মানুষের পক্ষেই সবকিছু জেনে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু, তার স্পেশালাইজেশানের বাণিজ্যিক বা সামাজিক বাজারদর চড়া হলে সে তার মূর্খতার ক্ষেত্রগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বা হেয় মনে করে। ভাবখানা এই– আমি যা জানি না, সেগুলো জানার কোনো দরকারই নেই! ছোট পরিসরের উদাহরণে, বহু বিজ্ঞানের ছাত্র যেমন ইতিহাস-ভূগোলকে ‘ফালতু’ বা বহু সাহিত্যের ছাত্র যেমন অঙ্ককে ‘অত্যাধিক’ মনে করে।
দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, যখন ব্যক্তিগত তথা জাতিগত সংস্কৃতির বনিয়াদের ফাটল চোখে পড়ে না, তখন প্রতিবেশীর পেরেক ঠোকাকেই দেওয়াল কাঁপার ‘কারণ’ মনে হয়। সংস্কৃতির অভাবে বহু রকম ‘কুসংস্কার’ও জাঁকিয়ে বসে। আসলে, ‘উত্তর না মিললে রেফারেন্স খোঁজা’র অভ্যেস তো আজকের নয়। কিন্তু, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ‘অমুক করতে হয়, তমুক করতে নেই’ জাতীয় নির্দিষ্ট কোনো রূপরেখাও হয় না। ফলে অনেক সময় তথাকথিত আসমানি কিতাবগুলিকে– বলা ভাল, ‘ধর্মীয় বইপত্রে অমুকটা লেখা আছে’ জাতীয় ধারণাগুলিকেই একমাত্র সমাধান মনে হয়। তার উৎস বা অভিমুখ যা-ই হোক না কেন, সাংস্কৃতিক সঙ্কটের সময় প্রায়শই ‘religion’ অর্থে ধর্ম্মই একমাত্র সংস্কৃতি হয়ে ওঠে।
ভেবে দেখুন, যে মানুষ পাণ্ডিত্যের মদগর্ব্বে বুঁদ হয়ে থাকার সময় ‘বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ যাতি পাত্রতাম্’ (‘হিতোপদেশঃ’)– জাতীয় তথাকথিত ধর্ম্মগ্রন্থীয় বাণীগুলি উপেক্ষা করেছে, সঙ্কটকালে তারাও ধর্ম্মগ্রন্থের ধূষর অংশের অপব্যাখ্যাগুলির পক্ষে গলা ফাটাতে শুরু করে।
পছন্দ হোক বা অপছন্দ, প্রতিটি তথাকথিত রাজনৈতিক প্রপঞ্চের পিছনে সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদন থাকে।– সেই অনুমোদনের প্রকৃতি সবসময় সার্ব্বভৌম না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ তো বটেই। এই গোষ্ঠীগত মনোভাব, বিশ্বাস আর অনুভূতি– এই তিনটি উপাদান (ও কিছু ক্ষেত্রে ‘religion’ অর্থে ধর্ম্মও) গড়ে তোলে সেই গোষ্ঠীর নতুন সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিকে শুধু যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তা-ই নয়, মাঝেমাঝে তাদের স্বপক্ষের ওজর যুক্তি হয়ে ওঠে।
একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, ক্ষমতার রাজনীতিতে সংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তাই কার্য্য-কারণ নির্বিশেষে সংখ্যাগুরুর ভাষা ও সংস্কৃতি হয়ে উঠতে চায় দেশের, বলা ভাল রাষ্ট্রের পতাকাবাহক। ক্ষমতামাত্রেই কিছু জনগোষ্ঠীকে হয় প্রভাবিত করতে, নয় ‘প্রান্তিক’ করে রাখতে চায় (‘প্রান্তিক’ শব্দের অর্থ শুধুই দরিদ্র নয়)। প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে চলে হরেক কিসিমের সত্য মিথ্যা অর্ধসত্য প্রচার।– তার কিছু কিছু নজরে পড়ে, কয়েকটি পায় নজরানা। বলাই বাহুল্য, ‘হিন্দু আক্রান্ত’, ‘ইসলাম খতরে মে হ্যায়’ বা ‘কৃষকের অধিকার বিপন্ন’-এর চাইতে অনেক বেশি বর্ণচোরা হল ‘মাতৃভাষা চর্চায় ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়’ বা ‘গেঁয়ো সংস্কৃতির মূল্য নেই’ গোছের প্রোপাগ্যান্ডাগুলি।– এই রাজনীতি আইনসভার ছোট-বড় ভবনগুলি ছাড়িয়ে আরো বহুদূর অবধি বিস্তৃত। কিন্তু, আ মরি বাংলাভাষা, ‘ক্ষমতা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ কিনা ‘ক্ষমা করিবার তারণ’!…
যে লোক ‘soil’ বা ‘dirt’ হিসেবেই ‘মাটি’কে চিনেছে, ‘ও আমার দেশের মাটি তোমার ’পরে ঠেকাই মাথা’ তার অনুভবে ধরা দেয় না। যে জন অবাক হলেই ‘mind blowing’ উচ্চারণে অভ্যস্থ, সে সৌন্দর্যের প্রশান্তি বুঝবে কী ভাবে?… না, ইংরেজি ভাষার ব্লাসোফেমি করা হচ্ছে না। মানুষের চিন্তায় ভাবনায় মননে যে তার ভাষা ও সংস্কৃতির গভীর প্রভাব থাকে, সেটুকু বলার জন্যই এই উদাহরণগুলির অবতারণা। মানুষ যে-ভাষা বলে, সে-ভাষা তার জীবন আর পৃথিবীকে দেখার বোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।
এস্কিমোদের ভাষায় বিভিন্ন ধরণের বরফের জন্য প্রায় আঠারোটি শব্দ আছে, ইংরেজিতে আছে পাঁচটি (ice, snow, frost, sleet, slush, icicles), বাংলায় বা হিন্দিতে আরো কম। আজ যদি এস্কিমোদের শুধুমাত্র বাংলা বা হিন্দি শিখতে বাধ্য করা হয়, কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই তারা আর ইগলু নির্মাণের উপযোগী বরফ চিনতে পারবে না। আবার নাও, ছিপ, বজরা, ময়ূরপঙ্খী, গয়না, পানসি, কোষা, ডিঙ্গি, ডোঙা, পাতাম, বাচারি, রপ্তানি, ঘাসি, সাম্পান, ভেলা, বাতনাই, বালার, একমালাই, ভুটভুটি– সবই ক্রমান্বয়ে ‘small boat’, ‘large boat’ আর ‘motorboat’–এ পরিণত হলে বাংলাভাষীর দশাও অন্যরকম কিছু হবে না।
ভাষা কোনো নিথর নিরেট আবয়ব নয়, সে নদীর মতো প্রবাহমান। আর নদীর মতো বলেই তার দূষণ বা বিপন্নতার ফলাফলও সুদুরপ্রসারী। আজ যদি বাংলা ভাষা থেকে ‘খেসকামলা’ শব্দটি হারিয়ে যায়, সেই ক্ষতি শুধু শব্দতালিকা অবধি সীমাবদ্ধ থাকে না। এদেশের কৃষকেরা দুর্দিনে কোনো মজুরি বা ফসলের ভাগের জন্য নয়, শুধুমাত্র অন্যকে সাহায্য করার তাগিদে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব মিলে শ্রম দান করে, কৃতজ্ঞ জমির মালিক তাদের আদর আপ্যায়ন করে ভোজে নিমন্ত্রণ করে (কৃতজ্ঞতা: ‘লৌকিক শব্দকোষ’ – কামিনীকুমার রায়)।– শব্দের সঙ্গে হারিয়ে যায় এই সংস্কৃতিটিও।
পৃথীবীর পাঠশালায় গায়ে ‘ইউনিফর্ম’ (ইউনিফর্মিটি) চড়িয়ে ডিসিপ্লিনড্ বা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা চলতেই থাকবে। এমন অবস্থায় প্রান্তিক মানুষের প্রাণে শক্তি যোগাতে অন্তত নিজের ভাষাটুকু আঁকড়ে ধরা ছাড়া পথ কোথায়?…
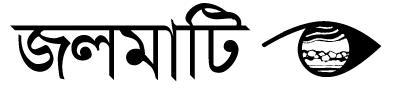












দারুণ লেখা। বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষা যে এত প্রাচীন না তা তো জানতাম ই না। দিদি যে তুর্কি আর বুবু যে সংস্কৃত থেকে আগত শব্দ এই ব্যাপারটাও খুব অবাক করে দিলো। এত এত তথ্য জানার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে লেখককে ধন্যবাদ।
প্রণাম
দাদা কি যে অসাধারণ লিখেছেন, আপনার লেখাটা নিয়মিত করেন দয়াকরে।আমাদর জলমাটিতে নিয়মিত লেখা চাই দাদা,বোন হিসেবে অধিকার বোধ থেকে বলছি।শুভ কামনা ও বিনম্র শ্রদ্ধ্যা জানবেন🙏🙏
একবার নয়, দু’বার পড়লাম। ভাললেগেছে বলেই দু’বার পড়া। এই লেখা নিয়ে সমালোচনার করার জন্য যে পরিমাণ পড়াশোনা থাকা দরকার, আমার তা নেই। একটা বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে লিখতে লিখতে তথ্যসূত্র উল্লেখ করে গেছেন লেখক। ফলে এটাকে কেবল মনগড়া কোন আলাপ মনে হয় নি। বর্ণভিত্তিক ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি এখনো সর্ব্বক্ষেত্রে গৃহীত হয় নি, তারমানে এই নয়, এটি সমালোচনার বাইরে। কিন্তু কিছুই না বলায় অবাক হতে হয়। এর পক্ষে কেউ কেউ এগিয়ে এসেছেন, আপনি তাদের একজন। আমি অতশত বুঝি না। রামায়ণ-মহাভারত বুঝার জন্য ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি প্রয়োগ না করে পড়লে, কিছুই বুঝা যায় না, এটা বুঝেছি খান-চক্রবর্তীর লেখা পড়ে। আপনার লেখাটি ভাবনার দুয়ার খুলে দিক, আলোচনা হোক, খুব করে চাই।
ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি বিষয়টা প্রাকৃতিক বলেই মনে হয়। সে বিষয়ে নিজের বইটিতে বিস্তারিত লিখেছি। সমস্যা হল ‘বর্ণভিত্তিক’ নিয়ে। তর্ক দূরে রেখে যদি খান-চক্রবর্তীর অভিধানের দিকেই তাকাই, সেখানে যে ‘অ’-এর অর্থ ‘অস্তিত্বন’ বা ‘ব’-এর অর্থ ‘বহন/ বৃদ্ধি’, ইত্যাদি পাওয়া যায়। একটু খুঁটিয়ে ভাবলেই বোঝা যাবে এই অস্তিত্বন বা বহন/ বৃদ্ধি- সবই আসলে ‘ক্রিয়া’।
হ্যাঁ, আমি ‘বর্ণভিত্তিকতা’র বদলে ‘ধ্বনিভিত্তিকতা’কেই সঠিক মনে করি। এবং তার যথেষ্ট যুক্তিও আছে। খোদ কলিমদার (কলিম খানকে ব্যক্তিগতভাবে ‘দাদা’ই ডাকতাম) সঙ্গেও এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা, তর্কও (ঝগড়া নয়) হয়েছে। ঘটনাচক্রে, কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী তাঁদের ‘বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ’-এ ‘ক্রিয়াভিত্তিক বর্ণভিত্তিক’-এর ইংরেজি তর্জমা হিসেবে ‘Verb-based Letter-based’ ব্যবহার করলেও তাঁদের এযাবৎকালের সর্বশেষ গ্রন্থ ‘ভাষাই পরম আলো’-তে তাকে ‘Action-based Phoneme-based’ বলেছেন। অবশ্য, এই শব্দার্থকোষের মুখবন্ধেই তাঁরা লিখেছেন, ‘এখানে বাংলা শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে শব্দের বানানের (বর্ণের বা বর্ণসমবায়ের, অর্থাৎ ধ্বনি বা ধ্বনিসমবায়ের) ভিতরে যে ক্রিয়াবাচক অর্থ রয়েছে, তা উপরে নির্ভর করে।’… এর পরেও ‘ধ্বনিভিত্তিক’ কীভাবে খান-চক্রবর্তীর বিরোধিতা হয়, তা রহস্যই বটে! আর তাঁরা যাকে ‘Action-based’ বলেছেন, এই বইতে অরেকধাপ উপরে ও গভীরে নিয়ে গিয়ে ক্রিয়ার পাশাপাশি বিষয়টির গাণিতিক, (বলা ভাল ‘আঙ্কিক’) দিকটি ধরার জন্য ‘ফাংশান-বেসড’ বলা হয়েছে। কারণ, ‘ফাংশান’ এমন একটি গাণিতিক ধারণা যা দুটি রাশির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রকাশ করে। একটি প্রদত্ত মান বা স্বাধীন চলক বা আর্গুমেন্ট বা ইনপুট। অপরটিকে উৎপাদিত রাশি বা ফাংশানটির মান বা আউটপুট। কোনো ফাংশানকে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করা যায়;– সূত্রের সাহায্যে, লেখচিত্রের সাহায্যে, বা তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। একটি ফাংশানকে অন্য এক বা একাধিক ফাংশানের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমেও প্রকাশ করা যায়। ভেবে দেখুন, শব্দ ও অর্থের চরিত্রের সঙ্গে এগুলি মেলে কিনা!
না, খান-চক্রবর্তীর তত্ত্বের অর্ধেকটা বাদ দিতে বলা হচ্ছে না। ‘পশ্চিমি আঙ্গিকে’ ধ্বনিভিত্তিকতাকেও আনার প্রস্তাবনা রাখা হচ্ছে না। (অবশ্য ‘পশ্চিম’-এর গন্ধ পেলেই জাতীয়তাবাদে আঘাত লাগলে বিপদ। জ্ঞানচর্চার জগতে তা এক ধরণের মৌলবাদও বটে।) ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি শব্দার্থের বহুমুখিতাকে সম্বোধন করে। তাকে নির্দিষ্ট আধারের (প্রচলিত প্রতীকী-অর্থের) বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেয়। বর্ণ আকার দান করলেই বরং আধেয়র ইনফাইনাইট পোটেনশিয়াল কিছুটা হলেও খর্ব হয়। ধ্বনি এনার্জি। সে শক্তি, প্রকৃতি। তার পুরুষাকারের প্রয়োজন হলে সে নিজের মধ্য থেকেই শিবসৃষ্টি করে নেবে। বিভিন্ন ভাষার বর্ণবিন্যাস ও রূপ আলাদা, মৌলিক ধ্বনিগুলি কিন্তু বহুলাংশে এক। কোনও একদিন (খান-চক্রবর্তী প্রস্তাবিত) ‘পরমভাষা’কে ধরতে চাইলে ধ্বনির মাধ্যমেই যেতে হবে নইলে ‘যত মত তত পথে’র জটিলতায় পড়তে হবে।
বর্ণ ‘বর্ণালী’ গঠন করে, বর্ণমালাও। সে আধার, অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ নয়। বরং তার আধেয় (ধ্বনি) অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্। বিজ্ঞানের পরিভাষায়, সে একটি ‘ফ্লাকচুয়েটিং সিস্টেম’। কিন্তু ‘সিস্টেম’, যা-ইচ্ছে-তাই নয়। এই ফ্লাকচুয়েটিং সিস্টেমের কম্পনই তাকে একমুখি হতে দেয় না। অনিশ্চয়তা সূত্রই ধরা যাক।… সেটা বলে আপনি একই সঙ্গে একটি কণার অবস্থান ও ভরবেগ নির্ধারণ করতে পারবেন না।– যে কোনো একটা। এবার ভরবেগকে কল্পনা করুন শব্দের পোটেন্সিয়াল হিসেবে, আর অবস্থান তার এক-একটি অর্থ।
এই প্রসঙ্গে আপত্তি তোলা হয়েছিল,– এখানে নাকি বর্ণ ও লিপি গোলানো হচ্ছে!… একটি শিশুও বোধহয় তার পার্থক্য বোঝে। ‘অ’ বর্ণ দেবনাগরীতেও আচে, গুরুমুখীতেও আছে, আমাদের সিদ্ধিমাতৃকাতেও আছে। নির্বাচিত অর্থপূর্ণ ধ্বনিকে স্বনিম/ ধ্বনিতা/ ধ্বনিমূল/ ফোনিম বলা যায়, বর্ণ নয়। ভাষার দুনিয়ায় ‘বর্ণ’ একটি প্রতিষ্ঠিত টার্মিনোলজিও (গ্রাফিম) বটে। ‘বর্ণভিক্তিক’ শব্দটি সেখানে অহেতুক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। হ্যাঁ, ‘বর্ণ’ শব্দটির বহুমুখী অর্থ আছে। কিন্তু, ভাষাতত্ত্বের দুনিয়ায় তা একমুখীই। সেখানে বর্ণগুলিকে ধ্বনির নামান্তর নয়, রূপান্তর/ চিহ্নকরণ। একসঙ্গে সবকিছু রিডিফাইন করতে যাওয়া বিপজ্জনক, এবং তা অপ্রয়োজনীয় বিতর্কেরও সৃষ্টি করা।
ঠাকুর শব্দটি সংস্কৃত নয়। তারমানে ভারতীয় ভাষাগুলোর কোথাও কি এর অস্তিত্ব ছিল না? বলা হয়েছে এটি তুর্কি হতে আগত। যদি তাই হয়, তবে ঠ বর্ণটি সৃষ্টি করার পেছনে কী কারণ কাজ করছিল? তাহলে কলিম খান যে বর্ণভিত্তিক ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির কথা বলছিলেন, সেটি কি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এখানে? কৌতুহল হচ্ছে, তাই এতগুলো প্রশ্ন করে ফেললাম। আশা করি , সাড়া পাব। ধন্যবাদ।
একটু ভুল হচ্ছে বোধহয়। সংস্কৃতে ‘ঠ’/ ‘থ’ বর্ণ বা ধ্বনিগুলির অস্তিত্ব ছিল না- এমন নয়। শব্দের শুরুতেই ‘ঠ’, ‘থ’, বর্ণ বা ধ্বনিগুলির উপস্থিতি খুব কম ছিল। আজও কিন্তু তেমনই আছে।…. জানি না, ওপার বাংলায় ‘গানের লড়াই’ বা ‘অন্তাক্ষরী’র চল আছে কিনা, যদি থাকে ও যদি কখনও তা খেলে থাকেন/ প্রত্যক্ষ করে থাকেন, মনে করে দেখবেন, ‘থ’ বা ‘ঠ’ দিয়ে শুরু হওয়া গানের সংখ্যা খুবই কম। আর সেইজন্যই অন্তাক্ষরীর খেলোয়ারেরা শেষ বর্ণে ‘ঠ’/ ‘থ’ আছে এমন গান গেয়ে বিপক্ষকে বেকাদায় ফেলার চেষ্টা করে।
কলিম খানের কোন এক লেখায় পড়েছিলাম, ঠ বর্ণে ঠাকুর দিয়ে একটি শব্দের অস্তিত্ব ছিল। অনেক আগে পড়া। ভুলও হতে পারে। আমি ভেবেছিলাম, ঠাকুর সংস্কৃত শব্দ। তাই কৌতুহল প্রকাশ করা ।
শব্দটা ‘ঠক্কুর’। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করলেও আদতে সে তুর্কি। মরিনার উইলিয়ামসের অভিধান বা রামেশ্বর শ-এর লেখায় পাবেন। কলিমদা হয়তো অভিধানে দেখেই তাকে সংস্কৃত ধরে নিয়েছিলেন।
পুঁজির স্বার্থেই ভাষার বৈচিত্রের পরিবর্তে ভাষার ঐক্য একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। যদিও আপাতত দৃষ্টিতে বিপরীত ধারায় তাদের বসতি, বিষয়টা এমনকি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মূলধারার সাম্রাজ্যবাদ এবং নানা প্রকরণের জাতিবাদ, ধর্মীয় ও সামাজিক তত্ত্ব ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের প্রসারেও ভাষা বিশেষের ঐক্যের প্রতি বল প্রয়োগের প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।